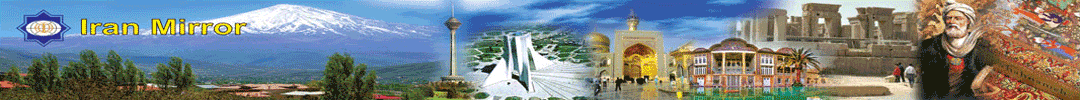বাংলা সাহিত্য ফারসি রসে ঋদ্ধকরণে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান
পোস্ট হয়েছে: জুন ১৫, ২০২১
বাংলা সাহিত্য ফারসি রসে ঋদ্ধকরণে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান
মেহেদী হাসান
কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি.) বাংলা সাহিত্যের অভূতপূর্ব প্রতিভা এবং চিরন্তন বাঙালি জাতিসত্তার প্রতিভূ এক স্বভাব-কবি। আজীবন দারিদ্র্যের সাথে মিতালিতে অভ্যস্ত মহান নজরুল সৈনিক হিসেবে বিশ^যুদ্ধের রণাঙ্গনে, নির্ভীক সাংবাদিক হিসেবে ধূমকেতুর মতো প্রকাশনার জগতে এবং সাধারণ বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে রাজনীতির আঙ্গিনায় অবাধ বিচরণের পাশাপাশি কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস ও নাটকসহ সাহিত্যের সকল শাখায় নিজের যে অসামান্য সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, বিশ^সাহিত্যে তার দৃষ্টান্ত বিরল। বিশ^কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১ খি.) যুগে জন্মগ্রহণ করেও তিনি কেবল তাঁর প্রভাবমুক্ত হতেই সক্ষম হননি, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সূচনা করতে পেরেছিলেন এক অনন্য ধারার, যে ধারাটি মধ্যযুগে বাঙালি মুসলিম কবিদের প্রচেষ্টায় ‘মুসলমানি রীতি’ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। মূলত ‘আধুনিক বাংলা সাহিত্য কেবল হিন্দুদের সাহিত্য নয়, মুসলমানদের সাহিত্যও বটে’Ñ এ বিষয়টিকে যে কেবল প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন, তা-ই নয়, বাংলা সাহিত্য-জগতে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী শ্রেষ্ঠত্বের স্থানটিকেও তিনি নিজের করে নিতে পেরেছেন। তিনি এ দুরূহ কাজটি করতে সক্ষম হয়েছিলেন কুলীন আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অবহেলিত, কিন্তু বাংলার আপামর গণমানুষের মুখে মুখে সাধারণভাবে প্রচলিত ফারসি, আরবি ও উর্দু শব্দরাজিসমৃদ্ধ ‘মুসলমানি ভাষা’ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সাহিত্যকর্মে ব্যবহারের মাধ্যমে। তিনি এতে এতটাই সফল হয়েছিলেন যে, তাঁর জীবদ্দশাতেই এ সাহিত্য-রীতিকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী ধারার উদ্ভব ঘটে। তাঁর সম ও উত্তরকালে হিন্দু মুসলমান বহু কবি-সাহিত্যিকই এ ধারায় প্রভাবিত হন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নজরুল যে ভাষার শব্দ সবচেয়ে বেশি ঋণ করেছেন, সেটি হচ্ছে ফারসি। শুধু ফারসি শব্দই নয়, বিশ্বখ্যাত ফারসি সাহিত্যের বিভিন্ন সাহিত্য-উপাদানও বাংলা সাহিত্যে প্রয়োগ করে এ সাহিত্যকে তিনি নিয়ে যান এক অনন্য উচ্চতায়। ফারসি সাহিত্যের বিশ^বিশ্রুত কবিদের বিভিন্ন সাহিত্যকর্মের অনুবাদ ও তাঁদের দর্শন ও ভাবধারাকে বাংলা সাহিত্যে প্রবিষ্ট করে তিনি এ সাহিত্যে একটি ভিন্নমাত্রা সংযোজন করেন। তাঁর এ বিস্ময়কর প্রতিভাই বাংলা সাহিত্যে তাঁকে দান করেছে শ্রেষ্ঠত্ব ও চিরন্তনতা; আসীন করেছে বাংলাদেশের ‘জাতীয় কবি’র আসনে।
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, আর্য ও অনার্যদের সংমিশ্রণের ফসল হচ্ছে বাঙালি জাতি। এর পরবর্তী পর্যায়ে আরব-ইরান তথা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম ব্যবসায়ী, ধর্মপ্রচারক ও বিজয়ী শাসকগোষ্ঠী বঙ্গীয় জনপদে ইসলাম প্রচারের ফলে বাঙালি জাতির মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানÑ এ দুটি বৃহত্তর স্বতন্ত্র সম্প্রদায় অস্তিত্ব লাভ করে। ফলে অবধারিতভাবে ধর্মকে কেন্দ্র করে একই ভাষার দুটি ধারা সূচিত হয়। সনাতনী বাংলা এবং মুসলমানি বাংলা। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ থেকে এ দুটি ধারায়ই যথাক্রমে হিন্দু লেখকগণ মঙ্গলকাব্য এবং মুসলমান কবি-সাহিত্যিকগণ ফারসি সাহিত্যের অনুবাদ-নির্ভর বাংলা পুঁথিকাব্য, যেমন : ইউসুফ-জুলেখা, লাইলী-মজনু, জঙ্গনামা, নূরনামা প্রভৃতি কাব্য রচনা করতে থাকেন। মুসলমানি বাংলা বলতে আমরা ওই বাংলাকে বুঝি, যে বাংলা সমৃদ্ধ হয়েছিল ফারসি এবং ফারসিভাষী শাসকগোষ্ঠীর ভাষায় ব্যাপকহারে ব্যবহৃত আরবি শব্দাবলির দ্বারা, যেগুলোকে তারা ফারসি ভাষার আবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করত। বলা হয়ে থাকে, ফারসি-আরবি শব্দভা-ারসমৃদ্ধ এ মুসলমানি বাংলা-ই বাংলা ভাষাকে মৃতভাষায় পরিণত হবার হাত থেকে রক্ষা করে। এ ভাষাটি সৃষ্টির পটভূমি হচ্ছে : ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ারুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বঙ্গদেশ মুসলিম শাসনের আওতায় আসার পর থেকে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৬৩৪ বছর বাংলার সরকারি তথা রাজভাষা ছিল ফারসি। চাকুরি পাবার ক্ষেত্রে এখন যেমন প্রতেকের ইংরেজিজ্ঞান থাকা আবশ্যক, ওই সময়কালে তেমনি হিন্দু, মুসলমান কিংবা অন্য যেকোনো ধর্মের অনুসারীকেই সরকারি চাকুরি পেতে হলে ফারসি ভাষা জানতেই হতো। শাসকদের ভাষা হিসেবে এটি ছিল সকল সম্প্রদায়ের অভিজাত শ্রেণির ভাব বিনিময়ের মাধ্যম। ফলে এ ছয় শতাধিক বছরে হাজার হাজার ফারসি এবং ফারসিতে ব্যবহৃত আরবি শব্দ ব্যাপকহারে বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করে। উল্লেখ্য, ফারসি ভাষা বাঙালি জাতির উপর এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ কর্তৃক এ দেশ বিজিত হলেও ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৮১ বছর তারা তাদের ভাষা ইংরেজি দ্বারা ভারতবর্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হয়নি। এ সময়ে তাদেরকেও ফারসি ভাষা শিখেই এদেশ শাসন করতে হয়েছে। এমনকি ১৮৩৮ সালে এক রাজকীয় ফরমানের মাধ্যমে ইংরেজিকে সরকারি ভাষায় রূপান্তরিত করা হলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত ফারসি ভাষার ব্যবহার ও চর্চা এদেশের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে স্ব-মহিমায় বিদ্যমান ছিল।
এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, ফারসির ভাষাশৈলী সাহিত্যচর্চাÑ বিশেষত কাব্যচর্চার জন্য বিশ্বের যে কোনো ভাষার চেয়ে অনুকূলতর। তবে কেবল ভাষাশৈলীই নয়, এ ভাষায় বিদ্যমান প্রেম, মানবতা ও নৈতিকতার বাণী ও শিক্ষা বাঙালি কবি-সাহিত্যিকদের ভীষণভাবে আকৃষ্ট করত। আর এ কারণেই তাঁরা বাধ্য হয়ে নয়, বরং মনের টানেই এ ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। আর সে কারণেই ১৮৩৮ সালে সরকারিভাবে এ ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ হয়ে গেলেও এর চর্চা সাধারণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই তখনও বিদ্যমান ছিল। তবে এটা ঠিক যে, চর্চাটি তখন ক্রমক্ষয়িষ্ণু ছিল।
বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে তখনও ফারসি ভাষার চর্চা সমাজে বিদ্যমান ছিল; এমনকি মধ্যযুগে যে বাঙালি হিন্দু কবি-সাহিত্যিকগণ বিদ্বেষপ্রসূতভাবে এ ভাষার শব্দরাজি ব্যবহার থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিলেন, তাঁরাও এ যুগে তাঁদের গল্প-কবিতায় ফারসি-আরবি শব্দের ব্যবহার শুরু করেন, এদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদারের নাম প্রণিধানযোগ্য। অত্র প্রেক্ষাপটটির এ কারণে অবতারণা করা হলো, যাতে আগ্রহী পাঠকগণ অনুধাবন করতে পারেন যে, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেয়া কাজী নজরুল ইসলাম এমন একটা সময়, পরিবেশ ও পরিবারে বেড়ে উঠেছিলেন, যেখানে ফারসি কোনো অপরিচিত ভাষা ছিল না এবং এর চর্চা ক্ষীণভাবে হলেও সেখানে তখনও বিদ্যমান ছিল। তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি গভীর আকর্ষণ জিনগতভাবেই নজরুলের মধ্যে বিরাজমান ছিল। এটা ছিল শত শত বছরের প্রাচীন এমন এক উত্তরাধিকার, যা দ্বারা তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।
ফারসি ভাষাজ্ঞানের সাথে নজরুলের পরিচয়, যখন তিনি চুরুলিয়া গ্রামের মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে যান। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, তৎকালীন মক্তবসমূহে বাংলা, উর্দু ও আরবি শেখানোর পাশাপাশি কবি শেখ সাদির গুলিস্তান, বুস্তান ও পান্দনামা, ফরিদুদ্দিন আত্তারের পান্দনামা ও মানতেকুত্তাইর এবং মৌলানা রুমির মসনভি শরিফের পাঠও দেয়া হতো। তাই মক্তবে পাঠগ্রহণকালীন তিনি ফারসির উপর প্রাথমিক জ্ঞান লাভ তো করেনই, উপরন্তু শিক্ষালাভ শেষে তিনি যখন একই মক্তবে শিক্ষকতা শুরু করেন, তখন হয়ত ওই ফারসি কিতাবাদি তাঁকে পড়াতেও হতো। এছাড়া তাঁর জীবনীগ্রন্থসমূহে দেখা যায়, শৈশবকালে তিনি তাঁর চাচা বজলে করিমের কাছে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উপর তালিম নেন। এভাবে তাঁর ফারসি ভাষাজ্ঞান ধীরে ধীরে আরো শাণিত হয়ে ওঠে।
ভৌগোলিক দিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামের কিছুটা উত্তর থেকেই শুরু হয়েছে উর্দুভাষী বিহারী অধ্যুষিত ভারতের ঝাড়খ- রাজ্য। সে কারণের চুরুলিয়া এলাকার মানুষের মাতৃভাষা বাংলা হলেও তা ছিল ব্যাপক মাত্রায় উর্দু প্রভাবিত। আর যেহেতু ফারসি শব্দভা-ারকে আশ্রয় করে হিন্দি ভাষা থেকে উর্দু ভাষার জন্ম, তাই ভৌগোলিক কারণেও নজরুল উর্দু ও উর্দুর হাত ধরে ফারসি শব্দরাজির সাথে পরিচিতি লাভ করেন সেই ছোটবেলাতেই।
নজরুলের এ ফারসিজ্ঞান পরিপক্বতা লাভ করে যখন তিনি ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে যোগদান করে বর্তমান পাকিস্তানে অবস্থিত করাচি শহরে গমন করেন। সেখানে তিনি ১৯১৯ সাল পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উপর গভীর জ্ঞান লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর অনূদিত ‘রুবাইয়াত-ই-হাফিজ’ গ্রন্থের ‘মুখবন্ধে’ নজরুল নিজেই উল্লে¬খ করেন :
আমি যখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি, সে আজ ইংরেজি ১৯১৭ সালের কথা, সেখানেই প্রথম হাফিজের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙালি পল্টনে একজন মৌলভী সাহেব থাকতেন। একদিন তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতগুলি কবিতা আবৃতি করে শোনান, শুনে আমি এমনি মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেদিন থেকেই তাঁর কাছে ফারসি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি। তাঁর কাছেই ক্রমে ক্রমে ফারসি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি।
তিনি যে ফারসি সাহিত্যের একজন বড় অনুরাগী ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর প্রিয় বন্ধু মুজাফফর আহমদের ভাষ্যেও। করাচি থেকে ফিরে আসার পর তিনি কবির গাঁঠরির মধ্যে অন্যান্য জিনিসের সাথে ফারসিতে লেখা দিওয়ান-ই-হাফিজের একটি বড় সংস্করণও দেখতে পান বলে জানান। উল্লে¬খ করার মতো বিষয় হলো, কবি নজরুল তাঁর সফল কবিতা রচনা শুরু করেছিলেন হাফিজের কবিতা দিয়েই। কবিতাটির নাম ছিল ‘আশায়’ এবং এটি বাংলা ১৩২৬ সালে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। হাফিজের একটি গজলের ভাবধারা অবলম্বনে তিনি রচনা করেছিলেন এ কবিতাটি, কবিতার প্রথম দুটি লাইন ছিল এমন :
নাইবা পেল নাগাল, শুধু সৌরভেরই আশে
অবুঝ সবুজ দূর্বা যেমন যুঁই কুঁড়িটার পাশে…
তিনি চেয়েছিলেন এ কবিতার মধ্যমে ইরানি কবি হাফিজের কাব্যে বাংলার সবুজ দূর্বা ঘাস ও যুঁই ফুলের সুবাসকে ছড়িয়ে দিতে। ফারসি কাব্য বাংলা ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে তিনি চেয়েছিলেন পারস্যের প্রেমময় আবহকে বাংলা সাহিত্যে আনয়ন করে একে পরিপূর্ণতায় পৌঁছে দিতে। তিনি ইরানের গোলাব আর নার্গিসের সুবাসকে বাংলার যুঁই-চম্পা-চামেলীর বাগিচায় স্থান দিয়ে একে আরও সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি শোনাতে চেয়েছিলেন কোকিলের পাশাপাশি ইরানি বুলবুলির গান, যাতে বাঙালি জাতি এক নবসুরের রসাস্বাদন করে পরিতৃপ্ত হতে পারে। তিনি তাঁর প্রচেষ্টায় শতভাগ সফলতাও লাভ করেছিলেন। তিনি ইরানের দার্শনিক কবি ওমর খৈয়ামের ১৯৭টি রুবায়ি বা চতুষ্পদী কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। তবে এতে তিনি এতটাই মুন্সিয়ানা দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, সেগুলো কি অনুবাদ নাকি মৌলিক রচনা, অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণও পাঠ করার সময় সে পার্থক্যটি নির্ণয় করতে সত্যিই সংশয়ে পড়ে যান। উদাহরণত খৈয়ামের একটি রুবাই:
گویند کسان که بهشت با حور خوش است
من می گویم آب انگور خوش است
این نقد بگیر و دست از نسیه مدار
که آواز دهل شنیدن از دور خوش است
(رباعیات، شماره: )
গুইয়ান্দ্ কাসা’ন্ কে বেহেশ্ত্ বা’ র্হু খোশ্ আস্ত্
মান্ মী গুইয়াম্ আ’বে আর্ঙ্গূ খোশ্আস্ত্
ঈন্ নাগ্দ্ বেগীরো দাস্ত্ আয্ নাসিয়ে মাদার্’
কে আ’ওয়া’জে দোহ্ল্ শেনীদান্ আয্ র্দূ খোশ্ আস্ত্
নজরুলের অনুবাদ:
করছে ওরা প্রচার-পাবি স্বর্গে গিয়ে হুর-পরী
আমার স্বর্গ এই মদিরা, হাতের কাছের সুন্দরী
নগদা যা পাস তাই ধরে থাক, ধারের পণ্য করিসনে,
দূরের বাদ্য মধুর শোনায়, শূণ্য হাওয়ার সঞ্চারি।
ইরানের বিশ্ববিখ্যাত সুফিকবি মৌলানা জালালুদ্দিন রুমির বিখ্যাত গ্রন্থ মসনভি শরিফের শুরুর অংশটি:
بشنو از نی چون حکایت می کند
از جدایی¬¬ها شکایت می کند
(مثنوی، جلد اول، مقدمه)
বেশ্নু আয্ নেই চূন্ হেকা’ইয়াত্ মী কোনাদ্ আয্ জোদা’ঈহা’ শেকা’ইয়াত্ মী কোনাদ্
কবি নজরুল অনুবাদ করেন ‘বাঁশির ব্যথা’ শিরোনামে এভাবে :
শোন দেখি মন বাঁশের বাঁশির বুক জেগে কী উঠবে সুর,
সুর তো নয় ও কাঁদবে যে রে বাঁশরি বিচ্ছেদ বিধুর।
কিন্তু রুমির দর্শনে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ নজরুল তাঁর খুব বেশি কবিতা অনুবাদ করেননি, যেমনটি করেছেন ইরানের প্রেমিক কবি হাফিজের কবিতার। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, নজরুল সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত ছিলেন হাফিজের দ্বারাই। ইরানের এ অনন্য কবির বহু গজল যেমন তিনি অনুবাদ করেছেন, তেমনি প্রায় ৭৩টি রুবায়ি বা চতুস্পদী কবিতাও সরাসরি মূল ফারসি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন বলে নজরুল নিজেই উল্লে¬খ করেছেন। হাফিজকে গভীরভাবে অধ্যয়নের ফলে নজরুল বাংলার ভাষা-শক্তি, ভাষা-চরিত্র এবং ভাষা-মেজাজের স্টাইল বা ভঙ্গিকে আমূল বদলে দিতে পেরেছিলেন। এর প্রমাণ মেলে নজরুলকৃত হাফিজের ফারসি কাব্য-ছন্দের হুবহু অনুকরণে অনূদিত কয়েকটি গজলের পঙ্ক্তি থেকে। যেমন :
হাফিজের গজল :
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها
(دیوان حافظ، شمارۀ غزل: ১)
আলা’ ইয়া’ আইয়্যুহাস্ সা’ক্বী আর্দে কা-সান্ ওয়া’ না’ভেল্হা’
কে এশ্ক্ব্ আ’সা’ন্ নেমুদ্ আওয়াল্ ওয়ালী ওফ্তা’দ্ মোশকেল্হা’
সুনিপুণ দক্ষতায় নজরুল এ গজলটিকে ঠিক একই ছন্দে বাংলায় অনুবাদ করেন নি¤œলিখিতভাবে :
হ্যাঁ, এয় সাকি, শরাব ভর লাও, বোলাও পেয়ালী চালাও হরদম
প্রথম প্রেম পথ সহজ সুন্দর, শেষের দিক তার ঢালাও কর্দম!
এছাড়া কবি হাফিজের বিখ্যাত গজল :
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا
بخال هندویش بخشم سمرقند و بخارارا
(دیوان حافظ، شمارۀ غزل: ২)
আর্গা অ’ন্ র্তোকে শীরা’যী বেদাস্ত অ’রাদ্ দেলে মা’রা’
বেখা’লে হিন্দুইয়াশ্ বাখ্শাম্ সার্মাকান্দো বোখা’রা’রা’
ফারসি ছন্দের পুরোপুরি অনুসরণ করলেও তাঁর বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে অর্থের কোনো ব্যত্যয়ই এতে ঘটেনি। উদাহরণত নজরুলের অনুবাদ :
যদিই কান্তা শিরাজ সজনি ফেরত দেয় মোর চোরাই দিল ফের
সমরকন্দ আর বোখারায় দিই বদল তার লাল গালের তিলটের।
এভাবে নজরুল কেবল ফারসি কবিতার অনুবাদ দ্বারাই নয়, বরং ফারসি কবিতার ছন্দকেও চমৎকার মুন্সিয়ানার সাথে বাংলা কবিতার জগতে সংযোজন করে বাংলা কাব্যসাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ করেছেন।
এছাড়া তিনি কবি হাফিজ ও বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ যে গযলটি বিদ্যমান, সে গযলটিরও দুটি লাইন অত্যন্ত সফলতার সাথে চমৎকার কাব্যানুবাদ করেছেন, যার মধ্যে বিখ্যাত পঙ্ক্তিটি হচ্ছে :
হাফিজ :
شکر شکن شوند همه طوطیان هند
زین قند پارسی که به بنگاله می رود
(دیوان حافظ، شمارۀ غزل: ২২৩)
শের্কা শেকান্ শাভান্দ্হামে তুতীয়া’নে হেন্দ্
যিন্ গান্দে র্ফাসি কে বে বাঙ্গা’লে মী রাভাদ্
নজরুল :
আজকে পাঠাই বাংলায় যে ইরানের এই ইক্ষুশাখা
এতেই হবে ভারতের সব তোতার চঞ্চু মিষ্টি মাখা।
নজরুল দৃশ্যত রুমি, হাফিজ ও খৈয়ামÑ এই তিন ইরানি কবির রচনা অনুবাদ করলেও এর অর্থ এই নয় যে, তিনি কেবল এদের দ্বারাই উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত ছিলেন; বরং তিনি গোটা ফারসি সাহিত্য দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি যেমন শেখ সাদি’র নৈতিকতা ও মানবতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিলেন, তেমনি ফেরদৌসির বীররসও আস্বাদন করেছিলেন। তিনি শেখ সাদির বিখ্যাত নাত ‘বালাগাল উলা বিকামালিহী’ অবলম্বনে রচনা করেছিলেন নাতে রাসুল :
কূল মাখলুক গাহে হযরত বালাগাল উলা বেকামালিহী
আঁধার ধরায় এলে আফতাব কাশাফাদ্দোজা বিজামালিহী
এছাড়া নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতাসহ বীররস সমৃদ্ধ কবিতাগুলি আমাদের ফেরদৌসির ‘শাহনামা’র কথাই মনে করিয়ে দেয়। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, নজরুল ইরান, ফারসি ভাষা ও ফারসি সাহিত্যের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত ছিলেন। কবির এমন একটি গান বিদ্যমান রয়েছে, যেটিতে তিনি সরাসরি কয়েকটি ফারসি ছন্দের উল্লেখ করেছেন। গানটির প্রথম পঙ্্ক্তি হলো :
মোফাআলতুন মোফাআলতুন, মোফাআলতুন মোফাআলতুন
কানের তার তুল দোদুল দুল, কোথায় তার তুল কোথায় তার তুল
ফারসি সুরের উপরেও কবি বেশ কিছু গান লিখেছেন। এর মধ্যে ‘শুকনো পাতার নূপুর পায়ে’ এবং নাতে রাসুল ‘ত্রিভূবনের প্রিয় মোহাম্মাদ এলরে দুনিয়ায়’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
তাঁর রচনায় ফারসি শব্দের দেদার ব্যবহার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি এটি করেছেন অবলীলায় এবং স্বভাবগতভাবেই। কারণ তাঁর জন্মস্থান চুরুলিয়ার মাতৃভাষা বাংলার রূপটি ছিল এমনই ফারসি-উর্দু মিশ্রিত। তাই তাঁর পক্ষে এমন সব ফারসি শব্দের ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে ঘটানো সম্ভব হয়েছে, যা সেই সময়কার সাধারণ লোকজন তাদের দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তায় ব্যবহার করত। সত্যিকারার্থেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সেসব শব্দের ব্যবহার ছিল অভূতপূর্ব। তাঁর ব্যবহৃত এ ধরনের কিছু ফারসি শব্দ নিম্নরূপ :
খোদা, নামাজ, রোজা, জায়নামাজ, আসমান, জমিন, বেহেশত, দোজখ, আমদানি, আরাম, আহাজারি, ঈদগাহ, একদম, কম, কমজাত, কমজোর, কমবখত, কামান, কিশতি, খঞ্জর, খাক, খাজা, খামোশ, খাঞ্চা, খোশ আমদেদ, খোশখবর, খোশনসিব…।
এমন অসংখ্য ফারসি শব্দ নজরুল অত্যন্ত সফলতার সাথে নিজ সাহিত্যকর্মে ব্যবহার করেছেন, যা মূলত বাংলা সাহিত্যকেই করেছে সমৃদ্ধ এবং তেজোদ্দীপ্ত। তাঁর এ অবদান অবিস্মরণীয়। আর এ কারণেই নজরুল বাংলা সাহত্যে চির-অম্লান, চির-ভাস্বর হয়ে থাকবেন।
লেখক : নজরুল গবেষক এবং সহকারী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়।
সহায়ক গ্রন্থ
১. নজরুল রচনাবলী- রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
২. নজরুল সাহিত্য বিচার- শাহাবুদ্দীন আহ্মদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩. নজরুল সাহিত্যে ফারসি ভাষার প্রভাব- রাশেদুল হাসান শেলী এবং মাহবুব বারী সম্পাদিত, নজরুল গবষেণা ও লোকসংস্কৃতি ইনস্টিটিউট, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
৪. নজরুলের কাব্যানুবাদ- নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৫. যুগ ¯্রষ্টা নজরুল- খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন, আলহামরা প্রকাশনী, ঢাকা।
৬. রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম- কাজী নজরুল ইসলাম, মোহন লাইব্রেরি, কলিকাতা।
৭. دیوان حافظ، شمس الدین محمد حافظ، انتشارات کتاب آبان، تهران
৮. رباعیات عمر خیام، حکیم عمر خیام نیشابوری، امیر کبیر، تهران
৯. مثنوی معنوی، مولانا جلال الدین محمد، کتابخانۀ ملی ایران، تهران