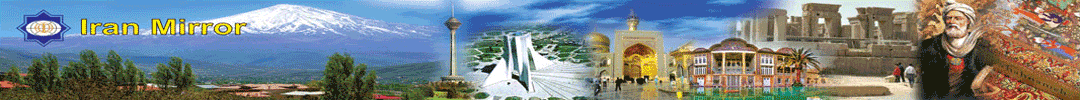তিন হাজার বছরের ইরানী স্থাপত্য শিল্প
পোস্ট হয়েছে: মার্চ ৩১, ২০১৪

অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান
প্রাচীন পারস্যের শিল্প ঐতিহ্য
প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে মিশরীয়, গ্রীক এবং রোমান সভ্যতা যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রাচীন পারসিক সাম্রাজ্য। পুরাতন পৃথিবীতে ইরানীয় মালভূমিতে যে পারসিকরা বসতি করত তারা অনন্যসাধারণ স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন রেখে গেছে। এক সময় সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে ফেরাউনের প্রতাপ ছিল। তারপরে এল নিনেভা এবং ব্যাবিলনের রাজাদের প্রতাপ। এরপরই আমরা ইরানে একিমিনীয় সাম্রাজ্যের সন্ধান পাই। একিমিনীয় সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ছিল দীর্ঘকাল পর্যন্ত। এই সাম্রাজ্য যে বলিষ্ঠ সংস্কৃতিকে বহন করত সেই সংস্কৃতির নিদর্শনস্বরূপ আমরা প্রাচীন পারস্যে অনেক দুর্গ ও প্রাসাদের নিদর্শন পাই। এই দুর্গ ও প্রাসাদের নিদর্শন থেকে নির্ণয় করতে অসুবিধা হয় না যে, প্রাচীন পারস্যের এই সভ্যতায় বিত্তের অধিকার এবং প্রতাপ ছিল প্রচণ্ড। এর প্রমাণ আমরা পাই বহু বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তাদের ধ্বংসাবশেষের চিহ্নের মধ্যে।
 ইরানের অভ্যুদয় কখন হয় তা আমরা সুস্পষ্টভাবে জানি না। গবেষকগণ অনুমান করেন যে, ‘জেন্দাবেস্তা’য় উল্লিখিত ‘আরিয়ান’ শব্দটি থেকেই ইরান শব্দের উদ্ভব ঘটেছে। ‘জেন্দাবেস্তা’য় উল্লিখিত নামের অর্থ হচ্ছে আর্য জাতির বসতভূমি। ‘পারস্য’ শব্দটিও প্রাচীন। এ শব্দটি এসেছে গ্রীক ‘পারসিস’ শব্দ থেকে। ‘পারসিস’ শব্দের অর্থ ফারস প্রদেশ। প্রাচীন যে একিমিনীয় রাজশক্তির উদ্ভব ইরানে ঘটেছিল তাদের উদ্ভব হয়েছিল ফারস্ প্রদেশ থেকেই। একিমিনীয় রাজ্যের রাজধানী ফারস্ প্রদেশে বলেই বর্তমান পারস্য শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়। প্রাচীন পারস্যে মিদ এবং পারসিক- এ দু’টি সম্প্রদায় ছিল আর্য সম্প্রদায়। মিদ সভ্যতাও একটি প্রাচীন সভ্যতা যা পরে পারসিস সভ্যতার সঙ্গে মিশে যায়। মিদ সভ্যতার সঙ্গে অ্যাসিরিয় এবং সিথীয় সভ্যতার সম্পর্ক ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ১১০০ অব্দের অ্যাসিরীয় শিলালিপিতে মিদ সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। এরা ছিল পারস্যের পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী এবং দীর্ঘকাল এরা অ্যাসিরীয়দের শাসনাধীনে ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ অব্দে এরা স্বাধীনতা অর্জন করে। দক্ষিণ পারস্যের অধিপতি কাইরাস খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০ অব্দে মিদ সম্প্রদায়কে পরাভূত করে নিজের সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। তিনি লিদিয়ার রাজা ক্রিসাসকেও পরাজিত করেন এবং সর্বশেষ পর্যায়ে ব্যাবিলনও তার বশ্যতা স্বীকার করে। এ ঘটনাটি ঘটে খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৮ অব্দে। এভাবে ব্যাবিলন এবং মিদীয় সাম্রাজ্য অধিকার করে কাইরাস যে বিরাট সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন তা বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে একিমিনীয় সাম্রাজ্য নামে চিহ্নিত। যেহেতু এই সাম্রাজ্যের সম্রাটদের পূর্বপুরুষদের একজনের নাম ছিল একিমিনীয় সেই কারণে কাইরাসের সাম্রাজ্য একিমিনীয় সাম্রাজ্য বলে খ্যাতি পেয়েছে। কাইরাসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রের রাজত্বকালে একিমিনীয় সাম্রাজ্য মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু এই সাম্রাজ্য চূড়ান্তভাবে বিস্তৃতি লাভ করে দারিয়ুসের সাম্রাজ্যকালে। সময়কাল হচ্ছে ৫২১ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ৪৮৬ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত। এভাবে যে সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে সে সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় সমগ্র এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, অ্যাসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য। ককেশাস ও কাস্পিয়ান অঞ্চল, মিদিয়া, পারস্য ও ভারতবর্ষের সিন্ধু দেশ। এই সাম্রাজ্য খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০ অব্দ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল এবং ৩৩০ অব্দেই আলেকজান্ডারের আক্রমণে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
ইরানের অভ্যুদয় কখন হয় তা আমরা সুস্পষ্টভাবে জানি না। গবেষকগণ অনুমান করেন যে, ‘জেন্দাবেস্তা’য় উল্লিখিত ‘আরিয়ান’ শব্দটি থেকেই ইরান শব্দের উদ্ভব ঘটেছে। ‘জেন্দাবেস্তা’য় উল্লিখিত নামের অর্থ হচ্ছে আর্য জাতির বসতভূমি। ‘পারস্য’ শব্দটিও প্রাচীন। এ শব্দটি এসেছে গ্রীক ‘পারসিস’ শব্দ থেকে। ‘পারসিস’ শব্দের অর্থ ফারস প্রদেশ। প্রাচীন যে একিমিনীয় রাজশক্তির উদ্ভব ইরানে ঘটেছিল তাদের উদ্ভব হয়েছিল ফারস্ প্রদেশ থেকেই। একিমিনীয় রাজ্যের রাজধানী ফারস্ প্রদেশে বলেই বর্তমান পারস্য শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়। প্রাচীন পারস্যে মিদ এবং পারসিক- এ দু’টি সম্প্রদায় ছিল আর্য সম্প্রদায়। মিদ সভ্যতাও একটি প্রাচীন সভ্যতা যা পরে পারসিস সভ্যতার সঙ্গে মিশে যায়। মিদ সভ্যতার সঙ্গে অ্যাসিরিয় এবং সিথীয় সভ্যতার সম্পর্ক ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ১১০০ অব্দের অ্যাসিরীয় শিলালিপিতে মিদ সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। এরা ছিল পারস্যের পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী এবং দীর্ঘকাল এরা অ্যাসিরীয়দের শাসনাধীনে ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ অব্দে এরা স্বাধীনতা অর্জন করে। দক্ষিণ পারস্যের অধিপতি কাইরাস খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০ অব্দে মিদ সম্প্রদায়কে পরাভূত করে নিজের সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। তিনি লিদিয়ার রাজা ক্রিসাসকেও পরাজিত করেন এবং সর্বশেষ পর্যায়ে ব্যাবিলনও তার বশ্যতা স্বীকার করে। এ ঘটনাটি ঘটে খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৮ অব্দে। এভাবে ব্যাবিলন এবং মিদীয় সাম্রাজ্য অধিকার করে কাইরাস যে বিরাট সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন তা বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে একিমিনীয় সাম্রাজ্য নামে চিহ্নিত। যেহেতু এই সাম্রাজ্যের সম্রাটদের পূর্বপুরুষদের একজনের নাম ছিল একিমিনীয় সেই কারণে কাইরাসের সাম্রাজ্য একিমিনীয় সাম্রাজ্য বলে খ্যাতি পেয়েছে। কাইরাসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রের রাজত্বকালে একিমিনীয় সাম্রাজ্য মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু এই সাম্রাজ্য চূড়ান্তভাবে বিস্তৃতি লাভ করে দারিয়ুসের সাম্রাজ্যকালে। সময়কাল হচ্ছে ৫২১ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ৪৮৬ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত। এভাবে যে সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে সে সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় সমগ্র এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, অ্যাসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য। ককেশাস ও কাস্পিয়ান অঞ্চল, মিদিয়া, পারস্য ও ভারতবর্ষের সিন্ধু দেশ। এই সাম্রাজ্য খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০ অব্দ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল এবং ৩৩০ অব্দেই আলেকজান্ডারের আক্রমণে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
 এভাবেই ক্রমশ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড অধিকারের ফলে সামগ্রিকভাবে একিমিনীয় শিল্পকর্মের যে বিকাশ ঘটে তা এককভাবে একিমিনীয় শিল্পরূপ নয়, তার মধ্যে মিশ্রণ ঘটে মিশরীয় শিল্পের, অ্যাসিরীয় এবং গ্রীক শিল্পের। কিন্তু এই শিল্পের সকল প্রকার নিদর্শন আমরা পাই না। আমরা শুধু রাজসিক শিল্পের নিদর্শনস্বরূপ পুরাতন রাজপ্রাসাদগুলোর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পাই। তবে এই ধ্বংসাবশেষও একটি অসাধারণ স্থাপত্য শিল্পের অধিকারকে প্রমাণ করে। যখন ৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে কাইরাস ব্যাবিলন দখল করেন তখন ব্যাবিলনের শাসনের চূড়ান্ত পতন ঘটে এবং টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেতিসের নিকটবর্তী শহরগুলো মূল্যহীন হয় এবং নতুন শহর সমৃদ্ধি পায় সুসায়, পার্সিপোলিসে এবং পাসারগাদে। আমরা জানি যে, যে কোন শিল্প দু’টি অবস্থাকে আত্মস্থ করে গড়ে ওঠে অথবা বলা যেতে পারে, নির্ভর করে গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে একটি বাস্তব অবস্থা এবং অপরটি হচ্ছে বোধ এবং বিশ্বাসের অবস্থা। প্রাথমিক অবস্থার ক্ষেত্রে আবহাওয়া এবং প্রাপ্য উপকরণের গুরুত্ব অসীম। দ্বিতীয় অবস্থার জন্য ধর্মবিশ্বাস এবং সামাজিক রীতিনীতির গুরুত্ব অপরিহার্য। একটি দেশের কি ধরনের শিল্প গড়ে উঠবে তা নির্ভর করে সে দেশের অবস্থান এবং প্রাকৃতিক বিন্যাসের ওপর। মহেন-জো-দারোয় পাথর ছিল না। সেখানে সবকিছু ছিল মাটির। তেমনি সুমার দেশেও পাথর ছিল না, কাঠও ছিল না। তাই তারাও তাদের অট্টালিকা মাটি দিয়ে তৈরি করেছিল। কিন্তু পারস্যের অবস্থা ছিল ভিন্ন। পারস্যে পাথর ছিল প্রচুর। তাই সেখানে মাটির তৈরি অট্টালিকার কথা চিন্তাও করা যায় না।
এভাবেই ক্রমশ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড অধিকারের ফলে সামগ্রিকভাবে একিমিনীয় শিল্পকর্মের যে বিকাশ ঘটে তা এককভাবে একিমিনীয় শিল্পরূপ নয়, তার মধ্যে মিশ্রণ ঘটে মিশরীয় শিল্পের, অ্যাসিরীয় এবং গ্রীক শিল্পের। কিন্তু এই শিল্পের সকল প্রকার নিদর্শন আমরা পাই না। আমরা শুধু রাজসিক শিল্পের নিদর্শনস্বরূপ পুরাতন রাজপ্রাসাদগুলোর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পাই। তবে এই ধ্বংসাবশেষও একটি অসাধারণ স্থাপত্য শিল্পের অধিকারকে প্রমাণ করে। যখন ৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে কাইরাস ব্যাবিলন দখল করেন তখন ব্যাবিলনের শাসনের চূড়ান্ত পতন ঘটে এবং টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেতিসের নিকটবর্তী শহরগুলো মূল্যহীন হয় এবং নতুন শহর সমৃদ্ধি পায় সুসায়, পার্সিপোলিসে এবং পাসারগাদে। আমরা জানি যে, যে কোন শিল্প দু’টি অবস্থাকে আত্মস্থ করে গড়ে ওঠে অথবা বলা যেতে পারে, নির্ভর করে গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে একটি বাস্তব অবস্থা এবং অপরটি হচ্ছে বোধ এবং বিশ্বাসের অবস্থা। প্রাথমিক অবস্থার ক্ষেত্রে আবহাওয়া এবং প্রাপ্য উপকরণের গুরুত্ব অসীম। দ্বিতীয় অবস্থার জন্য ধর্মবিশ্বাস এবং সামাজিক রীতিনীতির গুরুত্ব অপরিহার্য। একটি দেশের কি ধরনের শিল্প গড়ে উঠবে তা নির্ভর করে সে দেশের অবস্থান এবং প্রাকৃতিক বিন্যাসের ওপর। মহেন-জো-দারোয় পাথর ছিল না। সেখানে সবকিছু ছিল মাটির। তেমনি সুমার দেশেও পাথর ছিল না, কাঠও ছিল না। তাই তারাও তাদের অট্টালিকা মাটি দিয়ে তৈরি করেছিল। কিন্তু পারস্যের অবস্থা ছিল ভিন্ন। পারস্যে পাথর ছিল প্রচুর। তাই সেখানে মাটির তৈরি অট্টালিকার কথা চিন্তাও করা যায় না।
 একিমিনীয় শিল্প-সম্ভারের একমাত্র নিদর্শন হচ্ছে তাদের প্রাচীন স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষগুলো। যেমন অ্যাসিরীয় রাজারা নিজেদের সৌভাগ্য এবং প্রতাপ চিহ্নিত করার জন্য রাজপ্রাসাদ এবং দুর্গ নিমার্ণ করেছিলেন, তেমনি একিমিনীয়রা রাজার প্রতাপ এবং প্রতিপত্তি চিহ্নিত করার জন্য বিরাট মহিমাময় এবং আড়ম্বরপূর্ণ রাজপ্রাসাদ নিমার্ণ করেছিলেন। যেহেতু একিমিনীয় সাম্রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং যাকে আমরা সেকালীন সভ্যতার সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য বলে আখ্যায়িত করতে পারি, তাই বিরাট সাম্রাজ্যের উপযোগী স্থাপত্য নির্মাণের প্রয়োজন তারা অনুভব করেছিল। এই প্রাসাদগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিরাট ছিল পার্সিপোলিসের প্রাসাদ। যার ধ্বংসাবশেষ আজো আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। পার্সিপোলিসের প্রাসাদের যে দীর্ঘ স্তম্ভগুলো আজো বিদ্যমান রয়েছে সেগুলোর উচ্চতা ছিল ৭০ ফুটের মতো। প্রাসাদের ভিত্তিভূমি-সিঁড়ি, বিভিন্ন দেয়াল, প্রবেশদ্বার এবং উচ্চ কলামগুলো প্রমাণ করে যে, সেকালের শিল্পীরা এমন একটা কিছু করতে চেয়েছিলেন তা দেব-দুর্লভ এবং অনন্যসাধারণ। পার্সিপোলিসের দীর্ঘ কলামগুলোর পাশে মানুষ যদি দাঁড়ায় তাহলে মানুষগুলোকে ক্ষুদ্রাকায় বামনের মতো দেখাবে। এই প্রাসাদ ছিল মানুষের স্বাভাবিক পরিমাপবোধের বাইরে। পৃথিবীর কোন সভ্যতায়ই এত বিরাট এবং বিপুলায়তনের চিহ্ন আমরা খুঁজে পাই না। এই রাজপ্রাসাদটি নির্মাণ করা হয়েছিল পাহাড়ের সানুদেশে এবং সে যুগের স্থপতিরা পাহাড়ের মহিমাময় এবং বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনার প্রেক্ষাপটে রাজপ্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন একটি অপরূপ দৃশ্যমান সঙ্গতিতে। আমরা দেখেছি যে, স্থাপত্যশিল্পে কলাম বা স্তম্ভ প্রাচীনকালে প্রাধান্য পেয়েছিল। এই প্রাধান্যের সূত্রপাত গ্রীকযুগ থেকে। গ্রীক শিল্পীরাই প্রথম মনোরম, বলিষ্ঠ, সুদৃশ্য কলাম নির্মাণ করেছিলেন। একিমিনীয়রা গ্রীকদের কাছ থেকেই এই কলামের ব্যবহার পায়। কিন্তু একিমিনীয়রা এই কলামকে একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়। পার্সিপোলিসের যে সমস্ত কক্ষ এবং প্রকোষ্ঠ নির্মিত হয়েছিল সেগুলোকে ধারণ করার জন্য মোট ৫৫০টি কলাম নির্মিত হয়েছিল। এটি এক ধরনের অবিশ্বাস্য অতিরিক্ততা বলা যায়। এত বেশি কলামের শৈল্পিক দিক থেকে কোন প্রকার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পারসিকরা এক প্রকার মহিমা সৃষ্টির জন্যই হয়ত এগুলো নির্মাণ করেছিলেন। শৈল্পিক দিক থেকে স্থাপত্য শিল্পে কলামকে একটা মোটিফ বলতে পারি। একটি মোটিফের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে পার্সিপোলিসের স্থপতিরা একটি অলংকরণের ব্যবস্থা ঘটিয়েছিলেন।পার্সিপোলিসের দেয়ালগাত্রে অথবা অধিরোহণীর পার্শ্বে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলো দর্শককে অভিভূত করে। প্রাচীন পারসিকদের ধর্মবিশ্বাসে ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে সংগ্রামটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সৎবুদ্ধি, ন্যায় এবং সৌন্দর্যের প্রতীক হচ্ছে ‘আহুর মাজদা’ এবং পাপ ও অসত্যের প্রতীক হচ্ছে ‘আহরিমান’। বিভিন্ন চিত্রে আহরিমানের পরাজয় এবং বিনাশ দেখানো হয়েছে এবং এর মাধ্যমে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে কল্যাণ কর্মে ন্যায়ের জয় হবেই এবং যথার্থ সংগ্রামে অন্যায় এবং পাপ বিমূঢ় হবে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। একটি চিত্রে দেখানো হয়েছে যে, ড্রাগনকে হত্যা করা হয়েছে। ড্রাগন সেখানে হিংস্রতা এবং ধ্বংসের প্রতীক। পারসিকদের শিল্পে আমরা প্রথম ঘোড়সওয়ারের মূর্তি দেখি। পরবর্তীকালে খ্রিস্টজগতের বিভিন্ন আইকনে ঘোড়সওয়ারের মূর্তি আমরা দেখতে পাই। এটা পারসিকদেরই দান। পাপ এবং পুণ্যের মধ্যে এভাবে ঘোড়সওয়ার মূর্তিকে ব্যবহার করা হয়েছে। ঘোড়সওয়ার বর্শার সাহায্যে বিরোধী শক্তিকে দমন করছে এই দৃশ্য পার্সিপোলিসে দেখা যায়। শিল্পসৌকর্য এবং দক্ষতার বিচারে আক্রমণরত ঘোড়সওয়ারের মূর্তিটি বিশিষ্ট শিল্প কৌশলের প্রমাণ বহন করে। ঘোড়ার গ্রীবাভক্তি এবং অশ্বপৃষ্ঠে অশ্বারোহীর আনত ভঙ্গি দু’টির মধ্য দিয়েই দক্ষ শিল্প কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।
একিমিনীয় শিল্প-সম্ভারের একমাত্র নিদর্শন হচ্ছে তাদের প্রাচীন স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষগুলো। যেমন অ্যাসিরীয় রাজারা নিজেদের সৌভাগ্য এবং প্রতাপ চিহ্নিত করার জন্য রাজপ্রাসাদ এবং দুর্গ নিমার্ণ করেছিলেন, তেমনি একিমিনীয়রা রাজার প্রতাপ এবং প্রতিপত্তি চিহ্নিত করার জন্য বিরাট মহিমাময় এবং আড়ম্বরপূর্ণ রাজপ্রাসাদ নিমার্ণ করেছিলেন। যেহেতু একিমিনীয় সাম্রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং যাকে আমরা সেকালীন সভ্যতার সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য বলে আখ্যায়িত করতে পারি, তাই বিরাট সাম্রাজ্যের উপযোগী স্থাপত্য নির্মাণের প্রয়োজন তারা অনুভব করেছিল। এই প্রাসাদগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিরাট ছিল পার্সিপোলিসের প্রাসাদ। যার ধ্বংসাবশেষ আজো আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। পার্সিপোলিসের প্রাসাদের যে দীর্ঘ স্তম্ভগুলো আজো বিদ্যমান রয়েছে সেগুলোর উচ্চতা ছিল ৭০ ফুটের মতো। প্রাসাদের ভিত্তিভূমি-সিঁড়ি, বিভিন্ন দেয়াল, প্রবেশদ্বার এবং উচ্চ কলামগুলো প্রমাণ করে যে, সেকালের শিল্পীরা এমন একটা কিছু করতে চেয়েছিলেন তা দেব-দুর্লভ এবং অনন্যসাধারণ। পার্সিপোলিসের দীর্ঘ কলামগুলোর পাশে মানুষ যদি দাঁড়ায় তাহলে মানুষগুলোকে ক্ষুদ্রাকায় বামনের মতো দেখাবে। এই প্রাসাদ ছিল মানুষের স্বাভাবিক পরিমাপবোধের বাইরে। পৃথিবীর কোন সভ্যতায়ই এত বিরাট এবং বিপুলায়তনের চিহ্ন আমরা খুঁজে পাই না। এই রাজপ্রাসাদটি নির্মাণ করা হয়েছিল পাহাড়ের সানুদেশে এবং সে যুগের স্থপতিরা পাহাড়ের মহিমাময় এবং বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনার প্রেক্ষাপটে রাজপ্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন একটি অপরূপ দৃশ্যমান সঙ্গতিতে। আমরা দেখেছি যে, স্থাপত্যশিল্পে কলাম বা স্তম্ভ প্রাচীনকালে প্রাধান্য পেয়েছিল। এই প্রাধান্যের সূত্রপাত গ্রীকযুগ থেকে। গ্রীক শিল্পীরাই প্রথম মনোরম, বলিষ্ঠ, সুদৃশ্য কলাম নির্মাণ করেছিলেন। একিমিনীয়রা গ্রীকদের কাছ থেকেই এই কলামের ব্যবহার পায়। কিন্তু একিমিনীয়রা এই কলামকে একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়। পার্সিপোলিসের যে সমস্ত কক্ষ এবং প্রকোষ্ঠ নির্মিত হয়েছিল সেগুলোকে ধারণ করার জন্য মোট ৫৫০টি কলাম নির্মিত হয়েছিল। এটি এক ধরনের অবিশ্বাস্য অতিরিক্ততা বলা যায়। এত বেশি কলামের শৈল্পিক দিক থেকে কোন প্রকার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পারসিকরা এক প্রকার মহিমা সৃষ্টির জন্যই হয়ত এগুলো নির্মাণ করেছিলেন। শৈল্পিক দিক থেকে স্থাপত্য শিল্পে কলামকে একটা মোটিফ বলতে পারি। একটি মোটিফের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে পার্সিপোলিসের স্থপতিরা একটি অলংকরণের ব্যবস্থা ঘটিয়েছিলেন।পার্সিপোলিসের দেয়ালগাত্রে অথবা অধিরোহণীর পার্শ্বে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলো দর্শককে অভিভূত করে। প্রাচীন পারসিকদের ধর্মবিশ্বাসে ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে সংগ্রামটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সৎবুদ্ধি, ন্যায় এবং সৌন্দর্যের প্রতীক হচ্ছে ‘আহুর মাজদা’ এবং পাপ ও অসত্যের প্রতীক হচ্ছে ‘আহরিমান’। বিভিন্ন চিত্রে আহরিমানের পরাজয় এবং বিনাশ দেখানো হয়েছে এবং এর মাধ্যমে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে কল্যাণ কর্মে ন্যায়ের জয় হবেই এবং যথার্থ সংগ্রামে অন্যায় এবং পাপ বিমূঢ় হবে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। একটি চিত্রে দেখানো হয়েছে যে, ড্রাগনকে হত্যা করা হয়েছে। ড্রাগন সেখানে হিংস্রতা এবং ধ্বংসের প্রতীক। পারসিকদের শিল্পে আমরা প্রথম ঘোড়সওয়ারের মূর্তি দেখি। পরবর্তীকালে খ্রিস্টজগতের বিভিন্ন আইকনে ঘোড়সওয়ারের মূর্তি আমরা দেখতে পাই। এটা পারসিকদেরই দান। পাপ এবং পুণ্যের মধ্যে এভাবে ঘোড়সওয়ার মূর্তিকে ব্যবহার করা হয়েছে। ঘোড়সওয়ার বর্শার সাহায্যে বিরোধী শক্তিকে দমন করছে এই দৃশ্য পার্সিপোলিসে দেখা যায়। শিল্পসৌকর্য এবং দক্ষতার বিচারে আক্রমণরত ঘোড়সওয়ারের মূর্তিটি বিশিষ্ট শিল্প কৌশলের প্রমাণ বহন করে। ঘোড়ার গ্রীবাভক্তি এবং অশ্বপৃষ্ঠে অশ্বারোহীর আনত ভঙ্গি দু’টির মধ্য দিয়েই দক্ষ শিল্প কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।
পারসিকদের ধর্মবিশ্বাসে পাপ এবং পুণ্যের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এবং বিভেদ চূড়ান্ত পর্যায়ে আনা হয়েছে। এই দুইয়ের মধ্যে চূড়ান্ত বৈপরীত্য বিদ্যমান ছিল। ইংরেজিতে যাকে বলে পোলারিটি, পারসিক ধর্মে পাপ এবং পুণ্যকে দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থিত বলে গণ্য করা হতো। আর্যদের দেবতা ছিল আলো। আলোর অধিকার হচ্ছে অন্ধকারকে দূর করা। এই আলোর অভিষেকের উদ্দেশে পারসিকরা বহু দেবতার কল্পনা করেছিল। অথবা সত্যের রক্ষক হিসাবে জ্বীনদের কথা কল্পনা করেছিল। পার্সিপোলিসের দেয়ালগাত্রে এই সমস্ত দেবতা এবং জ্বীনের মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। এ সমস্ত উৎকীর্ণ মূর্তির বাহুল্য পার্সিপোলিসে স্থাপত্যগত অলংকরণের একটি বৈশিষ্ট্য নির্মাণ করেছিল। সিংহ একটি ষাঁড়কে পরাভূত করছে- এ রকম দৃশ্য পার্সিপোলিসে আছে। এই দৃশ্যের অর্থ হচ্ছে সূর্য দেবতা ‘মিথরা’ অশুভ শক্তিকে পরাজিত করছেন।
একিমিনীয়দের শৈল্পিক নিদর্শনের মধ্যে সমাধি মন্দিরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সমাধি মন্দিরগুলো তারা একটি সুস্পষ্ট স্থাপত্যগত উচ্চারণে বিমণ্ডিত করেছে। পাসারগাদের অঞ্চলে কাইরুসের সমাধি মন্দির একটি দর্শনীয় স্থাপত্য নিদর্শন। নাসখ-ই-রুস্তমে এবং পার্সিপোলিসে যে সমস্ত সমাধি মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোর কারুকর্ম বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নাসখ-ই-রোস্তমে সম্রাট প্রথম দারায়ুসের সমাধি মন্দিরটি পাহাড় খনন করে নির্মাণ করা হয়েছে। সমাধিগাত্রে উৎকীর্ণ কিছু রিলিফ মূর্তি আছে যা সে যুগের শিল্প কুশলতার পরিচয় বহন করে। এ সমস্ত সমাধি মন্দিরে মিশরীয়দের মতো অনেক দামি তৈজসপত্র, মূল্যবান দ্রব্যাদি এবং অলংকার মৃতের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। এই মন্দিরগুলো অতীতে লুণ্ঠিত হয়েছে বহুবার। মনে হয় পারসিকরা মৃত্যুর পরের একটি জীবনে বিশ্বাস করত। অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর পর একটি বিশেষ সময় অতিক্রান্ত হলে মৃত ব্যক্তি পুনর্জাগরিত হবে। এই কারণেই প্রাচীন পারসিকরা বিশ্বাস করত যে, মানুষ যদি জীবিতকালে সৎগুণের চর্চা করে তাহলে পরবর্তী জীবনে তার মূল্য পাবে। এই কারণে পরবর্তী জীবনের অবস্থান এবং সাফল্যকে নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে সমাধি মন্দিরগুলোকে মহার্ঘ করে তারা নির্মাণ করত। নাসখ-ই-রুস্তম এবং পার্সিপোলিসের সমাধি মন্দিরগুলো প্রমাণ করে যে, পারসিকরা মনে করত যে, মৃত্যুর পরেও একটা জীবন আছে এবং সে জীবনের জন্য মৃতের সঙ্গে জীবন-যাপনের উপকরণ দিয়ে দেয়া প্রয়োজন। নাসখ-ই-রুস্তমের একটি সমাধিতে দেখা যায় যে, সম্রাট একটু উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান রয়েছেন যেন তিনি পৃথিবীতে তাঁর অধিকারের দিকে দৃষ্টিপাত করে আছেন। আরো মজাদার হলো যে সমস্ত উৎকীর্ণ শিলাচিত্র আমরা পাই তাতে দেখা যায় তাঁর সমগ্র মুখাবয়বের চতুর্দিকে একটা বৃত্তের বেষ্টনী আছে। এই বৃত্তটি অনন্তকালীনতার প্রতীক বহন করছে। মনে হয় প্রাচীন মিশরীয়দের দ্বারা একিমিনীয় পারসিকরা প্রভাবিত হয়েছিল। মিশরেও যেটা ছিল পাখাসংযুক্ত গোলাকার বৃত্ত, একিমিনীয়দের কাছে সেই বৃত্তটাই এসেছিল। কিন্তু পাখা দু’টি আসেনি।
যে যুগের কথা বলেছি সে যুগে পারসিক সাম্রাজ্য ছিল বিপুল বিস্তার এবং সমৃদ্ধির সাম্রাজ্য। এই বিপুল বিস্তার এবং সমৃদ্ধিকে চিহ্নিত করার জন্য পার্সিপোলিসের দেয়ালগাত্রের বাস-রিলিফ-এ অজস্র মানুষের মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। এই মূর্তিগুলো দেখে মনে হয় এগুলো যেন পটভূমির মধ্যে প্রায় প্রোথিতভাবে নির্মিত। এটাকে আমরা উঁচু উৎকীর্ণতা বলতে পারি। সম্রাট জীবিতকালে যে সমারোহের মধ্যে এবং অত্যুজ্জ¦ল দীপ্তির মধ্যে সিংহাসনে বসে রাজকার্য পরিচালনা করতেন শিল্পীরা এ সমস্ত উৎকীর্ণ মূর্তির সাহায্যে তারই একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। অ্যাসিরীয়দের উৎকীর্ণ শিল্পচিত্রে আমরা একটি বীভৎসতা এবং নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাই। সেখানে সম্রাটকে দেখা যায় ভোজসভায় আহার করছেন এবং তার সামনে শত্রুদের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। পারসিকদের বাস-রিফিল-এ কোন প্রকার বীভৎসতার চিহ্ন নেই। সেখানে দেখা যায় যে, অলংকৃত ফ্রিজগুলোতে রাজার অমাত্যগণ রাজাকে উপঢৌকন দেবার জন্য বহুবিধ সামগ্রী বহন করে নিয়ে চলেছে। এই ফ্রিজগুলোতে টেবলোর যে দৃশ্যগুলো আমরা পাই তাতে দেখা যায় যে, মূর্তিগুলো একে অন্যের হাত ধরে আছে, কেউ যেন ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের লোকের সঙ্গে কথা বলছে অথবা কেউ সামনের মানুষের ঘাড়ে হাত রেখেছে। এই দৃশ্যগুলো অপরূপ দক্ষতায় উৎকীর্ণ করা হয়েছে। প্রাচীনকালে এর সমতুল্য উৎকীর্ণ আর কোন সভ্যতার শিল্পসাধনায় আমরা পাই না। ফ্রিজের সব মূর্তি পার্শ্ব-অবস্থানে উৎকীর্ণ। কোন মূর্তির সম্মুখীন অথবা পশ্চাদের চিত্র আমরা পাই না। তবে এ সমস্ত দেয়ালগাত্রে নতুন নতুন দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।
পারসিকদের অন্য একটি প্রাচীন নগরী হচ্ছে সূসা। সূসা নগরীর অবস্থিতি এমন একটি পটভূমিতে ছিল যেখানে কোন পাথর ছিল না। এর ফলে সেখানকার বাড়িঘর ছিল পোড়ামাটির ইটের এবং উৎকীর্ণ মূর্তিও ছিল পোড়ামাটির। এখানে আমরা রং এর ব্যবহার পাই। রং এর সাহায্যে মূর্তিতে চকচকে ভাব আনা হয়েছে। নানাবিধ রং এর ব্যবহার তারা করেছিল। তাদের উৎকীর্ণ মূর্তিতে আমরা অদ্ভুত আকৃতির নানা ধরনের জীবজন্তুকে পাই এবং তীর নিক্ষেপরত ধনুকধারীকে পাই। তাছাড়া নানা আকৃতির পাখাযুক্ত মূর্তিকে পাই। এ সমস্ত কিছুই যেন স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তবে রেখাঙ্কিত হয়েছে। উৎকীর্ণ মূর্তিগুলো ছাড়াও সূসায় পূর্ণকায় বিভিন্ন মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে, যেমন ব্রোঞ্জনির্মিত সিংহ অথবা স্ফিংক্স? পার্সিপোলিসের মতো সূসাতেও বহু রাজকীয় প্রহরীর উৎকীর্ণ মূর্তিও আমরা পাই। পার্সিপোলিসে এগেুলো ছিল পাথরের ওপর উৎকীর্ণ। কিন্তু সূসাতে এগুলোকে পাচ্ছি পোড়ামাটির ইটের গায়ে। যে সমস্ত রং আমরা সূসায় পাই, সেগুলো হচ্ছে উজ্জ্বল নীল গিরি মাটির রসুন এবং হলুদ। এগুলো এখনও এত উজ্জ্বল যে, রৌদ্রের আলোতে জ্বলজ্বল করে ওঠে। পরবর্তীকালে পারস্যের ইসফাহানে মসজিদের উজ্জ্বল নীল টালির সঙ্গে প্রাচীন যুগের নীল রং-এর সঙ্গতি পাওয়া যায়। এই নীল রংটি পারসিক স্থাপত্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
প্রাচীন পারসিক সভ্যতার শিল্পসম্ভার আজও আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মহিমময়তায়, ঔজ্জ্বল্যে, সূক্ষ্ম কারুকার্যে বিবিধ রং-এর বৈশিষ্ট্যময় ব্যবহারে প্রাচীন পারস্যে স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য অনন্যসাধারণতার চিহ্ন বহন করছে। প্রাচীন বিভিন্ন সভ্যতার শিল্পচাতুর্যকে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় আপন শিল্পসত্তার অঙ্গীভূত করে তাঁরা যে নিদর্শনগুলো রেখে গেছেন, মহাকালের প্রেক্ষাপটে তা চির উজ্জ্বল থাকবে। সুমেরীয় রাজারা ছিলেন দেবতাদের প্রতিনিধি। ব্যাবলনীয় রাজারা ছিলেন সকল বস্তুর অধিকর্তা, কিন্তু প্রাচীন পারস্যে রাজারা ছিলেন রাজাদের রাজা। প্রাচীন পারসিকদের কল্পনায় রাজাকে রাজত্ব করার অধিকার দিয়েছিলেন আহুর মাজদা। যিনি রাজাদের রাজা হতেন তিনি হতেন বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি, যাঁর থাকত প্রচুর সৈন্য-সামন্ত এবং প্রচুর অশ্ব। রাজার রাজা ছিলেন ন্যায়াধি। তার রাজত্বে অগ্নি ছিল সমস্ত কিছু শুদ্ধিকরণের উজ্জ্বল উপাদান। সর্বাংশে না হলেও সেই প্রাচীন সাম্রাজ্যো ভগ্নাবশেষের মধ্যেই আমরা অভূতপূর্ব মহিমার নিদর্শন পাই।
ইসলামী শিল্পকলা
‘ইরান সর্বদাই চেষ্টা করেছে তার জাতীয় স্বকীয়তা নির্মাণকর্মের মধ্যে প্রস্ফুটিত করতে। এই স্বকীয়তাএসেছে তার অতীত থেকে। যে অতীতের ধর্মীয় চেতনাকে সে অস্বীকার করেছে, কিন্তু তার নির্মাণশিল্পকে গ্রহণ করেছে এবং সম্মান করেছে।’
৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে আরব অশ্বারোহীরা পূর্ণ বিক্রমে সাসানীয় সাম্রাজ্য আক্রমণ করল এবং ইরানের সমগ্র মালভূমি তাদের অধিকারে আনল। এক সময় মহামতি আলেকজান্ডরের হাতে একিমিনীয় সাম্রাজ্য পরাভূত হয়েছিল, তেমনি আরবদের হাতে সাসানীয় শক্তি নিশ্চিহ্ন হলো। দেশের দখল বিদেশীদের হাতে চলে গেল, কিন্তু তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধ্বংস হতে দিল না। ইসলাম ধর্ম তারা গ্রহণ করল। কিন্তু আরবদের ভাষাকে গ্রহণ করল না, তারা ফারসি ভাষাকেই তাদের জীবনে প্রচলিত রাখল।
ইসলামের বিজয়ের প্রাথমিক দিকে আরবরা ইরানে মসজিদ শিল্পের প্রতিষ্ঠা ঘটায়। উমাইয়াদের সময় যে ধরনের মসজিদ তৈরি হতো অবিকল সেই ধরনের মসজিদ ইরানে তৈরি হতে লাগল। উমাইয়া মসজিদের বিশেষত্ব ছিল যে, সেখানে একটি বিরাট অঙ্গনের চতুর্দিকে পোর্টিকোর ব্যবস্থা ছিল এবং নামাজের জন্য একটি আবরিত কক্ষের ব্যবস্থা ছিল। নবম শতকে আব্বাসী আমলে যে সমস্ত মসজিদ তৈরি হয়েছিল, সেগুলো সবই এ ধরনের ছিল। প্রথম প্রথম ইরানের দামগানে এবং নাঈনে এ ধরনের মসজিদ তৈরি হয়েছিল, কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে তারা নিজস্ব পদ্ধতিতে মসজিদ নির্মাণের সূত্রপাত ঘটাতে লাগল। ইরান তার অতীতের স্থাপত্যের নিদর্শন থেকে অনেক উপমা এবং ভাষা গ্রহণ করল। স্থাপত্যের ভাষায় যাকে ‘কীয়স্ক’ বলে প্রাচীন অগ্নিপূজার বেদীর থেকে তার নির্মাণকৌশল গ্রহণ করল এবং সাসানীয় যুগের অর্ডিয়েন্স হলকে ইসলামের প্রয়োজনে রূপান্তরিত করল। এই সংযোগটি রাজপ্রাসাদ-মসজিদ এবং মাদ্রাসার মধ্যে একটি সেতু-বন্ধন নির্মাণ করল। ইরানীয় রাজপ্রাসাদের এবং পরবর্তীকালে মাদ্রাসার মাঝখানে একটি চতুষ্কৌণিক কোড থাকত যার চতুর্দিকের অভ্যন্তরীণ দেয়ালে আইভান বা অর্ডিয়েন্স হলগুলো থাকত। একে অনেকটা ক্রুশাকার বা ‘ক্রুশিফর্ম প্ল্যান’ বলা হয়ে থাকে। ইরানীয়রা অতীতের পদ্ধতিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করতে সমর্থ হয়। মসজিদের মধ্যে কেবলা নির্দিষ্ট হয় এবং একটি ‘নিশ’ এর আকারে মেহরাব সংযুক্ত হয়। এক প্রকার বক্র খিলানের মধ্যে মেহরাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইরানীয় মসজিদ-স্থাপত্যে ভোল্ট এর ব্যবহার অনন্যসাধারণ। অনেক প্রকার খিলানের পারস্পরিক সংযোগে বিরাট খিলানের ভোল্ট-এর সৃষ্টি তারা করেছিল।
ইরান সর্বদাই চেষ্টা করেছে তার জাতীয় স্বকীয়তা নির্মাণকর্মের মধ্যে প্রস্ফুটিত করতে। এই স্বকীয়তা এসেছে তার অতীত থেকে। যে অতীতের ধর্মীয় চেতনাকে যে অস্বীকার করেছে, কিন্তু তার নির্মাণশিল্পকে গ্রহণ করেছে এবং সম্মান করেছে। অতীতের এই নির্মাণশৈলীর বৈশিষ্ট্য ছিল তার অগ্নিপূজার বেদীভূমির কৌশলগত নির্মাণ, সাসানীয় সাম্রাজ্যের অর্ডিয়েন্স হল এবং গম্বুজ শিল্প। ইরান ইসলামী শিল্পকলার ক্ষেত্রে নতুন ভঙ্গিতে এবং নতুন ভাষায় প্রাচীনকালের নির্মাণ পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছে। আমরা লক্ষ্য করি যে, ইসলামী স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ইরান গম্বুজকে নানাভাবে ব্যবহার করেছে এবং বহু খিলানের সমন্বিতরূপে ভোল্টের ব্যবহারকে প্রবল করেছে। ইরানকে অন্য কোন দেশ থেকে গম্বুজের কলাকৌশল গ্রহণ করতে হয়নি। ইটের তৈরি গম্বুজ ইরানে পূর্বেও ছিল, এমনকি বাসগৃহেও ছিল। ইতিহাস বলে, প্রার্থীয় এবং সাসানীয় সাম্রাজ্যের সময় গম্বুজের ব্যবহার নানাভাবে বিস্তৃত হয়। রাজপ্রাসাদ এবং মন্দিরের চূড়ায় গম্বুজের ব্যবহার ছিল। ইসলামের আগমনের পর ইরানের মুসলমান স্থপতিরা গম্বুজ এবং ভোল্টের ব্যবহার নতুনভাবে বিশুদ্ধ করেছে এবং এসব ক্ষেত্রে অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করেছে। পূর্বেকার গম্বুজগুলো চতুষ্কৌণিক ভিত্তির ওপর নির্মিত হতো। ইসলামের আগমনের পরে এই চতুষ্কৌণিক ভিত্তি বৃত্তাকারে পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন সাধনের ফলে গম্বুজের যেমন দৃশ্যগত পরিবর্তন সাধিত হয়, তেমনি নির্মাণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। ইরানের শিল্পীরা জ্যামিতিক সূক্ষ্ম বিচারের সাহায্যে তাদের গম্বুজ, খিলান এবং ভোল্টের উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। আমরা জানি, তাঁরা জ্যামিতিক কৌশলে বৃত্ত, অর্ধ বৃত্ত, চতুষ্কোণ এবং বহুবিধ কৌণিক ব্যঞ্জনা অট্টালিকার নির্মিতির মধ্যে অসাধারণ বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন। প্রাচীন গ্রীকরাও জ্যামিতিকে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তারা জ্যামিতির সাহায্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়নি। তারা ত্রিভুজের ব্যবহার করেছে এবং লম্ব রেখার ব্যবহার করেছে। ইরানের মুসলমান শিল্পীরা এ দু’টি ব্যবহারে সন্তুষ্ট থাকেননি। তাঁরা সমান্তরাল রেখা, লম্বরেখা, বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত, বক্ররেখা এবং নানাবিধ আকৃতি নিয়ে বিস্ময়কর পরীক্ষা করেছেন। এসব পরীক্ষার ফলস্বরূপ যে শিল্পস্বভাবের পরিস্ফুটন দেখি তা অতুলনীয়।
এভাবে ডোম এবং ভোল্ট নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিতে যাকে বলে ‘পেনডেনটিভ’ এবং ‘স্ট্যালাকটাইট’- সেই সমস্ত সূক্ষ্ম কারুকার্যের সম্মোহনী বিন্যাস ঘটিয়ে ইরান যে অসাধারণ শিল্প চাতুর্যের নিদর্শন সৃষ্টি করেছে তা আজও পরিশীলিত স্থপতি-বিজ্ঞানীদের কাছে অসাধারণ নির্মাণ-কৃতি হিসাবে পরিগণিত হয়। প্রাচীন গুহায় ছাদ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ে শুকিয়ে যেভাবে ঝুলন্ত দণ্ডের সৃষ্টি হয় তাকেই ‘স্ট্যালাকটাইট’ বলা হয়। ইরান তার মসজিদ এবং অন্যান্য ভবন নির্মাণ কাজের মধ্যে নানা রকম ‘স্ট্যালাকটাইট’ সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া মৌমাছির মধুচক্র বা চাকের মতো ছিদ্রবহুল ছোট ছোট খোপের সাহায্যে অদ্ভুত সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল। এগুলো ছিল নিছক সৌন্দর্যের জন্য, ব্যবহারের প্রয়োজনে নয়।
ইরানের ইসলামী শিল্পকে যদি আমাদের পরীক্ষা করতে হয়, তাহলে ইসফাহান শহরের দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে। ইসফাহান শহরটি একটি পরিকল্পিত শহর ছিল এবং এ শহরের মসজিদ পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে নগরের চতুর্দিকে বিস্তৃতি ঘটেছিল। একাদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইসফাহান নগরের স্থাপত্যগত বিকাশ ঘটে। সেলজুকদের আমলে এবং সাফাভীদের আমলে ইসফাহান ছিল ইরানের রাজধানী। ইসফাহানের প্রধান মসজিদই হচ্ছে ‘মসজিদ-ই-জামি’। সেলজুকদের আমলে এই মসজিদটি নির্মিত হয়। মালিক যখন সম্রাট, তখন ১০৭৩ থেকে ১০৯২ সালের মধ্যে এই মসজিদটি নির্মিত হয়। যথার্থ ইরানীয় পদ্ধতিতে এই মসজিদটি নির্মিত হয়। সাফাভীদের আমলে ১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দে ইসফাহান যখন পুনরায় ইরানের রাজধানীতে পরিণত হয় তখন সম্রাট শাহ আব্বাস ইসফাহানকে স্থাপত্যকলার দিক থেকে নতুন করে পুনর্গঠিত করেন। তিনি ‘মায়দান-ই-শাহ’ নামক একটি বিরাট রাজকীয় কমপ্লেক্স নির্মাণ করেন। উক্ত কমপ্লেক্সে চল্লিশটি কলাম বা পিলারের ওপর একটি প্রাসাদ নির্মিত হয় এবং ‘আলী কাপু’ নামক অন্য একটি প্রাসাদ ময়দানের নিকটে নির্মিত হয়। এই কমপ্লেক্সে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল শেখ লুৎফুতউল্লাহ মসজিদ। অন্য একটি মসজিদ ছিল যাকে ‘শাহের মসজিদ’ বলা হতো। এই ‘শাহের মসজিদ’ হচ্ছে ইরানের একটি অনন্যসাধারণ স্থাপত্য কীর্তি। এই মসজিদের মধ্যে একটি চতুষ্কৌণিক আয়তক্ষেত্র ছিল যার চারপাশে ভোল্ট আকৃতির ৪টি মেহরাবের মতো নির্মিতি ছিল। এই নির্মিতিগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত। মসজিদ এলাকার অভ্যন্তরে মাদ্রাসার জন্য দু’টি স্থান নির্দিষ্ট ছিল। শিল্পকলার দক্ষ এবং কৌশলগত অভিনিবেশ এই মসজিদকে শুধু ইরানের কেন, সমগ্র বিশ্বের একটি অলোকসামান্য কীর্তি হিসাবে গণ্য করা যায়। ময়দানে শাহের অভ্যন্তরে মসজিদ-ই-শাহ একটি অনন্যসাধারণ স্থাপত্য কীর্তি। ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় ইরানের নিজস্ব স্থাপত্য ভাষায়। মাঝখানে একটি আয়ত ক্ষেত্র যাকে ইংরেজিতে ‘কোর্ট’ বলে এবং চারপাশে ‘পোর্টিকো’। পোর্টিকোগুলোর ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে ৪টি আইভানের দ্বারা। এই পদ্ধতিটা ইরানের নিজস্ব পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটি বহাল রেখে বহুবিধ কারুকার্য সম্পাদন করা হয়েছে। এসব কারুকার্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, সাফাভীরা স্থাপত্যে অলংকরণের ক্ষেত্রে সকল কুশল প্রয়োগ করেছিল। এই মসজিদের সমগ্র নির্মাণকর্মটি এমনভাবে সম্পূর্ণ করা হয়েছে যাতে একটা পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য অনুভব করা যায়। নির্মিতিটি সকল দিক থেকেই সমভাবে এবং সুসমঞ্জস পূর্ব ও পশ্চিম দিকের দুই আইভান অবিকল এক রকম এবং প্রতিটি আইভান দিয়ে অগ্রসর হয়ে আমরা একটি করে গম্বুজের ছাদবিশিষ্ট একটি করে কক্ষ পাই। দক্ষিণ দিকের আইভানটি অন্য দু’টি আইভানের চেয়ে বড় এবং এই আইভান দিয়ে আমরা উপাসনা-গৃহের পবিত্রতম অংশে প্রবেশ করি। এই অংশেই মেহরাব অবস্থিত এবং এই অংশের গম্বুজটি তার বেইজ থেকে ক্রমশ প্রসারিত হয়ে ওপরে মিলিত হয়েছে কিছুটা ঘোড়ার খুরের নালের মতো। উপাসনা কক্ষের দু’টি উন্মুক্ত কক্ষ রয়েছে। প্রধান আইভানের দু’পাশে দু’টি মিনার উঠে গেছে। সামগ্রিকভাবে নির্মাণ কৌশলের দিক থেকে এ মসজিদটি একটি সমগ্রতা, একটি সম্পন্নতা, ভারসাম্য এবং দক্ষ বিভাজনে একটি অপূর্ব মহত্ত্বব্যঞ্জক সৃষ্টি। এই মসজিদের ভিতরকার মিনা করা কারুকার্যগুলো আলোকসম্পাতে অসাধারণ দীপ্তিমান হয়ে দেখা দেয়। মিনা কারুকার্যের মধ্যে উজ্জ্বল নীল, ফিরোজা এবং হলুদের ব্যবহার খুবই সুন্দর। লতানো কারুকার্যগুলো বিচিত্র শোভার সৃষ্টি করেছে। গম্বুজের বেষ্টনীতে ‘কুফী’ হরফে কুরআন শরীফের আয়াত লিখিত হয়েছে। মসজিদের মূল গম্বুজের ওপরের বেষ্টনীতে নীল, হলুদ লতাপাতাগুলো পরস্পর সংলগ্ন হয়ে একটি চমৎকার দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। গম্বুজের মধ্যভাগের সামগ্রিক বেষ্টনীতে নীলের ওপর সাদা ব্যবহার করে কুরআন শরীফের আয়াত খচিত আছে। গম্বুজের সর্বনিম্নভাগ কয়েকটা খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত করে আল্লাহর বিভিন্ন নামে অলংকরণ নির্মাণ করা হয়েছে। গম্বুজের বহির্বিভাগটি যেমন সুন্দর, অভ্যন্তরীণ কারুকার্যও তেমনি সুন্দর। অভ্যন্তরভাগে একবারে ওপরের ছাদে চক্রাকারে একটি ফুলের পুনরাবৃত্তি তৈরি করা হয়েছে এবং তার নিম্নে মৌমাছির ঝুলন্ত কারুকার্য আমাদের অভিভূত করে। ইটের সাহায্যে অসাধারণ অভিনিবেশের সাহায্যে মৌচাক সদৃশ আকৃতিগুলো বিন্যস্ত করা হয়েছে।
এই মসজিদের ভোল্টগুলো অনেকগুলো খিলানের সাহায্যে এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যাতে মনে হয় যে, একটি আটমুখী তারা ভোল্টের ৮টি দিকে তার আলো ছড়িয়েছে। ভোল্টের জ্যামিতিক বিন্যাস এবং বিস্তার নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করব না। শুধু এ কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, এই ভোল্টগুলো একই সঙ্গে স্থাপত্যগত দক্ষতা এবং শিল্পগত মনোজ্ঞ বিন্যাসের পরিণতি। যেভাবে খিলানগুলো পরস্পরের সংলগ্ন হয়ে একটি আচ্ছাদন নির্মাণ করেছে তাতে একই সঙ্গে ভারসাম্য এবং দক্ষ নির্মিতি-কৌশলের পরিচয় দেয়। ভোল্টের অভ্যন্তরে আলোর বিকিরণের ব্যবস্থাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আইভানের শেষের দিকে যে অর্ধ গম্বুজের ভোল্টিং রয়েছে তা পারস্যের স্থপতিদের সুচারু দক্ষতার পরিচয় দেয়। একটি গম্বুজকে মাঝখানে কেটে দু’খ- করলে যে অর্ধবলয় নির্মিত হয় সে আইভানটি এমনভাবে গঠিত যে, দর্শকের জন্য তা বিস্ময়-বিমূঢ়তার সৃষ্টি করে। এই অর্ধগম্বুজ নির্মাণের ক্ষেত্রে পারস্যের স্থপতিরা বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে তাদের সামনে অজস্ত্র বিকল্প ছিল- এই প্রমাণ আমরা পাই নানাবিধ আইভানের মধ্যে। আইভানগুলো সবই এক রকমের নয়।
শাহ আব্বাস যে সমস্ত স্থপতি নিযুক্ত করেছিলেন, এক কথায় তাদের বলা যায় ‘মাস্টার বিল্ডার্স’, সাধারণ ভাষায় অসাধারণ দক্ষ নির্মাণকারী। নির্মাণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত জটিল সমস্যার সম্মুখীন তাঁরা হয়েছিলেন সেগুলোর সমাধান তাঁরা করেছিলেন বিচিত্রভাবে। এ সমস্ত নির্মাণগত সমস্যা ছিল অত্যন্ত জটিল। তাঁরা এই সমস্ত জটিল সমস্যার সমাধান করে নির্মাণগত ‘ভার্চুয়াসিটি’ অর্থাৎ আঙ্গিকগত দক্ষতার যে পরিচিতি দিয়েছেন তা আজকের বৈজ্ঞানিক যুগের নির্মাতাদের কাছেও অভূতপূর্ব মনে হয়। খিলানের সভঙ্গ আকৃতিগুলো যে জটিল যুক্তি বিচারে একে অন্যের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে ওপরের ছাদ নির্মাণ করেছে তা অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ।
গম্বুজ আকৃতির নির্মিতি আমরা অনেক দেখেছি বাইজানটাইন শিল্পে। গম্বুজের আকৃতি অসাধারণ শোভনতা এককালে প্রকাশিত হয়েছিল আমরা জানি। ওসমানীয় তুর্কীরা বাইজানটাইন শিল্প প্রকৃতি অবলম্বন করে গম্বুজধারী বহু মসজিদ নির্মাণ করে গেছেন। সে সমস্ত গম্বুজ নির্মাণগত দিক থেকে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় বহন করে। ইরানের গম্বুজ কিন্তু কোনক্রমেই তুর্কী গম্বুজের দ্বারা প্রভাবিত নয়। বহুকাল ধরে ইরানের মানুষ তাদের বাসগৃহে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের জন্য একপ্রকার গম্বুজ ব্যবহার করে এসেছে। সুতরাং গম্বুজটা ইরানের নিজস্ব ভার্নকুলার বা শিল্পভাষার অন্তর্গত। ইরান নিজস্ব ঐতিহ্য থেকেই গম্বুজের ধারণা পেয়েছে এবং তাদের মসজিদে সেই গম্বুজ তারা ব্যবহার করেছে। দৃশ্যত বাইজানটাইন গম্বুজ এবং ইরানী গম্বুজের মধ্যে পার্থক্য আছে। নির্মাণ পদ্ধতিতে এদের উভয়ের জটিলতা ব্যাখ্যা না করে বলা যায় যে, এই দুই গম্বুজ রীতিগতভাবে ভিন্ন প্রকৃতির।
ইরানে মসজিদের অলংকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মিনার কাজ অত্যন্ত সুন্দর। এই মিনার কাজের সাহায্যে যে সমস্ত আকৃতি গঠিত হয়েছে সেগুলো উজ্জ্বল চাকচিক্যে অসাধারণ কুশলতার পরিচয় বহন করে। পাকা ইটের ওপর মিনার কাজ করা হয়েছিল। সেলজুক যুগে রং এর ব্যবহার তেমন প্রবল ছিল না। কিন্তু আব্বাস তাঁর শিল্প সচেতনতার সাহায্যে অট্টালিকায় মিনার চাকচিক্যের বৈচিত্র্যে আনলেন। আইভানের খিলানগুলো এবং গম্বুজগুলো নানা রং-এর মোজাইকে তিনি অলংকৃত করলেন ঘন নীল, ওকার বা হালকা হলুদ এবং হলুদ। এই রং এর কাজগুলোর ওপর কালো এবং সাদা রং-এর আরবি অক্ষরগুলো লেখা হয়েছিল। ‘পলিক্রম’ বা বহুবর্ণের ব্যবহার সাফাভী আমলে মসজিদগুলোতে এত সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণভাবে করা হয়েছে যে, মসজিদের দেয়াল, মেঝে, গম্বুজের অভ্যন্তর, আইভানের অভ্যন্তর এবং পোর্টিকোতে কোথাও রংবিহীন খালি জায়গা নেই। এক্ষেত্রেও বাইজানটাইন এবং রোমের মোজাইক থেকে তা ভিন্নতর। রোম এবং বাইজানটাইনে রং-এর ব্যবহার ছিল অসম্ভব সীমাবদ্ধ, কিন্তু সাফাভীদের রং-এর ব্যবহার এত সমগ্র এবং সম্পূর্ণ যে, দর্শকের মনে এক প্রকার মোহগ্রস্ততা এবং তন্ময়তা সৃষ্টি করে। সাফাভীদের আমলে তৈরি ইসফাহানের ইটের অট্টালিকাগুলো সামগ্রিকভাবে বহুবর্ণের পরিমার্জনীয় উজ্জ্বল। পৃথিবীতে কোন যুগে কোন দেশে স্থাপত্যকর্মের ইতিহাসে পলিক্রমের এমন সামগ্রিক ব্যবহার আর নেই। স্থাপত্যের নিদর্শনের দিক থেকে ইসফাহান লালিত্যে, মাধুর্যে এবং মহার্ঘতায় একটি চিরকালীনতার স্বাক্ষর রেখেছে যা অতুলনীয় এবং অনন্যসাধারণ।
ইসফাহানের এই গৌরব দীর্ঘকাল পর্যন্ত ছিল এবং এখনও আছে। এখন ইসফাহান বিখ্যাত তার কার্পেট শিল্পে, হস্তশিল্পে এবং ছাপ-চিত্রে। ইসফাহানের এই সমস্ত ছাপ-চিত্রশিল্পীকে ‘কলমকর’ বলা হয়। এই ‘কলমকরগণ’ তাঁদের সুনিপুণ হস্তশিল্পের কারুকার্যে বিশ্ববিখ্যাত। সেজন্যই সৌন্দর্য-পিপাসু শিল্প-রসিকরা ইসফাহানেরকে ‘অর্ধ পৃথিবী’ বলে থাকেন। ইসফাহানের অট্টালিকায় রৌপ্যধাতুর অভ্যন্তরীণ সজ্জায় প্রস্তরগুলো বিভূষিত এবং বিচিত্রিত হয়েছে।
পারস্য শিল্প বিশেষ করে স্থাপত্য শিল্প আজও তার প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। আধুনিক সময়ের একটি দাবি হচ্ছে, নির্মিত গৃহকে বাসযোগ্য করা অর্থাৎ প্রয়োজন সিদ্ধতাই বর্তমানে স্থাপত্য শিল্পে আদর্শ। এর ফলে আধুনিককালে সকল দেশেই একটা চেষ্টা চলছে। বর্তমানকালের ব্যবহারিক জীবন এবং দ্রুতগতি সময়ক্ষেপণের সঙ্গে সমন্বিত করা। কিন্তু ইরানই একমাত্র দেশ যে তার ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করছে এবং আধুনিককালেও তার প্রবাহকে বিদ্যমান রাখছে। দু’টি ক্ষেত্রে ইরান তার প্রাচীন সংস্কার এবং কৌশলকে পূর্ণ মর্যাদায় সংরক্ষিত রাখছে। এ দু’টি ক্ষেত্র হচ্ছে সমাধি মন্দির এবং মসজিদ। আচ্ছাদিত গম্বুজধারী অলংকৃত সমাধি-মন্দির আজও ইরানে তৈরি হচ্ছে। ইমাম খোমেইনীর মুসলিয়ামটি এর একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তবে অতীতের মতো সম্ভ্রান্ত এবং মহার্ঘ বিপুলায়তনে মসজিদ নির্মাণ এখন আর হচ্ছে না। সেটা আর সম্ভবপর নয়। মসজিদের নির্মাণ কৌশলের মধ্যে একটি সহজতা এসেছে এবং ‘মিনার’ কাজ থাকলেও তা ব্যাপক নয়। তবে ইরান তার সকল পুরানো মসজিদ এবং মুসলিয়ামগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে যাচ্ছে এবং লক্ষ্য করে যাচ্ছে যাতে তাদের পুরানো সৃষ্টির গৌরব এবং ঔজ্জ্বল্যের অবক্ষয় না ঘটে।