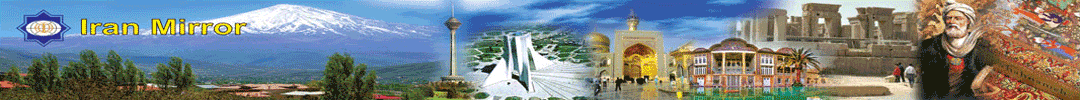সিনেমাকে কিভাবে দেখব
পোস্ট হয়েছে: এপ্রিল ২২, ২০১৮
অধ্যাপক মাসউদ সোফলায়ীর কর্মশালা-
সিনেমাকে কিভাবে দেখব
সাইয়্যিদ শাহজাদা আল কারীম*
খ্রিস্টের জন্মের বহু বছর পূর্ব থেকে পৃথিবীতে শিল্প-সাহিত্যসমৃদ্ধ যে জাতির অস্তিত্ব সেই পারস্য জাতিই আজকের ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান। যুগে যুগে বহু জাতি অন্য জাতির করায়ত্ত হয়েছে, কিন্তু এ ভূখণ্ডের জনগণ অনেক ক্রান্তি কালেও কারো কাছে মাথা নত করে নি। সেই পারস্য জাতি ইসলামি বিপ্লবের পরে বর্তমানে বিশ্বের কাছে এক নতুন আঙ্গিকে পরিচিত। নানা দিকে স্বকীয়তা বজায় রাখার সাথে সাথে চলচ্চিত্র জগতেও ইরান করেছে নিজস্ব ধাঁচের প্রকাশ।
ইরানি নাটক, সিরিয়াল, আর্টফিল্ম, সিনেমা আজ একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর সকল ফিল্ম ফেস্টিভালে দাপটের সাথে বিচরণকারী ইরানি চলচ্চিত্রকে অস্ট্রেলিয়ান ফিল্মমেকার মিশেল হেনেক ও জার্মান ফিল্মমেকার ওয়ার্নার হারজক One of the world most important artistic Cinema হিসেবে অভিহিত করেছেন। ১৯৯২ সালে চীনে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয়েছিল ইরানি চলচ্চিত্র। বাংলাদেশের সকল ফেস্টিভালে ইরানি চলচ্চিত্রের সাবলীল বিচরণ এবং বাংলায় ডাবিংকৃত ইরানি চলচ্চিত্র মানেই টিভি সেটের সামনে পুরো পরিবারের উপস্থিতি যা সুস্থ সংস্কৃতির প্রতি সমর্থনেরই পরিচায়ক। এসব কিছু কিন্তু বিপ্লবের দর্শনে বিশেষ কোড মেনেই হচ্ছে। এতে সিনেমার শিল্পমান, অ্যাকশন ও ইমোশান ক্ষুণ্ণ হয়নি। নৈতিকতা, মানবিকতা, প্রকৃতি ও শিশুদের ব্যাপক উপস্থিতি ইরানি চলচ্চিত্রে লক্ষ করা যায়। আরেকটি দিক এখানে বলতেই হবে, এসব চলচ্চিত্রে আক্ষরিকভাবে ধর্মীয় কোন নির্দেশনা বা ডায়ালগ সাধারণত দেখা যায় না। তবে উপন্যাস ও চরিত্রনির্ভর প্রতিটি ফিল্ম থেকে মানুষ কিছু না কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে যা পৃথিবীর অনেক বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি বিশ্বকে দিতে পারে নি।
ইরানের চলচ্চিত্রের কথা বললেই আমাদের মনে আসে আব্বাস কিয়ারোস্তামি, মাজিদ মাজিদি, জাফর পানাহী, আসগর ফরহাদিসহ আরো কিছু বিশ্বনন্দিত নাম। সুশীল ও নৈতিক কোড মেনেই কীভাবে মনোগ্রাহী দৃশ্য নির্মাণ করা যায়, মরুভূমিতে কীভাবে ফুল ফোটানো যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ যেন ইরানের চলচ্চিত্র। যে কোন বিষয়েই উচ্চ অবস্থানে পৌঁছতে হলে ব্যবহারিক জ্ঞানের পাশাপাশি তাত্ত্বিক জ্ঞানের সমন্বয় প্রয়োজন। ঠিক সেকথার সার্থকতা প্রমাণ করতেই যেন আজ থেকে প্রায় তিপ্পান্ন বছর পূর্বে ১৯৬৪ সালে তেহরান ইউনিভার্সিটি অব আর্ট এ সিনেমা ও থিয়েটার বিভাগ চালু হয় যা পরবর্তীকালে দুটি আলাদা বিভাগে বিভক্ত হয়।
বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের শুরু অনেক পূর্বে হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক পড়াশোনার চলনটা একেবারে নতুন বললেই চলে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম ২০১২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন নামে একটি বিভাগ চালু হয় যা বর্তমানে টেলিভিশন, ফিল্ম ও ফটোগ্রাফি বিভাগ নামে পরিচিত।
চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে অনেকাংশেই সঙ্গতিসম্পন্ন ইরানের মাধ্যমে বৈশ্বিক চলচ্চিত্রের সাথে দেশীয় চলচ্চিত্রের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়গুলোর সমন্বয় সাধনের প্রয়াসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন, ফিল্ম ও ফটোগ্রাফি বিভাগ আমন্ত্রণ জানায় তেহরান আর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেমা বিভাগের বর্তমান চেয়ারপার্সন প্রফেসর মাসউদ সোফলায়ীকে।
ইরান কালচারাল সেন্টারের যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ধারাবাহিকতায় ৮ জানুয়ারি বাংলাদেশে আসেন তিনি। উদ্দেশ্য তাঁকে নিয়ে বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর দুটি ব্যাচের সাথে পাঁচ দিন করে দশদিনের কর্মশালার আয়োজন করা। স্যারকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আনতে যাই আমরা তিনজন- আশিক, মমিনুল ভাই আর আমি।
মজার একটা ঘটনাও ঘটে তখন। এয়ারপোর্টে আমরা তিনজন তিন জায়গায় স্যারের নাম লিখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। একটু পরে আশিক এসে বলল : ‘স্যার চলে এসেছেন, দেখা হয়েছে, ভেতরে আছেন।’ মমিনুল ভাই সামনে এক ইরানি ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন : ‘ইনিই স্যার।’ আমার একটু খটকা লাগলো। কারণ, নেটে সার্চ দিয়ে স্যারের ঝকঝকে কোন ছবি না পেলেও যা পেয়েছিলাম সেই ছবির সাথে এই ভদ্রলোকের কোন মিল নেই। যাই হোক, কিছুক্ষণ পর ইরান কালচারাল সেন্টার থেকে ফোন পেয়ে জানতে পারলাম স্যারকে শুভেচ্ছা জানাতে ইরান কালচারাল সেন্টারের পক্ষ থেকে এসেছেন সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা জনাব জাওয়াদি। বুঝলাম সামনের ভদ্রলোকটিই জনাব জাওয়াদি। আমাদের বুঝতে ভুল হয়েছিল। একটু পর স্যার ইমিগ্রেশন পেরিয়ে আসলেন আর আমরা তাঁকে নিয়ে চললাম ঢাকা ক্লাবের উদ্দেশে। যাবার পথেই স্যারের সাথে অনেক বিষয় আলোচনা হলো। জানলাম তিনি বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নিয়ে অনেক আশাবাদী। জানতে চান এখানকার বর্তমান অবস্থার কথা, শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করতে চান বিশ্বের নানা প্রান্তের চলচ্চিত্র নিয়ে।
স্যার যে কদিন ছিলেন, স্যারের গাইড হিসেবে দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। প্রতিদিন ক্লাসের আগে স্যারকে ঢাকা ক্লাবের গেস্ট হাউস থেকে নিয়ে আসা, ক্লাসের পর পৌঁছে দেয়া, এছাড়া ঢাকার ঐতিহ্যবাহী কিছু জায়গায় স্যারকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি ছিল আমার কাজ, যে কারণে স্যারকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ ঘটেছিল।
স্যারের সম্পর্কে বলতে গেলে, প্রথমত স্যার খুব সুন্দর মনের একজন মানুষ। শিক্ষার্থীদের সাথে তাঁর আচরণ যেন বন্ধুত্বের পর্যায়ের। যেমন সিনেমার শিক্ষক, তেমনি তিনি নিজেও সিনেমা বানান। এপর্যন্ত তিনি সবমিলিয়ে প্রায় ২০০ সিনেমা সম্পাদনার কাজ করেছেন। এছাড়া নিজের পরিচালনায় তাঁর আছে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র। স্যারের ভাষ্যমতে একজন শিল্পীর প্রথম যে বিষয়টা থাকা দরকার সেটা হচ্ছে তার মানবীয় গুণ, বিবেকবোধ; নিজের মনের মধ্য দিয়ে অন্যের অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করে নিজেকে ঐ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারার ক্ষমতা। তারপর তা নিজের শিল্পবোধের মাধ্যমে প্রকাশ করা। দেখলাম স্যারকে নিয়ে যখনই শাহবাগের ওভারব্রিজের উপর দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছি তখনই তিনি ওভারব্রিজে বাস করা ঘরহীন মানুষদের দেখে অস্বস্তি বোধ করছেন, বলছিলেন ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যেখানে তিনি হোটেল রুমে বসে ঠা-ায় কাঁপছেন সেখানে খোলা জায়গায় ঠান্ডা বাতাসে এরা কীভাবে বেঁচে আছে! শেষ পর্যন্ত একদিন তিনি বলেই ফেললেন : ‘আমরা ওভারব্রিজ দিয়ে না গিয়ে অন্য কোনো ভাবে যেতে পারি?’
ক্লাসে স্যার দেখালেন কীভাবে একটি সিনেমার প্রতিটি ফ্রেম ধরে বিশ্লেষণ করা যায়, কীভাবে একটি আইডিয়া থেকে ধীরে ধীরে একটি চমৎকার চলচ্চিত্র তৈরি হয়, কীভাবে চলচ্চিত্রে ফিল্ম লুক দেয়া যায়, মোড ক্রিয়েট করা যায়, সম্পাদনার টেবিলে কী করে ধারণকৃত চিত্রগুলোকে নতুন রূপ দেয়া যায় ইত্যাদি নানা বিষয়। তিনি বলছিলেন : ‘সিনেমার জন্ম পাশ্চাত্যে এবং তাদের সিনেমার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের প্রাচ্যের মানুষ যখন সিনেমা তৈরি করব, তখন আমরা পাশ্চাত্যের কাছ থেকে শিক্ষা নেব ঠিকই, কিন্তু আমাদেরকে আমাদের গল্প নিজেদের ভাষায় বলতে পারতে হবে আর তখনই সেটা আমাদের সিনেমা হয়ে উঠবে।’
ইরানের সিনেমা যেহেতু ইতোমধ্যেই নিজেদের ধারা তৈরি করেছে সেকারণে স্যার দেখাচ্ছিলেন কোন কোন দিক দিয়ে ইরানের সিনেমা পশ্চিমের সিনেমা থেকে আলাদা। ইরানের সিনেমার গল্প বলার ধরনে মূলত পরিবর্তন এনেছে চারটি বিষয়। স্থান, চরিত্র, ভাষা আর দৃশ্য পরিকল্পনা। স্থান বা লোকেশনের দিকে ইরানের চলচ্চিত্রে বিশেষ করে অ্যাকচুয়াল লোকেশন এর ব্যবহার, চরিত্রের ক্ষেত্রে ভিন্ন ধারার চরিত্র বা ভিন্ন বৈশিষ্ট্যস¤পন্ন চরিত্র যাকে বলা হয় ত্রিমাত্রিক চরিত্র এবং চরিত্রের চিত্রায়নে সহজ ভাষা ব্যবহার বেশি লক্ষ্য করা যায়। ভাষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতা পরিহার এবং দর্শকদের বোঝার সুবিধার্থে সহজ শব্দের ব্যবহার এবং সংলাপের বিশেষায়ন ইত্যাদি লক্ষণীয়। দৃশ্য পরিকল্পনায় নিজেদের সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরাসহ নিজেদের চিত্রকর্ম, আলোকচিত্র থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে চিত্র পরিকল্পনা প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়া মুসলিম দেশ হিসেবে সেন্সরশিপের নিয়ম অনুযায়ী সিনেমা বানাতে গিয়ে পরিচালকরা এমনভাবে গল্প বলেছেন যেখানে নারী পুরুষের অন্তরঙ্গ দৃশ্য দেখানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় না। আর এটা করতে গিয়ে তাদের হতে হয়েছে আরো বেশি সৃজনশীল যা ঐ চলচ্চিত্রগুলোকে বিশ্ব চলচ্চিত্রের আসরে অনন্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
সার্জিও লিওনির চলচ্চিত্র ‘দ্য গুড, দ্য ব্যাড অ্যান্ড দ্য আগলি’ (১৯৬৬) এর শেষ সিকোয়েন্সে কীভাবে ক¤েপাজিশন, কালার আর ক্যামেরার কাজের মাধ্যমে ক্লাইমেক্স ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তার ফ্রেম ধরে ধরে স্যার বুঝিয়ে বললেন। এছাড়া দ্যামিয়েন শ্যাজেলের চলচ্চিত্র ‘হুইপল্যাশ’ (২০১৪) এর স¤পূর্ণ ছবিতে ফ্লেচার আর অ্যন্ড্রু এর মধ্যকার দ্বন্দ্ব, চিন্তা আর স¤পর্ককে কীভাবে আলো, ফ্রেমিং আর সংগীত এর সাহায্যে স¤পাদনার দক্ষতায় অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেটাও ব্যাখ্যা করলেন স্যার দীর্ঘ সময় ধরে। এছাড়াও ‘এ সেপারেশন’ (২০১১), ‘দ্য সেল্সম্যান’ (২০১৬), সেভিং প্রাইভেট রায়ান’ (১৯৯৮) সহ বেশ কয়েকটি সিনেমা নিয়েও আলোচনা করলেন।
চলচ্চিত্রের এরূপ ব্যবচ্ছেদ এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম ভালো সিনেমার কোন কিছুই বিনা কারণে করা হয় না। কোন একটি ফ্রেম কেন নেয়া হবে তার পেছনে থাকতে যথার্থতার বিবেচনাটা করতেই হবে।
শেষদিনে স্যার বোঝালেন কালার কারেকশন আর কালার গ্রেডিং এর পার্থক্য আর সিনেমায় এর প্রয়োজনীয়তা, হাই ডায়নামিক রেঞ্জ (এইচডিআর) এর বিশেষত্ব আর ক্যামেরাভেদে এর পার্থক্য। এছড়াও এলইউটি বা লুক আপ টেবিল প্লাগইনের সাহায্যে স¤পাদনায় ফিল্ম লুক পরিবর্তনের খুঁটিনাটিও তুলে ধরলেন।
কর্মশালার ফাঁকে ফাঁকে কেমন কী চলছে তার নিয়মিত খোঁজ রেখেছেন বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক হায়দার রিজভী স্যার। যিনি আমাদের সবসময় বলেন চলচ্চিত্র নির্মাণে সবার আগে দরকার মাথা। চিন্তার প্রাচুর্য না থাকলে চলচ্চিত্র হয় না।
ভালো চলচ্চিত্র নির্মাণে যেমন প্রয়োজন মেধা তেমনি প্রয়োজন শ্রমের। মাসউদ স্যার বলছিলেন বিভিন্ন সিনেমার উদাহরণগুলো একারণে দেয়া যেন সেগুলো আমাদের বাংলা চলচ্চিত্র তৈরির সময়ে আমরা আমাদের মতো করে ব্যবহার করতে পারি।
¯স্নাতক চতুর্থ বর্ষের ২৫ জন শিক্ষার্থীর আমরা প্রায় ২৩ জন নিয়মিত উপস্থিত ছিলাম। স্যার সম্পর্কে বন্ধু আশিক বলছিল স্যারের বৈশিষ্ট্য এখানে অতুলনীয় যে, স্যার আমাদের যা বলছেন সেগুলো জানতে স্যারের হয়তো অনেক সাধনা করতে হয়েছে, কিন্তু আমাদের এমনভাবে তিনি বিষয়গুলো বোঝাচ্ছেন, মনে হচ্ছে এগুলো খুবই সহজ আর সেকারণেই বিষয়গুলো মাথায় গেঁথে যাচ্ছে।
স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ৩২ জন শিক্ষার্থীর প্রায় ২৮ জন ছিলেন নিয়মিত উপস্থিত। তাঁদের মধ্যে ফারজানা সায়মা আপু বললেন স্যারের চিন্তার গভীরতার কথা, যার মাধ্যমে তিনি নিজে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত।
কর্মশালার মধ্যের এক শুক্রবারে ছুটি থাকায় স্যারকে নিয়ে ঘুরতে গিয়েছিলাম ঢাকেশ্বরী মন্দির, লালবাগ কিল্লা আর হোসেনী দালানে। বল্লাল সেনের নির্মিত যে মন্দিরের নামে ঢাকার নামকরণ হয়েছে সেখানে গিয়ে স্যার চারপাশ ঘুরে মন্দিরের ইতিহাস ঐতিহ্য আর প্রথা নিয়ে জানলেন, ক্যামেরায় হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন আচার করলেন ফ্রেমবন্দি। মুঘল সুবাদার আজম শাহ এর সময়কার অসম্পূর্ণ লালবাগ কিল্লা আর মীর মুরাদের নির্মিত শিয়া মুসলমানদের ইমামবাড়াও ঘুরে দেখলেন। কথা বললেন সেখানকার বর্তমান খতিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে। স্যার ইরান থেকে এসেছেন শুনে ইমামবাড়ার লোকজনও স্যারকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করলেন। স্যারের সাথে নিয়ে আমরা শিক্ষার্থীরা মিলে একদিন সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসও ঘুরে দেখালাম। চলার ফাঁকে ফাঁকে হলো সিনেমা নিয়ে আলোচনা আর মতবিনিময়। বুঝলাম একজন ভালো শিক্ষক কীভাবে চলার পথেও শিক্ষা দিতে পারেন। জাতীয় জাদুঘরে গিয়ে স্যার জানালেন বাংলাদেশে যেমন দেশের পাখি, প্রাণী, উদ্ভিদ, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদির সবকিছু একই জাদুঘরে বিন্যস্ত করা হয়েছে, ইরানে তেমন নয়; বরং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য রয়েছে আলাদা জাদুঘর। শিল্প-সংস্কৃতিসমৃদ্ধ সুপ্রাচীন জাতির জন্য সেটাই তো স্বাভাবিক।
স্যার বাংলাদেশে ছিলেন প্রায় ১২ দিনের মতো। যাবার বেলায় স্যার জানালেন এদেশের প্রতি তাঁর ভালোলাগার কথা, বললেন সম্ভব হলে তিনি আবার আসবেন, মতবিনিময় করবেন সিনেমার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। সিনেমা নিয়ে বাংলাদেশ আর ইরানের এই উদ্যোগ সামনেও বজায় থাকবে এই আশা নিয়ে তিনি এদেশের শিক্ষার্থীদের আমন্ত্রণ জানালেন নিজের দেশে।
এমন একজন শিক্ষকের সংস্পর্শে আসতে পারাটা আমাদের শিক্ষার্থীদের কাছে স্মরণীয় বিষয়গুলোর একটি হয়ে থাকবে। এমন উদ্যোগ নেয়ায় কৃতজ্ঞতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিভিশন, ফিল্ম ও ফটোগ্রাফি বিভাগকে, প্রিয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূইয়া, হায়দার রিজভী স্যারসহ অন্যদের। কৃতজ্ঞতা ইরান কালচারাল সেন্টারকে। কোন কোন পাখি উড়ে চলে গেলেও ফেলে যাওয়া পালকে তার স্মৃতি রেখে যায়। মাসউদ সোফলায়ী স্যারের সাথে কাটানো সময়, তাঁর শিক্ষা যেন আমাদের কাছে তেমনই। ভবিষ্যতে আরো এমন সুন্দর আয়োজন আমাদের চিন্তার পরিধিকে বৃদ্ধি করবে, দেশের চলচ্চিত্রে ভূমিকা রাখতে সাহায্য করবে এমনটাই প্রত্যাশা।
শিক্ষার্থী (সম্মান ৪র্থ বর্ষ)
টেলিভিশন, ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।