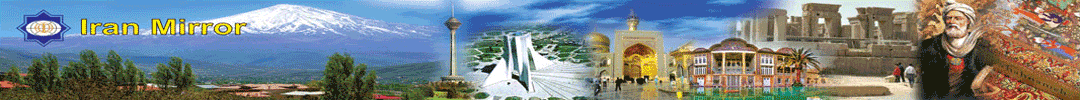সাক্ষাৎকার
পোস্ট হয়েছে: মার্চ ৮, ২০১৭
প্রশ্ন ১ : এ বছর আপনার ইরান সফর সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন?
উত্তর : ২০১৬ সালে আমি দুই দুই বার আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান সফরে যাই। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দাওয়াত পেয়ে তেহরান ও কোমে অনুষ্ঠিত দুইটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত মানবাধিকার সম্পর্কিত সেমিনারে বিশ্বব্যাপী সংখ্যালঘুদের অধিকারের ওপর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন করি। সেখানে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবার মানবাধিকার রক্ষায় মুসলিম দেশগুলোর ভূমিকা নিয়েও কথা বলি। আমার বক্তব্যের মৌলিক বিষয় ছিল কীভাবে আমরা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের দেশগুলোর মাঝে এ ব্যাপারে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে পারি। মধ্যপ্রাচ্যসহ বহু দেশেই সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। এই সেমিনারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে ইরানের বেশ কয়েকজন প্রসিদ্ধ আয়াতুল্লাহ অংশগ্রহণ করেন।
এই সফরে আমার অংশগ্রহণকৃত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয় ইরানের আধ্যাত্মিক নগরী কোমে। এটি যৌথভাবে আয়োজন করে জেনেভা ভিত্তিক ওঈজঈ এর হেডকোয়ার্টার এবং ইরান রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। এই সেমিনারটিতে কোমের সবগুলো বড় বিশ্ববিদ্যালয় ও হাওযার (নয়টি ধর্মীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের) বড় বড় আলেম, পঁচিশটি দেশের ত্রিশজন প্রতিনিধি এবং প্রায় এক হাজারেরও বেশি ইরানি ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। দুই দিনব্যাপী (৭ ও ৮ ডিসেম্বর) এই সেমিনারের কার্যক্রম চলে। পূর্বেরটির মত এই সেমিনারেও বাংলাদেশ থেকে আমি একাই অংশগ্রহণ করি। দ্বিতীয় এই সেমিনারে আমাকে কোন প্রবন্ধ উপস্থাপন না করে ইরানি ও বিদেশিদের উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহের অনানুষ্ঠানিক সমালোচক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়। উল্লেখ্য, এই সেমিনারের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে যুদ্ধ ও সকল প্রকার বিরোধ ও সংঘর্ষ বন্ধ করে কীভাবে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়।
প্রশ্ন ২ : ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান সফরের ইতিবাচক দিক সম্পর্কে বলুন?
উত্তর : বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে আমি উল্লিখিত দুটি আন্তর্জাতিক সেমিনার থেকে নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। গত ৩৫ বছরে শিক্ষা-দীক্ষা ও গবেষণায় ইরানি আলেম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের অভূতপূর্ব উন্নতি প্রত্যক্ষ করেছি। বিশেষ করে ইরানের মহিলা শিক্ষক ও গবেষকদের উন্নতি ও অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করে আমি উপলব্ধি করেছি যে, আমরা আরব-অনারবসহ সব মুসলিম জাতি আসলেই ইরানবিরোধী প্রচারণার শিকার। আমি মনে করি এই দুটি আন্তর্জাতিক সেমিনার বা সম্মেলন আমার মনোজগৎ ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাকে সমৃদ্ধ করেছে। আমার বিশ্বাস, এইবার আমি আরও অধিক নিরপেক্ষভাবে দক্ষিণ এশিয়া বা পুরো এশিয়াতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহে ইরানের শিক্ষা-দীক্ষা ও গবেষণার বিভিন্ন দিক তুলে ধরতে পারব।
উল্লেখ্য, ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক পরিম-লে আমার বেশ কিছু গবেষণামূলক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। যেযখানে ইরানের ইসলামি সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিভিন্ন দিক বিধৃত হয়েছে।
প্রশ্ন ৩ : ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের তথ্য প্রবাহ ও ন্যায় বিচার এবং শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা সম্পর্কে আপনার পর্যবেক্ষণ থেকে দয়া করে আমাদেরকে জানান।
উত্তর : প্রাচীন পারস্য ও বর্তমান ইরান সমৃদ্ধ সভ্যতার ধারক। একটি বিপ্লবী দেশ হিসেবে আমরা ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানকে খুবই পছন্দ করি। মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যকার বিবিধ চড়াই-উৎরাই, বিশেষত বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলি ও সংঘাতের ঊর্ধ্বে থেকে ইরান সব সময়ই তার মানবাধিকারের উত্তরাধিকার সংরক্ষণ করে আসছে, বরং তা গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে।
একটি জাতি হিসেবে ইরানিরা রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ক্ষেত্রে বহুত্ববাদের গঠন ও লালনে সব সময়ই বিরাট অবদান রেখেছে। এমনকি এর আগেÑগ্রীক ও রোমান সভ্যতার আগেওÑইরানি জাতি মানবাধিকারের, বিশেষ করে নারী জাতির ও সংখ্যালঘুদের অধিকারের হেফাযতে সব সময়ই যতœবান ছিল। পরবর্তীকালে মুসলিম শাসনাকমলে, যেমন : ফাতেমী, সেলজুক ও মোগল শাসনামলে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন ইসলামি ধ্যান-ধারণা বর্তমান ইরানের মূল ভূখ-সহ তৎকালীন পারস্যের সর্বত্র এবং আশেপাশের ভূখ- সমূহে বিস্তার লাভ করে।
এরপর ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের যুগে ইরানিরা উপনিবেশবাদী শক্তিগুলোকে তাদের দেশে প্রবেশ করতে দেয় নি, বরং তাদেরকে পারস্য উপসাগরের উপকূল থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে এবং স্বীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের হেফাযত করার ক্ষেত্রে পুরোপুরি সফল হয়। অবশ্য ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ও তাদের উদ্যোগে গড়ে ওঠা কোম্পানিগুলো অর্থনৈতিক, আর্থিক ও মনস্তাত্ত্বিক সম্পদসূত্র সমূহের ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক চেষ্টা চালায়। কিন্তু ইরানের দ্বীনী ও বুদ্ধিজীবী নেতৃবৃন্দের প্রতিরোধের ফলে ঔপনিবেশিক শক্তি তাতে সফল হয় নি। শুধু তা-ই নয়, ইরানের দ্বীনী ও বুদ্ধিজীবী নেতৃবৃন্দ দেশের সকল জনগণের সাংবিধানিক অধিকার ও মৌলিক মানবাধিকার সুসংহতকরণের লক্ষে সংগ্রামেও পুরোপুরি সফল হন। আমরা দেখতে পাই, এর ফলে ইরানে এমন একটি গতিশীল ও টেকসই আইনী, নৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে যা ইরানি জনগণের জীবন ও সংস্কৃতির প্রতিটি পর্যায়ে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে কাজ করছে। বিশেষ করে মুস্তায‘আফীন্ (দরিদ্র শ্রেণি) তত্ত্বের মর্মবাণী ও তার বিশ্বদৃষ্টি ইসলামি ইরানকে এমন একটি দেশের মর্যাদায় ভূষিত করেছে যা ধর্ম, সংস্কৃতি, জাতিগত গোষ্ঠী ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য আইনগত অধিকার ঘোষণা ও তার বাস্তব প্রয়োগের দৃষ্টিতে মুক্তি, মানবিক মর্যাদা ও উন্নয়নের দেশে পরিণত হয়েছে।
প্রশ্ন ৪ : ইসলামের মানবিক বিধান সমূহের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইরান যে নীতি অনুসরণ করেছে সে সম্পর্কে আপনার ধারণা আমাদেরকে জানালে খুশি হব।
উত্তর : এ প্রসঙ্গে আমি ইসলামি বিপ্লবী ইরানের ওপর চাপিয়ে দেয়া আট বছরব্যাপী যুদ্ধের সময়কার অবস্থার দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই। এ সময় আমরা দেখতে পাই যে, শত্রুর সামরিক হামলাজনিত ধ্বংসযজ্ঞের দ্বারা প্রতিটি ইরানি পরিবারই কম-বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ঐ সময় এবং এর পরেও ইরান বিশ্বের সর্ববৃহৎ সামরিক শক্তিবর্গের আরোপিত এক সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞার শিকার হয় এবং তারা গোটা ইরানি জাতিকে লাঞ্ছিত করার লক্ষ্যে ইসলামি ইরানের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাকেও ব্যবহার করে। তবে দীর্ঘ তিন দশকব্যাপী সফল কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে ইরান এ কঠিন অবস্থা মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামি ইরান এখন পুরোপুরিভাবে তার নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াতে এবং স্বয়ং স্বীয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও মানবিক প্রয়োজন সমূহ পূরণ করত সক্ষম হয়েছে।
আমরা লক্ষ্য করেছি, ‘আরব বসন্ত’ নামক রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাবে সমগ্র আরব জাহান অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত, চরম রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসাত্মক গৃহযুদ্ধের কবলে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সংগ্রামরত অনেক আরব দেশের জন্যই কোনো আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। এ পরিস্থিতিতে, সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তথাকথিত ‘ইসলামি রাষ্ট্র’ বা দা‘এশ্-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধকে এর সমাপ্তি পর্যন্ত এগিয়ে নেয়া এবং সিরিয়া, ইরাক, মিসর, লিবিয়া ও অন্যান্য গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলোর মানবিক প্রয়োজন সমূহ পূরণ সবচেয়ে বেশি জরুরি। এ ক্ষেত্রে, গোষ্ঠীগত, জাতীয়, ধর্মীয় ও মাযহাবি পরিচিতি নির্বিশেষে এসব দেশের জনগণের জন্য, বিশেষ করে ইরাকি ও সিরীয় জনগণের জন্য সম্ভবত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানই হচ্ছে একমাত্র আশার আলো।
প্রশ্ন ৫ : ইরানের শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চায় কী ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন?
উত্তর : গত ৩৫ বছরে আরও তিনবার ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বিভিন্ন অঞ্চল ও শহর ঘুরে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ১৯৮১ সালে আমি প্রথম বিপ্লবোত্তর ইরান দেখতে যাই। ঘটনাচক্রে আমি তখন ইরানি মজলিশের তৎকালীন স্পিকার হুজ্জাতুল ইসলাম আলি আকবর রাফসানজানীর মেহমান হই। ব্যক্তিগতভাবে খুব কাছ থেকে ইমাম খোমেইনীকে দেখার সৌভাগ্য হয় আমার। ইমাম খোমেইনীর ছেলে আহমাদ খোমেইনীর সাথে আমার সরাসরি কথা হয়। ইরানের বিভিন্ন শহর, যেমন : ইসফাহান, আবাদান, খোররাম শাহ্র, সিরাজ, আহ্ওয়াজসহ তেহরান ও কোম তো অবশ্যই, অনেক শহর পরিদর্শন ও প্রসিদ্ধ আয়াতুল্লাহদের বক্তব্যে আমি দারুণভাবে মুগ্ধ হই। কিন্তু সাদ্দামের সেনাবাহিনী দ্বারা বহুলাংশে যুদ্ধবিধ্বস্ত শহর ও জনপদ দেখে আমি কখনোই ভাবি নি যে, বিপ্লবোত্তর ইরান একা বড় বড় এত সব শক্তির সংগঠিত যুদ্ধের বিরুদ্ধে এককভাবে লড়ে বিজয়ী হতে পারবে। আজও যেন আমার সামনে ইরানের সে সকল যুদ্ধ বিধ্বস্ত জনপদের ছবি ভাসমান। গত কয়েক বছর পূর্বে আমি কাযভীন শহরে অবস্থিত ইমাম খোমেইনী আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে গিয়েছিলাম ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে। পৃথিবীর বহু দেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ও পড়ানোর সুযোগ আমার হয়েছে। কিন্তু কাযভীনের ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর অভিজ্ঞতা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। অনুবাদকদের সাহায্যে আমার পড়ানোর সে চেষ্টা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি। ফারসি ভাষা না জানার গ্লানি নিয়ে তুরষ্ক ও আফগানিস্তাান হয়ে পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন করি। উল্লেখ্য, আমাদের পূর্বপুরুষদের একটি আপ্তবাক্য তখন আমার বার বার মনে পড়ছিলÑ ‘আরবি বা ফারসি না জানলে নিজেকে পরিপূর্ণ শিক্ষিত বলে ধরে নেয়া বাতুলতা মাত্র।’ বলে রাখা ভালো যে, আমি রুশ ভাষার মত কঠিন মাধ্যম ব্যবহার করে মধ্যপ্রাচ্য, ইসলাম ও আইনশাস্ত্রীয় বহু জটিল বিষয়ে দীর্ঘদিন সফলভাবেই গবেষণা কর্ম চালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলাম। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, কয়েক দশক পূর্বেও আমি উজবেক, তাজিক, আফগানদের মাঝে থেকেও উপলব্ধি করি নি যে, আরবি ও ফারসি জানা বর্তমানেও এতটা জরুরি। ফারসি শুধু একটি অসাধারণ সাহিত্যসমৃদ্ধ ভাষা নয়। এটি আজ রুশ ও ফরাসি বা চাইনিজ ভাষার মত একটি বিপ্লবী ভাষা। ফেরদৌসী, শেখ সা’দী, ওমর খৈয়াম ও গালিবদের কথা না হয় বাদই দিলাম, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম একাই আরবি-ফারসি থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার শব্দ উপহার দিয়েছেন আমার প্রাণপ্রিয় বাংলা ভাষাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে একক কোন ব্যক্তির পক্ষে বিদেশি ভাষা থেকে নিজের ভাষায় এত বিপুল শব্দ ভা-ারের সংযোজনের ইতিহাস নেই। উল্লেখ্য, সৈন্য থাকাকালীন করাচির নৌবন্দরে সৈনিকের জীবন অতিবাহিত করার সময় আমাদের জাতীয় কবি এক বছরে ফারসি ভাষায় গভীর বুৎপত্তি অর্জন করেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নেহেরু কর্তৃক রচিত ঞযব এষরসঢ়ংবং ড়ভ ঃযব ডড়ৎষফ ঐরংঃড়ৎু ফারসি ভাষাতেই রচিত হয়। একসময়ের পারস্য আর আজকের বিপ্লবী ইসলামি প্রজাতন্ত্র সমগ্র মুসলিম বিশ্বের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের মাধ্যম হয়ে উঠছে। এটি প্রত্যক্ষ করে আমি যার পর নাই খুশি হয়েছি। তবে নিজেকে আজ মুসলিম ও ইসলামি সভ্যতাসহ সমগ্র মানবসভ্যতার কাছে অনেক বেশি দায়বদ্ধ মনে হয়।
প্রশ্ন ৬ : ইসলামের আন্তর্জাতিকতাবাদের কোন্ দিকটির পরিচর্যা আজকের ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানে বেশি?
উত্তর : আজ আমরা বিশ্বায়িত সমাজের নাগরিক। ইরানকে বা ইরানিদেরকে অনেক বাইরের পর্যবেক্ষকই ভুল প্রচারনার শিকার হয়ে মনে করেন আধুনিক বিশ্বের একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। অথচ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক শাখাসমূহের সাথে ভাষা ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যময় জ্ঞানের উৎসসমূহের ওপর ইরানিদের গবেষণা প্রমাণ করে যে, ইরানিরা জাতি হিসেবে এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান রাষ্ট্র হিসেবে আধুনিক বিশ্বের একটি আন্তর্জাতিকতাবাদের অনুঘটক (পধঃধষুংঃ)। বাংলাসহ ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা আজ এক নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে। কবিগুরুকে জীবদ্দশায় দাওয়াত করে এবং সমগ্র আধুনিক ইরানের সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয় করিয়ে দিয়ে ইরানিরা বুঝিয়েছিল যে, আমরা প্রাচ্যের একটি অতি বুনিয়াদি ও ঐতিহ্যম-িত সভ্যতার ধারক। কবিগুরুও নানা ভাবে ইঙ্গিত করেছেন পারস্য সভ্যতার অতীত যশগাঁথার বিভিন্ন দিকে। উল্লেখ্য, ইংরেজরা যখন লিখতে বা পড়তে পারত না বা ইংরেজদের ভাষাই যখন সৃষ্টি হয় নি, তখন পারস্যের অধিবাসীরা বর্ণমালার চারুলৌকিক গাঁথুনীকে সৌন্দর্যম-িত ও যুক্তিযুক্ত করার কাজে নিরলস প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। আধুনিক ইসলামি ইরানিদের জ্ঞানচর্চা, সাহিত্যসাধনা, সংগীতচর্চা ও চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সাফল্যগুলো আজ বিশ্বনন্দিত। আমার মনে হয় বাঙালি জাতি হিসেবে আমাদের উচিত হবে আরবি, ফারসিসহ প্রাচ্যের সম্মিলিত সমৃদ্ধ ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানভা-ার থেকে নুড়ি খুঁজে নিয়ে আমাদের জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করা। ভুলবশত মনে করা হয় যে, বিপ্লবোত্তর ইরান কেবল শিয়া দর্শনকে লালন করে এবং শিয়া-সুন্নি মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্বে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে। অথচ বিশ্ব ও আঞ্চলিক ঘটনাপ্রবাহে ইরানের গঠনমূলক ভূমিকা বড়ই স্পষ্ট এবং তা জ্ঞানী লোকদের কাছে সহজেই দৃশ্যমান।