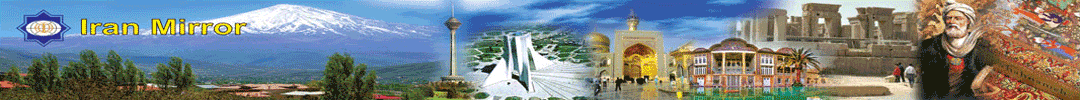সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ
পোস্ট হয়েছে: মার্চ ৩০, ২০১৪
এরভিন চ্যারগাফ
(এরভিন চ্যারগাফ একজন আধুনিক জার্মান দার্শনিক। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন। সাধারণত জার্মান ভাষাতেই তিনি লিখেন। কিন্তু ইংরেজি ভাষাতেও তাঁর চর্চা বেশ প্রশংসিত। চ্যারগাফ ইংরেজি ভাষায় ‘সিরিয়াস ম্যাটারস’ (Serious Matters) নামক একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করেন। এই বইয়েরই একটি রচনার সার সংক্ষেপ আমরা এখানে তুলে ধরলাম)।
কিছুদিন আগে ফরাসি সংস্কৃতি মন্ত্রীর একটি বক্তৃতা পড়েছিলাম। সেখানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে ‘সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ’ এর জন্য অভিযুক্ত করেছেন। আমি জানি না, এই ধরনের কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে কি নেই। তবে গ্রেশামস’ ল (Gresham’s Law)-এর কথা আমি জানি। গ্রেশামের আইন মতে কালো টাকা বাজারে এসে সাদা টাকাকে অচল করে দেবে। এটা একটি সত্য যে, মানুষ আর ঘোড়ার মধ্যে তফাৎ রয়েছে, আগেকার মানব প্রজ্ঞা বর্তমান আমি’র চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ ছিল। তা থেকে আমার উপলব্ধি হয়েছে, মানুষ ঘোড়াকে পানির কাছে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু জোর করে পানি খাওয়াতে পারে না। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, মানুষের বেলায় এই দু’টি কাজই সম্ভব। আমাদের রয়েছে প্রচার-প্রপাগান্ডার প্রভূত হাতিয়ার এবং উত্তেজনাকর বিবিধ শিল্পকলা। মিষ্টি-মধুর গানবাদ্য ছাড়াও এ ক্ষেত্রে যদি পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়, তাহলে মানুষকে মূত্রপান করতেও বাধ্য করা যেতে পারে। এটা কিভাবে সম্ভব? অর্থাৎ যদি দুই বা একজন চলচ্চিত্র তারকা মঞ্চে দাঁড়িয়ে এ কাজটির (মূত্রপান) ভান করে, তাহলেই লোকেরা তা করবে। তবে আমার মনে হয় না, এই ধরনের ব্যবসায়িক ফন্দি-ফিকিরে কেউ টাকা কামাতে পারবে। তাই যদি হতো তাহলে এতদিন আমরা একটি ‘আমেরিকান মূত্র কোম্পানির’ American Urine Company-A.U.C মুখ দেখতে পেতাম।
লর্ড রোজবেরী (১৮৯৯) একবার মন্তব্য করেছিলেন, ‘যৌক্তিক সাম্রাজ্যবাদ বৃহত্তর ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদে রূপ লাভ করে।’
‘যৌক্তিক’ বা ‘বিজ্ঞতাপূর্ণ’ এমন একটি বিষয়, যা নিকৃষ্টতম বর্বরতার বেলায়ও প্রযোজ্য হতে পারে।
উপনিবেশিত জনগণের প্রতি উপনিবেশবাদী প্রভুরা পশুর ন্যায় আচরণ করত। কারণ, ব্রিটিশ জাতীয়তাবাদ এবং ‘বিজ্ঞতা’র অভাবে এসব স্থানীয় লোক দুর্ব্যবহার পাওয়ারই যোগ্য ছিল। তাই প্রভুদের মতে উপনিবেশিত জনগণকে ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে যাওয়াতে অন্যায় কিছু হয় না।
সাম্রাজ্যবাদই শুধু নয়, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার আরো একটি শব্দ তাদের রয়েছে। তা হলো মোড়লিপনা বা hegemony; ইদানীংকালে চীন দেশে এর বেশ ব্যবহার দেখা যায়। যাদের সাথে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ভালো সম্পর্ক নেই তাদেরকে চীন এই বিশেষণে আখ্যায়িত করে থাকে।
সাম্রাজ্যবাদ বা আধিপত্যবাদের ওপর ব্যাপক রচনা সম্ভার রয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে লেনিন এবং অটো বাভের (Ott Baver) এর মতো কম্যুনিস্ট চিন্তানায়করা আধিপত্যবাদকে পুঁজিবাদেরই অস্ত্রসজ্জিত একটি শাখা হিসাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। সমাজতন্ত্রীদের ক্ষমতা লাভের পর আধিপত্যবাদের এই কঠোর সংস্থার রূপ পাল্টে যায়। আমি মনে করি, মানুষ যখন কোন কিছু করতে অক্ষম বোধ করে তখন মান-মর্যাদার দিকেই ফিরে তাকায়। মানুষের মধ্যে একদল আছে যারা সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপেই লিপ্ত থাকে। আর একটি দল সেই কার্যকলাপকে লেখনির মাধ্যমে তুলে ধরে। এভাবে ইতিহাসে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো পাওয়া যায়। কিছুকাল আগের ফকল্যান্ড দ্বীপমালার ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, প্রাক্তন রাজতন্ত্রের মিথ্যা স্বপ্নগরিমা ধীরে ধীরে বিস্মৃতির গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনা কার্ল মার্কস এর সেই উক্তিরও সত্যতা বিধান করে যখন কার্ল মার্কস বলেছিলেন : ‘হেগেল বলেছেন, ‘সকল ঐতিহাসিক ঘটনার দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্তি ঘটে’। কিন্তু তিনি এটা বলতে ভুলে গেছেন যে, এ সকল ঘটনা একবার বিয়োগান্ত রূপ লাভ করে এবং তারপর হাস্যকর রূপে পর্যবসিত হয়।’
অবস্থার যখন পরিবর্তন ঘটে এবং প্রচলিত কোন শব্দ যখন উপযুক্ততা হারিয়েছে বলে আমরা মনে করি তখন সেই শব্দের প্রারম্ভে সাধারণত আমরা একটি উপসর্গ জুড়ে দেই, যেমন ‘নতুন’ বা ‘পরবর্তী’ ইত্যাদি। আধিপত্যবাদের এ রকম এক নতুন রূপ হলো নয়া উপনিবেশবাদ (New Colonialism)। এর আভিধানিক অর্থ খুঁজলে পাওয়া যায়, অন্য দেশ ও জনগণের ওপর পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে বৃহৎ শক্তিগুলোর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতি।
এই সূত্রে আমেরিকার সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের উদ্দেশ্যে হলো অন্য দেশে পরোক্ষভাবে তার সংস্কৃতির চালান দেয়া। তবে এই ‘সংস্কৃতি’ শব্দটার অর্থ কী তা আমাদের জানা উচিত। Raymond Williams এর বিশ্ববিখ্যাত আভিধানিক গ্রন্থ KEY WORDS-এ বলা হয়েছে ইংরেজি ভাষায় ‘Culture’ অর্থাৎ সংস্কৃতি শব্দটার ব্যাখ্যা করা খুবই জটিল। এই সংস্কৃতির আওতায় অনেক বিষয়ই আসতে পারে, যেমন সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সংগীত, নাটক, সিনেমা ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের যুগে এই সংখ্যাকেও খুব সংক্ষিপ্ত মনে হয়। আমার মতে উচ্চতর শিক্ষা, অধ্যয়ন, গবেষণা প্রভৃতিও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তা ছাড়া জাতীয় ভাষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়াও সংস্কৃতির অঙ্গ। শিশুসন্তান এবং গাছপালার যে রকম যত্ন নেয়া হয় তেমনি ভাষারও যত্ন নেয়া উচিত। তবে সংস্কৃতির সংজ্ঞায়িতকরণে আমি অবশ্যই গণমাধ্যম ও অন্যান্য ভাবপ্রবণতা জাগানো উপাদানকে বাদ দেব। কারণ, এগুলো জনমতকে বিকৃত ও বিভ্রান্ত করায় ওস্তাদ। চিত্তবিনোদন শিল্পগুলোকেও আমি সাংস্কৃতিক অভিধায় আখ্যায়িত করতে চাই না।
রফতানি করতে হলে রফতানি করার মতো কিছু আপনার থাকতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের আদৌ কি তেমন কোন সংস্কৃতি রয়েছে যা সে অন্যদের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চাপাতে পারে? আমি বলব, নেই। বস্তুসামগ্রীর উৎকৃষ্ট মানের কারণে রফতানি করা হয়, তা ভাবা হাস্যকর হবে। সাম্রাজ্যবাদীরা প্রায়ই কোন গুণাগুণ বিচার ছাড়াই তাদের দ্রব্যসামগ্রী রফতানি করে থাকে। তবে তাদের মারণাস্ত্রগুলো বেশ উন্নতমানের হয়।
ফরাসি সংস্কৃতি মন্ত্রী যদি প্যারিস নগরীর দেয়ালগুলোর দিকে লক্ষ্য করেন, তাহলে কী দেখতে পাবেন? যদি কান পেতে দেন, তাহলে কী শুনতে পাবেন? তিনি দেখতে পাবেন আমেরিকান ধাঁচের ড্রাগ স্টোর, তিনি দেখতে পাবেন প্যারিসের যুবকেরা আমেরিকান ব্লু জীন্স পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমেরিকান সংগীতের তালে তালে নাচছে এবং আমেরিকান কোকাকোলায় চুমুক দিচ্ছে। তিনি আরো দেখতে পান প্যারিস নগরীর সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে কুৎসিত সব গগনচুম্বী অট্টালিকার কারণে। তিনি দেখতে পান সিনেমা হলগুলোয় হলিউডি মারদাঙ্গা সিনেমার দৌরাত্ম্য, টিভিতে একই রকম এক ঘেঁয়েমিপূর্ণ সিরিয়ালের আধিপত্য। তিনি যখন রেস্তোরাঁয় ঢোকেন তখন টেবিলে টেবিলে খাবারের আমেরিকান নামের বহর দেখে অবাক হয়ে যান। এসব কিছুই আধিপত্যবাদের নমুনা। তবে এসবকে কালচার অর্থাৎ সংস্কৃতি বলা যাবে কিনা- এ ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।
শিশুবেলায় ভিয়েনায় থাকতে আমি দেখেছি ফ্রান্স বা ব্রিটেন থেকে যা কিছুই আসত তা প্রশংসনীয় ছিল। যদিও হাঙ্গেরী, রোমানিয়া, পোল্যান্ডে ভিয়েনার জিনিসপত্র প্রশংসনীয় ছিল। ঠিক তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চল সকলের কাছে আকর্ষণীয় ছিল। কিন্তু আমি মনে করি গত ৩০ বছর এই সুনাম সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে।
আধিপত্যবাদ বা অ-আধিপত্যবাদ যাই হোক, আমি মনে করি, সংস্কৃতি হিসাবে তুলে ধরার মতো যুক্তরাষ্ট্রের কিছুই নেই। যতদূর জানি, যুক্তরাষ্ট্রে লেখকদের লেখার মান অত্যন্ত নীচু প্রকৃতির, সংগীত এবং সুকুমার কলার অবস্থাও তথৈবচ। শুধু সিনেমা এবং সম্ভবত নৃত্যশিল্পকে কিছুটা উন্নতমানের বলা যায়। অথচ ৭০ বছর পিছনে ১৯২২ সালে যদি আমরা ফিরে যাই, তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠবে। তখন আমেরিকান সমাজে বড় বড় ঔষধ, কবি, সাহিত্যিক, চিত্রকর, ভাস্কর এবং সংগীত বিশারদের প্রাচুর্য…। অথচ সেই সময়েও কালচার হিসাবে উপস্থাপন করার মতো যুক্তরাষ্ট্রের তেমন চমকদার কিছু ছিল না, তবে একটা জিনিস ছাড়া- তা ছিল জ্যাজ সংগীত। তাও আবার ছিল নিগ্রোদের অবদান।
এর পরে সাংস্কৃতিক আধিপত্যের আওতায় বাকি থাকে শুধু গবেষণা এবং বিজ্ঞান। বর্তমানে এই দু’টি বিষয় সম্পূর্ণভাবে কতিপয় বিশেষজ্ঞের হাতে কুক্ষিগত হয়ে আছে। কল-কারখানায় উৎপাদিত বস্তুসামগ্রীর মধ্যেই বিজ্ঞান ও গবেষণাকে তারা আবদ্ধ করে রেখেছে। অর্থাৎ সাধারণ জনগণের কাছ থেকে তা বিচ্ছিন্ন। এই গবেষণা ও বিজ্ঞানের আমেরিকান ব্রান্ডকে অপপ্রচারকারীরা সাংস্কৃতিক আধিপত্যের অন্যতম উপাদান হিসাবে জাহির করে।
নিজেদের অনিচ্ছা বা অক্ষমতার কারণে আমেরিকানরা অন্য কোন ভাষা শিখতে পারে না। এ জন্য নিজেদের ভাষাকে গোটা পৃথিবীর ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দেয়ার বদ মতলব তাদের স্পষ্ট। এ ক্ষেত্রেও গ্রেশামের নীতি কাজ করে।
স্লোগান হলো আধিপত্যবাদের একটি বড় হাতিয়ার। তবে এই স্লোগানকে সংস্কৃতি বলা যাবে কিনা আমার সন্দেহ। ইদানিং আমেরিকান জীবনধারা একটি প্রভাবশালী স্লোগান। আমি মনে করি এই জীবনধারা ‘রিয়েল এস্টেট’ ব্যবসার রঙিন পুস্তিকা এবং টিভি পর্দাতেই নিহিত। নিউইয়র্কে আমি অনেকদিন কাটিয়েছি। ওখানকার অধঃপতিত অবস্থা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হয়েছে। এখনো আমি বুঝতে পারি না, প্রাচ্য দেশগুলোর প্রচার সংস্থা ও গণমাধ্যমগুলো কেন তাদের লোকজনদের নিউইয়র্কের অলিগলি, ব্রংস-এর দক্ষিণভাগ এবং ব্রুকলিনের মহল্লাগুলোকে পরিদর্শনের জন্য পাঠায় না? তাহলে প্রকৃত অবস্থাটা তাদের চোখে পড়ত। কিন্তু আমি জানি, এই প্রশ্নটা একেবারে সাদামাটা গুরুত্বহীন একটা প্রশ্ন। কেননা, অধিকাংশ এশিয়াবাসীই যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় লাভের জন্য লালায়িত। আমার কাছে যা বাজে কুঁড়ে ঘর, তাদের কাছে তা স্বাধীনতার সোনার রথ।
‘মুক্তি’ শব্দটা ব্যবহার করে খুব শক্তিশালী স্লোগান বানানো যায়। এই শব্দটার উচ্চমূল্য রয়েছে। মুক্তি শব্দের বিচার করতে গেলে স্বাধীনতা শব্দটাও এসে যায়। এ দু’টি শব্দ যেমন সমার্থক, তেমনি আবার ভিন্নার্থকও হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার যখন তাঁর নাগরিক স্বাধীনতার বেলুন উড়িয়েছিলেন তখন সেগুলো নিউইয়র্কেও গগনচুম্বী অট্টালিকাগুলোকেও ছাড়িয়ে ওপরে উঠে গিয়েছিল। নাগরিকদের মুক্তির নামে কি তিনি সেই কাজ করতে পারতেন? আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমার মতে মুক্তি হলো স্বাধীনতার চূড়ান্ত রূপ। মুক্তির পরিসংখ্যানগত দিক থাকতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতা এমন জিনিস যা হতাশ হয়ে মানুষ খুঁজে বেড়ায়।
কিংবদন্তী সৃষ্টির মহান প্রক্রিয়াতেই এসব স্লোগানের শক্তি নিহিত। স্লোগান অবাস্তব স্বপ্ন কল্পনারই প্রতিফলন। নিজের অর্ধমুক্ত ভাগ্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্র এসব স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে সচেষ্ট। এ ধরনের আধিপত্যবাদের সবচেয়ে বড় বিপদ হলো এর বহির্মুখী রূপকে বিশ্বাস করা। আমাদের সময়ের কোটি কোটি নির্যাতিত অবহেলিত জনগণের কানে রাতদিন ঢোল পিটিয়ে এই অবাস্তবতা ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। তারা যদি শেষ পর্যন্ত এসবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাহলে এই বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই সময় থাকতেই আমাদের সাবধান হয়ে যাওয়া উচিত।