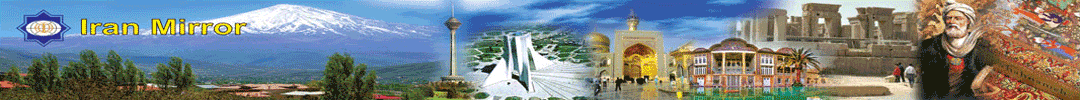সমকালীন ফারসি কাব্যসাহিত্যের বিকাশধারা
পোস্ট হয়েছে: মার্চ ৮, ২০২০
ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)
বিংশ শতাব্দীতে ইরানের সমকালীন ফারসি সাহিত্যজগতে যে ক’জন খ্যাতনামা কবির আবির্ভাব ঘটেছে ‘উমিদ’ নামে খ্যাত মাহ্দি আখাভানে সালেস (১৯২৮-১৯৯০ খ্রি.) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কেননা, তিনি স্বকীয়তা বজায় রেখে স্বাধীনভাবে কাব্যচর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন এবং দু’টি ধারায় কাব্যচর্চা করে সমাদৃত হয়েছেন। একদিকে তাঁর কাব্যচর্চার ব্যাপকতা ও দক্ষতা, অপরদিকে তাঁর নানাবিধ জ্ঞান ও মেধার স্ফূরণ ও বিস্তৃতির কারণে এ প্রথিতযশা কবি ফারসি সাহিত্যভুবনে জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছেন।
মাহদি আখাভানে সালেস খোরাসানের রাজধানী মাশহাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ভণিতা ছিল উমিদ। তাঁর পিতার নাম ছিল আলী, যাঁর আদি নিবাস ছিল ইয়ায্দ। আখাভানে সালেস প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা নিজ গ্রামের বিদ্যালয়েই অর্জন করেন। পরবর্তীকালে শিল্পকলা ইনস্টিটিউট থেকে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। যদিও শৈশব থেকেই তিনি কবিতাচর্চা শুরু করেন, কিন্তু ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দেই মূলত তাঁর কবিতাচর্চার সূচনা হয়। তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষক পারভীন কাভিয়ান তাঁর মাঝে কাব্যসুলভ প্রতিভা প্রত্যক্ষ করে তাঁকে কবিতাচর্চায় বিশেষ উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। তিনি প্রথম যে কবিতা রচনা করেছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণভাবে একত্ববাদনির্ভর কবিতা। এর কিছু কাল পরে সালেস মাশহাদ সাহিত্য পরিষদের সদস্যপদ লাভ করেন। এছাড়া সে সময় খোরাসানের খ্যাতনামা কবি নুসরাত মাহদি আখাভানে সালেসকে ‘উমিদ’ ছদ্মনামে আখ্যায়িত করেন। সে থেকেই তিনি কবি উমিদ হিসাবে পরিচিত হন।
সংগীতের প্রতি ছিল সালেসের বিশেষ ঝোঁক ও অনুরাগ। তিনি ইরানী রীতিতে বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারঙ্গম ছিলেন, এমনকি তিনি সেতারও বাজাতে পারতেন। কিন্তু পিতার অনাগ্রহ ও আপত্তির কারণে তাঁর সংগীতচর্চা আর হয়ে ওঠেনি। আনুমানিক দীর্ঘ ১৬ বছর পর্যন্ত মাশহাদে অবস্থানের পর সালেস ১৯৪৪ সালে রাজধানী তেহরানে চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তেহরানে তিনি প্রথমে শিক্ষকতার পেশাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। এ সময় স্বাধীনতা শীর্ষক একটি কবিতা লেখার অপরাধে তাঁকে জেল-জুলুমও সহ্য করতে হয়েছিল।
জীবনসায়াহ্নে এসে তিনি তেহরানের শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়, শহীদ বেহশতি বিশ্ববিদ্যালয় ও তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল কিছুটা ভিন্নধর্মী ও স্বতন্ত্র। কারণ, তিনি শুধু শিক্ষাবিদই ছিলেন না, তিনি একদিকে ছিলেন শিক্ষাবিদ, অন্যদিকে ছিলেন একজন কবি ও যুগ-সচেতন শিল্পী।
পেশা হিসাবে কবিতাচর্চা ও সাহিত্যের সঙ্গে সাংবাদিকতার একটি সম্পর্ক রয়েছে। তাই কবি সালেসও সাংবাদিকতা পেশায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকার সাথে যুক্ত থেকে তাঁর কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ একাধারে প্রকাশ করেছেন। এর পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার সিনেমায় ডাবিং-এর কাজও তিনি করতেন।
একজন কবি হিসাবে সালেস ছিলেন প্রতিভাধর। ফারসি সাহিত্য ও কাব্যচর্চায় তাঁর পরিধি ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। তিনি কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে ক্লাসিক তথা গ্রিক আদর্শে পরিপুষ্ট সাহিত্য-ধারা ও আধুনিক ধারা- এ উভয় রীতিই অনুশীলন ও অনুকরণ করেছেন।
তিনি স্তুতিমূলক কাব্য রচনার ক্ষেত্রে খোরাসানের প্রাচীন বড় মাপের কবিদেরকে অনুসরণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কবি মনুচেহ্রির* ছন্দরীতি বিশেষভাবে অনুসরণ করেছেন। তিনি গযল রচনায়ও সমানভাবে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি বিশিষ্ট গযল রচয়িতাদের প্রত্যক্ষ অনুসরণ করেছেন, যে কারণে তাঁর গযলে থাকত বাক্যের হৃদয়গ্রাহী আকর্ষণ ও প্রেমের অনল।
আখাভানে সালেস কাব্য রচনার ক্ষেত্রে ছন্দরীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, অর্থাৎ কবিতার মাত্রা ও ছন্দমিল এমন জিনিস নয় যে, তা কবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন, বরং তা কবিতার আত্মা ও অবয়বের সাথেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ, তাঁর মতে ছন্দমিল, মাত্রা ও শব্দের পারস্পরিক গাঁথুনি যদি কবিতায় অনুপস্থিত হয় তবে তা কবিতা হয়ে ওঠে না।
মাহদি আখাভানে সালেস খুব একটা বিলম্ব না করেই নিমা ইউশিজের কাব্যরীতি অনুসরণ করেন এবং তাঁর কাব্যধারা অনুসরণে ১৯৫৬ সালে যেমেস্তা’ন (শীতকাল) শীর্ষক কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করেন। তিনি এ গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে সমাজকে এক নতুন ধরনের কাব্যভাণ্ডার উপহার দিলেন যা উদ্দীপনাপূর্ণ ও সামাজিক আবহে সৃষ্ট কবিতায় সমৃদ্ধ। নিমার জীবনের শেষের দিকে সালেস তাঁর উচ্চাঙ্গের কাব্য সংকলন গ্রন্থ, যা আখেরে শাহনামে (শেষ রাজকীয় পত্রাবলি) নামে প্রকাশ করেন।
আখাভান এ যুগে কাব্য রচনা ছাড়াও সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একজন দক্ষ ও তীক্ষè সমালোচকের ভূমিকাও পালন করেন। তিনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি অত্যন্ত নিপুণভাবে নিমা ইউশিজের কাব্যগুলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, বিশেষ করে কবিতার ছন্দ, কাঠামো, আঙ্গিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর কর্মগুলোকে ফুটিয়ে তোলেন।
এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাঁর কাব্য গ্রন্থ যেমেস্তা’ন (শীতকাল) যা সমসাময়িক যুগের মানুষের হাল-অবস্থার প্রেক্ষিতে রচিত এবং যা কাব্যকলার বিচারে অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তা নিমার কাব্যাদর্শেই রচিত হয়েছে। তাই অকপটে বলা যায় যে, নিমার সাথে উমিদের কাব্যিক সাযুজ্য ছিল ব্যাপক।
আখাভানের দৃষ্টিতে কবিতা হচ্ছে তা-ই যা সমসাময়িক যুগের সমাজবিরোধী ও নির্যাতনকারীদের চোখের কণ্টক হিসাবে বিবেচিত হয়। আর যিনি এর প্রকাশ ঘটান তিনিই হলেন কবি অর্থাৎ কবির কবিতায় যুগ-সচেতনতা ও সমাজের সমকালীন পরিস্থিতি ও পরিবেশ এবং যালেম ও মযলুমের মধ্যকার সংঘাত বিধৃত হওয়া অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক ব্যাপার। কেননা, যুগ-সচেতন কবিদের কাব্যে মযলুমের ফরিয়াদ অনুরণিত হয়ে ওঠে। সত্যিকার অর্থে কাব্য হচ্ছে সমকালীন ও অনাগত কালের মানুষের আত্মিক, মানসিক ও অধ্যাত্ম চেতনার আশ্রয়স্থল। তাঁর মতে একজন কবিকে তাঁর সময়ের সমাজ ও সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।
কবি সালেসের বিপুল পরিমাণ প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সাহিত্যকর্ম রয়েছে। তাঁর সাহিত্যকর্মে স্বাধীনতাবোধ ও স্বকীয়তা চূড়ান্তভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি নিমা ইউশিজ প্রবর্তিত আঙ্গিক দ্বারা তাঁর কাব্য-সাহিত্যকে নতুন আঙ্গিকে সাজিয়েছেন। নি¤েœ আমরা তাঁর সাহিত্যকর্মের একটি তালিকা তুলে ধরার প্রয়াস পাব।
কাব্যগ্রন্থ অর্গানুন (অরগানন), আখেরে শা’হনা’মে (সর্বশেষ শাহনামা), যেমেস্তা’ন (শীতকাল), আয ইন আভেস্তা (এ আভেস্তা থেকে), পা’ইয দর যেন্দা’ন (জেলখানায় হেমন্ত), শেকার (শিকার), বেহতরিন উমিদ (উত্তম প্রত্যাশা), বারগুযিদে আয শেরহায়ে উমিদ (উমিদের নির্বাচিত কবিতাসমূহ), মানজুমেয়ে সাওয়াহেলি (উপকূলীয় কবিতা), দুযাখ আম্মা সারদ (জাহান্নাম কিন্তু শীতল), তুরা আয় কোহনে বুম ও বার দোস্ত দা’রাম (হে আদি ভূমি! তোমাকে আমি ভালোবাসি), বাহা’রে দিগার (আরেক বসন্ত), প্রবন্ধ সংকলন আদাবুর রাফি (উন্নত সাহিত্য), বেদায়াতহা’ ও বেদায়ে নিমা ইউশিজ (নিমা ইউশিজের অভিনবত্ব ও নতুন আবিষ্কার)- এ গ্রন্থটি ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। এতে নিমা ইউশিজের কাব্যরীতি, ছন্দরীতি ও আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের ওপর গবেষণা, বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এসব গ্রন্থ ছাড়াও সালেসের আরো কিছু গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি রয়েছে যার কিছু প্রকাশিত হয়েছে আর কিছু প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। নমুনা হিসাবে এবার আমরা মাহ্দি আখাভানে সালেসের একটি কবিতার অংশবিশেষ তুলে ধরছি :
‘আমার ঘরে আগুন লেগেছে, জীবন বিনাশী সে আগুন,
সর্বদিককে দগ্ধ করছে এ আগুন,
পর্দা, বিছানা আর তার সুতাগুলো তীব্র তাপে ধূমায়িত;
যেদিকেই আমি যাই না কেনো কেবল চিৎকার, আর্তনাদ,
আগুনের লেলিহান শিখা ধোঁয়ায় আচ্ছাদিত;
আমার ঘরে আগুন লেগেছে, নির্দয় সে আগুন
এ আগুন এমনিভাবে দগ্ধ করছে,
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে গড়া কপাট আর দেয়ালে আঁকা
আমার ছবিগুলো যেন
রাতের কূলহীন বঞ্চনার শিকার।’
সোহরাব সেপেহরি (১৯২৯-১৯৮১ খ্রি.) নিমা ইউশিজের অন্যতম শীষ্য ও অনুসারী। ইরানের কাশান নগরীতে তাঁর জন্ম। শিক্ষার্জনের জন্য তিনি কাশান ছেড়ে চলে আসেন তেহরানে। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ থেকে চিত্রকলার ওপর স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। শিল্পকলার ওপর তাঁর মূল কাজ ছিল চিত্রাঙ্কন। তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর মোট আটটি কাব্যগ্রন্থ একত্রে প্রকাশিত হয়েছে যার শিরোনাম দেয়া হয়েছে হাশত কেতা’ব (আটটি গ্রন্থ)। সোহরাব ভারত ও চীনসহ অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তিনি বিভিন্ন দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা ও বিস্তৃত তথ্য ভাণ্ডারকে কাজে লাগিয়ে সূক্ষ¥ভাবে তাঁর কাব্যের সৌকর্য বৃদ্ধি করেন। সোহরাবের কাব্যে প্রথম যে জিনিসটি চোখে পড়ে তা হলো অধ্যাত্মবাদ। এটি মূলত চীন, ভারত ও ইরানে ইসলামের আগমনোত্তর ও আগমনের পূর্বের অধ্যাত্মবাদের মিশ্রণে গঠিত। সোহরাব অস্তিত্বের সকল অণু-পরমাণুকে জীবন্ত ও অনুভূতিসম্পন্ন মনে করেন। এটি যেমন একটি তাপসসুলভ দর্শন তেমনি শিশুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিও বলা চলে। আরেফসুলভ দর্শন এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, অস্তিত্বের সকল অণু-পরমাণু আল্লাহর গুণগান করে থাকে। আর শিশুসুলভ দর্শন হলো এ জন্য যে, শিশুর সাত বছর বয়স পর্যন্ত তার মাঝে সর্বপ্রাণবাদের (অহরসরংস) বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকে। শিশু তার আশেপাশের সমস্ত বস্তুনিচয়কে জীবন্ত বলে ধারণা করে থাকে। সোহরাব সেপেহরি ভারতীয় সমকালীন দার্শনিক কৃষ্ম মূর্তির নিম্নোক্ত মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর মতে আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ শিখড়ে পৌঁছার জন্য অবশ্যই প্রকৃতির সাথে একীভূত হতে হবে। আর প্রকৃতির মাঝে নিজেকে প্রবিষ্ট করাতে হবে এবং স্বভাবের ধুলোবালি যা আমাদের চোখগুলোকে ঢেকে দিয়েছে এবং আমাদেরকে সত্তার সূক্ষ্ম, খাঁটি ও সুন্দর মহত্ত্বকে উপলব্ধি করা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে তা আমাদের চোখের সামনে থেকে দূরীভূত করে নতুন দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখা উচিত। চোখগুলো এমনভাবে পরিষ্কার করা উচিত যাতে অন্য প্রকারের জিনিস অবলোকন করা যায়।
আরেকটি বিষয় হচ্ছে, সোহরাব ছিলেন একজন চিত্রকর। যে কারণে তাঁর কবিতা চিত্রকর্মের সাথে মিশে গিয়ে একটি জটিল রূপ ধারণ করত এবং তাঁর বেশিরভাগ কবিতাই মিনিয়াচারের (গহরধঃঁৎব) বিষয় ধারণ করে থাকে। মিনিয়াচারের সাথে বাস্তবধর্মী চিত্রকর্মের পার্থক্য হলো এই যে, মিনিয়াচারের অবস্থান হলো আধ্যাত্মিক ও স্বর্গীয় বা উচ্চমার্গীয় তথা মেঘের ওপরের নির্মল বাতাস সম্পর্কিত একটা অবস্থান। যার ঔজ্জ্বল্যের জন্যই এর আলো উপলব্ধ হয় না। মিনিয়াচারে কোনো সময় বা স্থানের চিত্র ফুটে ওঠে না। নূরের বা জ্যোতির উৎসের বিভিন্নতা বা নানামুখিতা নেই এবং প্রেক্ষাপটও অভিন্ন। সোহরাব সেপেহরির কাব্যে ছন্দবিহীন শান্তিপূর্ণ এক প্রকারের ঢেউ খেলে যায়। ভারতীয় মরমিবাদ এক ধরনের মৌলিক অধ্যাত্মবাদ এবং এই মরণীবাদের শান্তিপূর্ণ অবস্থানটি সোহরাবের কাব্যের পরতে পরতে বিদ্যমান। অন্যদিকে সোহরাব বাণীপূর্ণ ছোট ছোট শব্দ এবং তাপসসুলভ বাক্যে রচিত এক ধরনের কবিতা যাকে ‘হাইকো’ বলা হয় তা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।
‘হাইকো’ অতি সংক্ষিপ্ত ও অনুভূতিপ্রবণ এক ধরনের চৈনিক কবিতাকে বলা হয়। সোহরাবের কবিতাকে ইরানের সাথে সম্পৃক্ত গোছের ‘হাইকো’ বলা যেতে পারে। সোহরাব বাস্তব জীবনস্পর্শী ঘটনাবলিতে গুরুত্ব প্রদান করেন। পৃথিবী যেরূপে রয়েছে সেভাবেই গ্রহণ করেন এবং একে ভালোবাসা দিয়ে ভরে দেন তিনি। তাঁর চিন্তা-চেতনায় কোনরূপ শত্রুতা বা মন্দের স্থান নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি ভারতীয় রচনাশৈলী দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন। সোহরাবের কাব্যে চোখ ভোলানোর মাধ্যমে নিজেকে দেখার সুযোগ পাওয়া যায়। তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : আ’রা’মগা’হে এশক্ (প্রেমের সমাধি), যেন্দেগিয়ে খা’বহা’ (স্বপ্নের জীবন), আ’ভা’রে আ’ফতা’ব (সূর্যের ধ্বংসাবশেষ), শারকে আনদুহ (বিষাদের প্রাচ্য), মার্গে রাঙ (রঙের মৃত্যু), হাজমে সাবয (সবুজের সমারোহ), সেদা’য়ে পা’য়ে আ’ব (জলতরঙ্গ), হাশত কেতা’ব (আটটি গ্রন্থ) প্রভৃতি। সোহরাবের কবিতার নমুনা :
‘আমরা পানি ঘোলা করবো না,
হয়ত নিচের দিকে কোনো কবুতর পানি খাচ্ছে
অথবা অনতি দূরের ঝোপ-ঝাড়ে পাখি তার পাখা ধৌত করছে।
অথবা হয়তো দূরের ঐ জনপদের কোনো ষোড়শী কলসি ভরছে।
আমরা পনি ঘোলা করবো না,
সম্ভবত এই প্রবহমান পানি কোনো দেবদারুকে স্পর্শ করে
কোনো হৃদয়ের মলিনতাকে ধুয়ে দিবে,
কোনো দরবেশের হাতের শুকনো রুটি ভেজাবে এ পানিতে
কোনো এক রূপসী এসেছে এ নদীর তীরে
তাই পানি ঘোলা করবো না আমরা।’
ফোরুগে ফাররোখযাদ (১৯৩৪-১৯৬৬ খ্রি.) ইরানের সমকালীন যুগের একজন স্বনামধন্য মহিলা কবি। তাঁকে অধুনাকালের সবচেয়ে আধুনিক কবি বলা হয়। ইরানের রাজধানী তেহরানের কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন সেনাবাহিনীর লোক। যে কারণে তাঁর মেজাজ ছিল সৈনিকদের ন্যায় রুক্ষ ও কর্কশ। ফাররোখযাদ এমনি পরিবেশেই তাঁর শৈশব অতিবাহিত করেন। তাঁর বোন ও বন্ধু-বান্ধবদের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে জানা যায় যে, শৈশব থেকেই অন্যান্য মেয়ের সাথে তাঁর অধিক পার্থক্য ছিল। হঠাৎ করেই তিনি খেলাধুলা ও কর্মচাঞ্চল্য পরিহার করে অন্তর্মুখিতার দিকে ধাবিত হন। অর্থাৎ ১৬ বছর বয়সে পারভিয শাহপুর নামক সেকালের একজন বিখ্যাত কার্টুনিস্ট ও ছড়াকারের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু ফাররোখযাদ ছিলেন সাধারণ জীবন যাপনের চরম বিরোধী। তিনি নিজের জগতকে পরিতৃপ্ত করতে চাইতেন। পারভিয তাঁকে উপলব্ধি করতে পারতেন না। এ সময়ই আসির (বন্দি) শীর্ষক তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এরপর দিওয়ার (দেয়াল) ও এসইয়ান (অবাধ্যতা বা বিদ্রোহ) নামের কাব্যগ্রন্থ দ্বয় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। আসির বা বন্দি শীর্ষক কাব্যগ্রন্থে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত প্রেম-ভালোবাসা, অনুভূতি ও বন্দিত্বের বিষয়ে আলোকপাত করেন। এর পাশাপাশি এ কাব্যগ্রন্থে দ্রুত হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের কৈশোর ও ভাসাভাসা জীবনের বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে। দিওয়ার (দেয়াল) নামক কাব্যগ্রন্থে তাঁর এ বন্দিত্ব ও দুঃশ্চিন্তার কারণগুলো বিধৃত হয়েছে। আর তাঁর এসইয়ান শিরোনামের কাব্যগ্রন্থে সামাজিক ও রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে সোচ্চার বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়। সাবলীলতা ও পরিশীলিত ভাবধারা, আন্তরিকতা, সত্যতা তাঁর বর্ণনায় সূক্ষ্মভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে- যা সে সময়ে ছিল বিরল এবং এসব সমাজে ব্যাপকভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। এই ধরনের কবিতা এবং তাঁর স্বাধীন বা বন্ধনহারা চেতনার কারণে পারভিযের সাথে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে। ফাররোখযাদের দ্রুত শামাল দেয়ার বিস্ময়কর শক্তি ছিল যা তাঁকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। জালাল আলে আহমাদের মতে ‘ফাররোখযাদ প্রথমে নারীর স্বাধীনতাকে দৈহিক স্বাধীনতার সাথে গুলিয়ে ফেলে ভুল করেছিলেন। কিন্তু যা কিছু তাঁর ব্যাপারে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে তার কারণে এমনটি হয়নি যে, তিনি মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন। তিনি একাকী নারীর নিজস্ব অনুভূতি, দুর্বলতা, হালকা ও ভাসাভাসা ভাবনাগুলো তাঁর লেখার মাধ্যমে তুলে ধরেন।’
ফাররোখযাদ কয়েকটি স্বল্পদৈর্ঘ্য ও পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে অভিনয়সহ চলচ্চিত্র নির্মাণ কাজের সাথে ওৎপ্রতোভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ব্রিটেন থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণ কৌশল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এর ফলে চলচ্চিত্র অঙ্গনে তাঁর ব্যাপক ভূমিকা ফলপ্রসূ হয়েছিল।
ফাররোখযাদের কাব্যে স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছাপ পরিলক্ষিত হয় এবং তাঁর হৃদয়ে লুক্কায়িত বিষয়গুলোকে জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা করেছেন তিনি। তাঁর কাব্যে জীবন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় শব্দ ও বাক্য বিন্যাসের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অনাকাক্সিক্ষত ও ক্রোধ বা জীবনের ব্যথা-বেদনার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেন।
কবিতায় ছন্দের বিষয়টি একটি উল্লেখযোগ্য দিক। তাঁর কবিতা সমকালীন কবিদের কবিতার চেয়ে অধিক মাত্রায় স্বাধীন যা খানিকটা অতিরঞ্জন বলে মনে হয়। পাঠক এতে অনেকটা কবিতার ঝংকার ও স্পন্দন অনুভব করেন না।
অন্যদিকে নতুন নতুন বিষয়বস্তুর আবিষ্কার, নতুন আবিষ্কৃত কল্পচিত্র, বস্তুনিচয় ও চতুর্দিকের পরিবেশ-পরিস্থিতি এমন ভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ করা তাঁর অনুপম কাব্যবৈশিষ্ট্য বলে ধরে নেয় হয়। ওপরে উল্লিখিত কাব্যগ্রন্থগুলো ছাড়াও তাঁর আরো দু’টি কাব্যগ্রন্থ তাভাল্লোদে দিগার (অপর জন্ম) ও ইমান বিয়াভারিম বে আ’গা’যে ফাসলে সারমা (শীতকালের সূচনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি) বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, ফোরুগে ফাররোখযাদ এক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর কবিতার নমুনা নিচে তুলে ধরা হলো :
‘প্রতি মুহূর্ত আয়নার কাছে বিষণœ হয়ে জানতে চাই
বলত তোমার চোখে আমি কে, আমার স্বরূপই বা কী?
কিন্তু আয়নায় দেখছি যে, হায়!
আমি যে ছায়াস্বরূপ ছিলাম
তার একটিও আমি নই।’
সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হোসাইন শাহরিয়ার তাবরিযি (১৯০৬-১৯৮৮ খ্রি.) ইরানের তাবরিয শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মির্যা আগা খোশগোনাবি তাবরিযের একজন নামকরা আইনজীবী ছিলেন। শাহরিয়ার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা তাবরিযে সমাপ্ত করেন এবং তেহরানের দারুল ফনুন স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন করেন। চিকিৎসাবিদ্যার শেষ পর্যায়ে এসে তা ছেড়ে দেন। শাহরিয়ার নিজ ও পরিবারের জীবন ধারণের জন্য ১৯৩১ সালের দিকে সরকারি দলিল রেজিস্ট্রি তথা তফসিল অফিসে চাকুরিতে যোগদান করেন। প্রথম দিকে নিশাপুরে, পরে মাশহাদে বেশ কিছু দিন চাকুরি জীবন অতিবাহিত করেন। পরবর্তীকালে তেহরানে কৃষি ব্যাংকে চাকুরিরত ছিলেন।
তেহরান থাকাকালীন তিনি সে সময়ের বিখ্যাত কবি মালেকুশ শুয়ারা বাহার, আরিফ কাযভিনি, ফররুখি ইয়াযদি, মিরযাদে এশকি প্রমুখের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের বিভিন্ন কবিতার আসর ও প্রতিযোগিতাগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের সাহচর্যের ফলে তাঁর মাঝে কাব্যপ্রতিভার উন্মেষ ঘটে। কবিতাচর্চার শুরুর দিকে শাহরিয়ার তাঁর কাব্যনাম ‘বেহজাত’ লিখতেন। কিন্তু হাফিযের কাব্য থেকে ভাগ্য গণনার মাধ্যমে পরবর্তীকালে ‘শাহরিয়ার’ ভণিতা ধারণ করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা হলো রুহে পারভা’নে (প্রজাপতির আত্মা) শীর্ষক মাসনাভি (দ্বিপদী) কবিতাÑ যা তৎকালীন কাব্যজগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।
নিশ্চিন্তে বলা যায় যে, শাহরিয়ার ক্ষমতাধর কাব্যপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর সমগ্র কাব্যে মনস্তাত্ত্বিকতা, সংবেদনশীলতা ও কবিসুলভ ঢেউ খেলে যায়। যেখানে কল্পনার ডানায় চড়ে সৃষ্টিশীল ও অনুসন্ধানী হয়ে উড়ে বেড়ান। তাঁর কবিতায় যেকোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন আধুনিকতা ও নব ধারার ঝোঁকপ্রবণতার বৈশিষ্ট্যগুলো অনুভূত হয়ে থাকে। তিনি যেসকল কবিতা নিমার জন্য এবং তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে রচনা করেছেন এবং বিশেষ আকৃতি বা গঠনে তাঁর রচিত কবিতাসমূহ যেমনি বিশ্লেষণধর্মী তেমনি কল্পচিত্রের দিক থেকে সনাতনী ধারার পরিবর্তন প্রকাশের নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছে।
শাহরিয়ারের দিভান তথা কাব্যসমগ্রের মূল অংশ জুড়ে রয়েছে গযল বা গীতি কবিতা। তাঁর কাব্যসমগ্রে তুর্কি ভাষার কবিতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ১৫ হাজার শ্লোক সম্বলিত তাঁর এ কাব্যসমগ্রটি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তুর্কি সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত তাঁর সালা’ম বে হেইদার বা’বা’* শীর্ষক কবিতাটি ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।
ভাষার অনাড়ম্বরতা, সর্বজনীনতা ও বিশ্লেষণধর্মী হওয়ার কারণে শাহরিয়ারের কবিতা ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে। শাহরিয়ার তাঁর হৃদয়ানুভূতি ও কাব্যপ্রতিভার দ্বারা নিজের কল্পনাগুলো ও চিন্তাধারাকে সাধারণের ভাষায় তুলে ধরেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর কবিতা সকলের জন্য বোধগম্য ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।
শাহরিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা বৈচিত্র্যের কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর যে কবিতাগুলো দেশ, সমাজ, ইতিহাস, ধর্ম-দর্শন ও কালের ঘটনা প্রবাহের ওপর রচিত সেগুলোর পরিমাণও কম নয়। বিশেষ করে কল্পনা, বিশ্লেষণ, এমনকি তাঁর কবিতার কাঠামোর নতুনত্ব অন্যান্য সমকালীন কবি থেকে তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। তাঁর কবিতার নিদর্শন হিসাবে কয়েকটি শ্লোক তুলে ধরা হলো :
‘এসেছ, তোমার তরে আমার প্রাণ উৎসর্গিত হোক, তবে এখন কেন?
হে অবিশ্বস্ত! এখন তো আমি নিশ্চল হয়ে পড়ে আছি, তবে এখন কেন?
আনন্দের ঔষধি (তুমি), সেই তো এলে তবে সোহরাবের মৃত্যুর পরে,
হে পাষাণ হৃদয়! আরো আগে আসলেই তো পারতে, এখন কেন?
তোমার তরে আজ ও কালের অবকাশ আমার জীবনে অবশিষ্ট নেই
আমি তোমার আজকের অতিথি, তবে আগামীকালের জন্য কেন?
হে প্রেয়সী আমার! তোমার প্রেমে আমার গোটা যৌবন বিলিয়ে দিয়েছি
এবার তরুণদের সাথে প্রেমানুরাগে মত্ত হও, আমার সাথে কেন?’
ইরানের সমকালীন কাব্যসাহিত্য ধারার আরেকজন উচ্চ মার্গের কবি, লেখক ও সমালোচক হলেন ড. কেইসার আমিনপুর। যাঁকে বিপ্লবোত্তর ফারসি সাহিত্যের পথিকৃৎ বলা হয়ে থাকে। তিনি ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ইরানের খোযেস্তান প্রদেশের অন্তর্গত গুতভান্দ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। দেযফুল শহরে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপনের পর ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের পশু চিকিৎসা বিভাগে ভর্তি হন। কিন্তু এক বছর অধ্যয়নের পর তা ত্যাগ করে তিনি নতুন করে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে ভর্তি হন। ফারসি কবিতা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ তাঁকে সাহিত্যাঙ্গনে টেনে আনে এবং অবশেষে ২০০০ সালে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমকালীন কাব্যে সনাতন ও নবধারা শীর্ষক অভিসন্দর্ভের ওপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন প্রফেসর ড. শাফিয়ে কাদকানি, যিনি নিজেও একজন সমকালীন ধারার অন্যতম কবি।
তিনি তাঁর দীর্ঘ সফল জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা এবং শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি ছাড়াও বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এর মধ্য থেকে ‘সোরুশে নুজাভান’ শীর্ষক মাসিক সাহিত্য সাময়িকীর সম্পাদনা এবং ফারসি ভাষা ও সাহিত্য একাডেমির সদস্য পদ লাভ বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।
২০০০ সালে গাড়ি চালাতে গিয়ে এক দুর্ঘটনায় তাঁর কিডনি দুটি অকেজো হয়ে যায়। এ সত্ত্বেও তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। অত্যধিক ব্যথা-বেদনা ও দুঃখ-কষ্টের সাথে লড়াই করা সত্ত্বেও শিক্ষকতা ও সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রেখেছেন। এমনকি তিনি মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্বেও শ্রেণি কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। অবশেষে অতি সাম্প্রতিককালের আধুনিক কাব্যমহীরুহ ২০০৭ সালের ৩০ অক্টোবর মধ্যরাতে পরলোক গমন করেন।
নিঃসন্দেহে কেইসার আমিনপুর সমকালীন ফারসি কাব্যের সবচেয়ে সৃজনশীল ও জনপ্রিয় মুখ। কেবল কাব্যেই নয়, বরং গদ্য, সমালোচনা সাহিত্য, চিত্রকর্ম ও ক্যালিগ্রাফিতেও তাঁর সমান কৃতিত্ব রয়েছে। ড. কেইসার আমিনপুরের সাহিত্যকর্মের মধ্যে তানাফফোসে সোবহ্ (প্রভাতের নিঃশ্বাস), দার কুচেয়ে অ’ফতা’ব’ (সূর্যের গলি পথে), তুফা’ন দার পারা’নতেয (বন্ধনীর মাঝে ঝড়), যোহর রুযে দাহোম (দশম দিবসের মধ্যাহ্ন), মেছলে চেশমে মেছলে রুদ (যেমন ঝর্না তেমন নদী), বি বা’ল পারিদান (পালকবিহীন ওড়া), অ’ইনেহা’য়ে না’গাহা’ন (অকস্মাৎ দর্পণগুলো), বে গ¦াওলে পারাস্তু (ভরত পাখির ভাষায়), সুন্নাত ভা নুঅ’ভারি দার শে’রে মুঅ’সের (সমকালীন কাব্যে সনাতন ও নতুনধারা), গোলহা’ হামে অ’ফতা’ব গারদা’নান্দ (সবফুলই সূর্যের আলোরোধক), শে’র ভা কুদাক (কবিতা ও শিশু) ও দাস্তুরে যাবা’নে এশ্গ¦ (প্রেমের ব্যাকরণ) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, কেইসার আমিনপুর প্রবন্ধকারের সরাসরি শিক্ষক ছিলেন। এখানে কায়সার আমিনপুরের কাব্যের নমুনাস্বরূপ কয়েকটি শ্লোক তুলে ধরা হলো :
‘আল্লাহ তাআলা গ্রামকে
আর মানুষ শহরকে সৃষ্টি করেছে
কিন্তু কবিরা সৃষ্টি করেছে কল্পনার জগৎ
যা স্বপ্নেও
সে স্বপ্নকে তারা দেখেনি।’
ফারসি সাহিত্যের সমকালীন যুগে যেসকল খ্যাতিমান কবির আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের আলোচনা ওপরে তুলে ধরা হলো। এছাড়া সমকালীন যুগের আধুনিক কাব্যধারায় যেসব কবি খ্যাতির উচ্চমার্গে অবস্থান করেছেন তাঁরা হলেন, পারভিন এতেসামি, আহমেদ শামলু, জালালুদ্দিন হুমায়ি, গুলচিন গিলানি, পারভিয নাতেল খানলারি, মাহদি হামিদি শিরাযি, ফারিদুন তাভাল্লুলি, হামিদ সাবযভারি, ইসমাইল শাহরুদি, মুশফেক কাশানি, ফারিদুন মাশিরি, হোশাং এবতেহাজ, সিমিন বাহমানি, মাহমুদ শাহরুখি, মেহেরদাদ আভেস্তা, মানুচেহের আতাশি, তাহেরে সাফ্ফারযাদে, মুহাম্মাদ রেযা শাফিয়ে কাদকানি, মুহাম্মাদ আলি সেপানলু, আলি মুসা গারমারুদি, নাসরুল্লাহ মারদানি, শামস লাংগারুদি, সালমান হারাতি, আব্দুল জাব্বার কাকায়ি প্রমুখ। (সমাপ্ত)