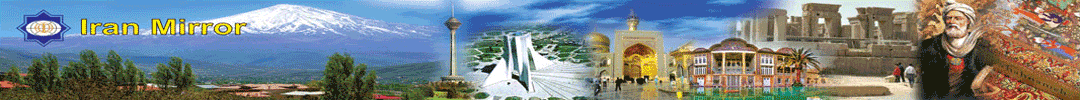শাহনামা কাব্যগ্রন্থ : আধ্যাত্মিকতা, প্রজ্ঞা ও আদর্শের সম্মিলন
পোস্ট হয়েছে: জুন ১৫, ২০২১
শাহনামা কাব্যগ্রন্থ : আধ্যাত্মিকতা, প্রজ্ঞা ও আদর্শের সম্মিলন
ড. তারিক সিরাজী
ফারসি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ও বরেণ্য কবি হাকিম আবুল কাসেম ফেরদৌসি [৯৪০-১০২০/১০২৫ খ্রি. (আনুমানিক)] ছিলেন ইরানের প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য ও গৌরবগাথার সার্থক রূপকার। ইরানের মহাকবি হিসাবেই তিনি সমধিক পরিচিত। তাঁর মর্যাদার এই বিশালত্বের কারণে তাঁর জীবন-কাহিনী রূপকথার সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। বিশ^বিশ্রুত বীরত্বগাথা শাহনামা রচনার মধ্য দিয়ে তিনি মূলত ইরানিদের জাতিসত্তা ও ফারসি ভাষার মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যকে সংরক্ষণ করেছেন। এ কালজয়ী সাহিত্যকর্মটির গুরুত্ব অনুধাবন করে পৃথিবীর অধিকাংশ জীবন্ত ভাষায় এ গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে এবং অসংখ্য সাহিত্যামোদীর কাছে তা হয়েছে সমাদৃত। বর্তমানে গ্রন্থটি বিশ^সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। যে কারণে এ কাব্যগ্রন্থটিকে কেবল ইরানি ও ফারসি ভাষাভাষীদের সম্পদ হিসাবেই পরিগণিত করা যায় না। কারণ, এর এক বৈশ্বিক আবেদন রয়েছেÑ যা সাহিত্যমোদী, গবেষক ও সাধারণ মানুষের কাছেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বহু গবেষক মানের বিচারে শাহনামা-কে বিশে^ রচিত অনেক মহাকাব্যের চেয়ে উন্নততর বলে অভিহিত করে থাকেন। শুধু তাই নয়, শাহনামার অনুকরণে অনেক বীরত্বগাথাও রচিত হয়েছেÑ যা এ গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা ও গুরুত্বের প্রমাণ বহন করে। উল্লেখ্য যে, জার্মান প্রাচ্য ও ভাষাতত্ত্ববিদ থিওডর নোল্ডেক ও হারমান এথি (ঞযবড়ফড়ৎ ঘস্খষফবশব ধহফ ঐবৎসধহহ ঊঃযল্ক) বিস্তর পরিশ্রম ও গবেষণার মাধ্যমে এ অমর কবির নির্ভরযোগ্য জীবনী ও শাহনামার প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনে সফল হয়েছিলেন।
ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রায় তিনশ বছরকালব্যাপী পারস্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ফারসি ভাষা উপযুক্ত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ও অবহেলিত হয়ে উঠেছিল। ফেরদৌসি তাঁর এ রচনার মাধ্যমে লুপ্তপ্রায় পারস্যের প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ফারসি ভাষা পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসেন। তিনি তাঁর শাহনামার শ্লোকে শ্লোকে জাতীয় অনুভূতি, উপলব্ধি ও চেতনার এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যার দ্বারা ইরানি জনগণ ব্যাপকভাবে জাতীয় মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে শাহনামা হলো ভিনদেশি শাসনশৃঙ্খলের বিরুদ্ধে বহুকালের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ এবং জাতীয়তার মূর্ত প্রতীক।
শাহনামা কাব্যগ্রন্থের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে মূলত প্রাচীন লোকগাথা, ইতিহাস, ধর্মগ্রন্থসমূহ, গল্প, উপাখ্যান, ও কিংবদন্তি থেকে। এছাড়া এতে বর্ণিত ঘটনাসমূহের ব্যাপ্তিকাল প্রায় তিন হাজার আটশ বছরের অধিক। কবি ফেরদৌসি এ দীর্ঘ সময়কালকে উপাখ্যান আর ইতিহাস এ দু’টি ভাগে বিন্যস্ত করেছেন। এছাড়া ঊনচল্লিশটি রাজবংশের শাসন-বিবরণী এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, শাহনামা গ্রন্থটি সুবিন্যস্ত আকারে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে ফেরদৌসি তাঁর জনৈক বন্ধু কবি দাকিকির পা-ুলিপির সাহায্য নিয়েছিলেন। শাহনামা রচনায় এটি ছিল ফেরদৌসির সবচেয়ে বড় সূত্র। কারণ, ফেরদৌসির পূর্বে সর্বশেষ শাহনামা রচয়িতা ছিলেন কবি দাকিকি তুসি। মূলত দাকিকি তৎকালীন শাসক নুহ ইবনে মানসুর সামানির নির্দেশে শাহনামা রচনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং এক হাজার পঙ্ক্তি রচনাও করেছিলেন। কিন্তু কবি দাকিকি পুরো রচনার কাজ সম্পন্ন করে যেতে পারেননি। তথ্য ও উপাত্তের প্রমাণস্বরূপ ফেরদৌসি তাঁর শাহনামায় দাকিকির উল্লিখিত এক হাজার বেইত তথা পঙ্ক্তি অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ফেরদৌসির শাহনামায় যে বিষয়গুলোর উল্লেখ রয়েছে তা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, বীরদের মানসিকতা, প্রচেষ্টা, ন্যায়পরায়ণতা, রাজনীতি, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি। এতে শিক্ষণীয় অনেক বিষয়ের উল্লেখের পাশাপাশি রয়েছে বিশ্বদর্শন।
সাহিত্যামোদীদের নিকট কবি ফেরদৌসির গুরুত্ব ও আবেদন কেবল তাঁর ভাষার লালিত্য ও মাধুর্যের মধ্যেই নিহিত নয়; বরং তাঁর ধর্মীয় চেতনা ও জাতীয়তাবাদের মাঝেও বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর রচিত শাহনামা গ্রন্থের পরতে পরতে গল্পের কাহিনীগুলো এমনিভাবে বিধৃত রয়েছে যে প্রতিটি চরিত্রই যেন একেক জন পর্যবেক্ষক হিসাবে কাজ করছে। যে কারণে এ মহাকাব্য সাহিত্যের একটি উচ্চমার্গে গিয়ে পৌঁছেছে। ফেরদৌসি তাঁর শৈল্পিক বর্ণনাগুলোতে অলক্সকারশাস্ত্রীয় উপাদানগুলোও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন, যা ছিল সে সময়ের বিরল ব্যবহার। এ ছাড়া তিনি প্রচলিত সাহিত্যরীতির বিপরীতে অন্তর্নিহিত বর্ণনার দিকে অগ্রসর হয়েছেন আর এটি ছিল তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবিত শৈলী। এ ধরনের সাহিত্যশৈলী ফারসি সাহিত্যে বিরল। তিনি তাঁর শাহনামা কাব্যগ্রন্থকে ধ্বনি, শব্দ চয়ন, এমনকি ব্যাকরণসহ সকল স্তরে একটি সুশৃঙ্খল গঠন কাঠামোর মাধ্যমে বিন্যস্ত করেছেন। যার ফলে এটি ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকেও সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত অবস্থানে রয়েছে।
কবি ফেরদৌসি ৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে শাহনামা রচনা শুরু করেন এবং ১০১০ খ্রিস্টাব্দে ৭৫ বছর বয়সে তা সমাপ্ত করেন। তিনি তাঁর যৌবনকালসহ পরবর্তী পুরো জীবনকালটাই এ সাহিত্যকর্ম রচনায় ব্যয় করেছিলেন। দীর্ঘ ত্রিশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তিনি যে শাহনামা কাব্যগ্রন্থটি রচনা করে গোটা পারস্যকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেনÑ তা তাঁর বক্তব্যেই নিহিত রয়েছে। তিনি বলেন :
بسي رنج بردم در اين سال سي عجم زنده كردم بدين پارسي
আমি বহু কষ্ট ভোগ করেছি এই দীর্ঘ ত্রিশটি বছর ধরে
আর এ পারসির (ফারসি) মাধ্যমে পারস্যকে জীবন্ত করেছি।
ফেরদৌসির যুগে আনুষ্ঠানিকভাবে গল্প বলা ও শোনার একটা প্রচলন ছিল। কারণ, সে সময় বেশিরভাগ লোকই পড়তে ও লিখতে জানত না। এ ধরনের গল্প পাঠের আসরে পরিবেশন করা হতো ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনী। পুরাণপাঠের এ কাজটিকে বলা হয় নাক্কালি আর যিনি কাহিনীগুলো পাঠ করে শোনান বা উপস্থাপন করেন তাঁকে বলা হয় নাক্কাল বা পুরাণপাঠকারী। তাঁর হাতে থাকত একটি লাঠি যা দিয়ে তিনি চরিত্র চিত্রায়ণ করতেন। বলা যায় ঠিক আমাদের দেশের পুথি পাঠের ন্যায়। অনেকের অভিমত পুরাণপাঠকারীর গল্প বলার কাজটিকে সহজতর ও প্রাণবন্ত করার লক্ষ্যেই ফেরদৌসি সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় পৌরাণিক কাহিনীগুলো রচনা করে তা শাহানামা কাব্যগ্রন্থে তুলে ধরেছেন। কবি ফেরদৌসি নিজেই শাহনামা গ্রন্থ রচনার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন :
توانم مگر پايهاي ساختن بر شاخ آن سرو سايه فکن
کزين نامور نامةشهريار به گيتي بمانم يکييادگار
تو اين را دروغ و فسانه مدان به رنگ فسون و بهانه مدان
ازو هر چه اندر خورد با خرد دگر بر ره رمز و معني برد
يکي نامه بود از گه باستان فراوان بدو اندرون داستان
پراگنده در دست هر موبدي ازو بهرهاي نزد هر بخردي
يکي پهلوان بود دهقان نژاد دلير و بزرگ و خردمند و راد
پژوهندةروزگارنخست گذشتهسخنهاهمهبازجست
ز هر کشوري موبدي سالخورد بياورد کاين نامه را ياد کرد
بپرسيدشان از کيان جهان وزان نامداران فرخ مهان
که گيتي به آغاز چون داشتند که ايدون به ما خوار بگذاشتند
چه گونه سرآمد به نيک اختري برايشان همه روز کند آوري
بگفتند پيشش يکايک مهان سخنهاي شاهان و گشت جهان
چو بشنيد ازيشان سپهبد سخن يکي نامور نامه افکند بن
چنين يادگاري شد اندر جهان برو آفرين از کهان و مهان
‘আমি উড়ন্ত জলধর, কিন্তু পদযুগ বিন্যস্ত করেছি
সেই ছায়াচ্ছন্ন দেবদারুর উন্নত শাখায়।
কারণ, যশস্বী নরপতিগণের এই ইতিকথা
দুনিয়ায় আমার স্মারক হয়ে থাকবে।
তুমি এ’কে অলীক কাহিনী বলে মনে করো না,
গণ্য করো না তাকে যুগ-চিত্তের উৎসার মাত্র বলে।
এর কিছু কাহিনীতে রয়েছে বুদ্ধির ও জ্ঞানের দীপ্তি,
অন্যরা নিজেদের মধ্যে বহন করছে রহস্যময় তাৎপর্য।
অতীত কালে ছিল পূরাকীর্তি সম্বলিত এক গাথা,
তার মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল অনেক উপাখ্যান।
প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির মুখে মুখে তা ছড়িয়েছিল,
সেগুলি থেকে তারা সংগ্রহ করত প্রজ্ঞা ও তত্ত্বের সম্পদ।
কোন নিভৃত গ্রামাঞ্চলের এক বীর সন্তান
বর্ষীয়ান সাহসী জ্ঞানী ও দানশীলÑ
আদিম যুগের সেই ইতিকথার খোঁজে তৎপর হলো,
কাহিনীগুলোর উদ্ধার মানসে সে ঘুরে বেড়ালো বহুদিন।
ফিরলো সে বহু নগরীর পথে পথে,
ফলে সংগৃহীত হলো এই গাথা।
সবারই কাছে সে জিজ্ঞাস করেছে কেয়ানী বংশের আদিম ইতিহাস,
জেনেছে সে তাদের থেকে যশস্বী সেই নক্ষত্রের পরিচয়।
জেনেছে, সেই আদিম যুগে রাজারা কেমন করে শাসন করতেন পৃথিবী,
আর আজ কেমন করে লুপ্ত হয়েছে সেই কীর্তিকলাপ?
প্রশ্ন করেছে সে, কেমন করে অস্ত গেলো সেই সুভগ নক্ষত্র,
কাল কেমন ছিল সেই বীরবৃন্দের উপর?
দলপতিগণ একে একে বিবৃত করেছেন তার কাছে
রাজ-রাজড়াদের কীর্তিগাথা ও জগতের পরিবর্তনের ইতিহাস।
সেই বীর-জ্ঞানী তাঁদের কাছ থেকে জেনেছে অতীতের সব কীর্তি,
তারপর সেই সংগ্রহ থেকে রচিত হয়েছে এক মহান পুরাণ কথা।
জগতে সেই গাথাই হয়ে আছে অতীতের স্মৃতি,
সর্বত্র জ্ঞানী ও ধর্মবেত্তা জানিয়েছে তাকে স্বাগতম।’(মনিরউদ্দীন ইউসুফ অনূদিত শাহনামা, ১ম খ-, পৃ. ১৩-১৪)
কবি ফেরদৌসি তাঁর এ কাব্যগ্রন্থটি শুরু করেছেন মহান আল্লাহ তায়ালার নামে। তিনি এ সাহিত্যকর্মে দেখাতে চেয়েছেন যে, মানুষ এক আল্লাহর সৃষ্টজীব। সমগ্র বিশ^জগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি হলেন মহান আল্লাহ। ইসলামের ন্যায় সত্যিকার ও পরম ধর্মের মধ্যেই শান্তি বিরাজমান। আমাদের চিন্তা ও দৃষ্টির সীমারেখার ভিতর ও বাহিরের সকল কিছুই আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি। তিনি তাঁর এ গন্থের শুরু-সূচনাতে সহজ ও সাবলীল ভাষায় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ব্যক্ত করেছেন। কবি বলেন :
به نام خداوند جان و خرد کزين برتر انديشه برنگذرد
خداوند نام و خداوند جاي خداوند روزي ده رهنماي
خداوند کيوان و گردان سپهر فروزنده ماه و ناهيد و مهر
ز نام و نشان و گمان برترست نگارندهۀبرشدهپيکرست
به بينندگان آفريننده را نبيني مرنجان دو بيننده را
نيابد بدو نيز انديشه راه که او برتر از نام و از جايگاه
سخن هر چه زين گوهران بگذرد نيابد بدو راه جان و خرد
خرد گر سخن برگزيند همي همان را گزيند که بيند همي
‘প্রাণ ও প্রজ্ঞার প্রভুর নামে শুরু করি,
অতিক্রম করতে পারে না কল্পনা তাঁর নামের সীমা।
প্রভু তিনি নামের, প্রভু তিনি স্থানের,
তিনিই আহার্য দান করেন, তিনিই পথ দেখান।
তিনি প্রভু পৃথিবীর ও ঘূর্ণ্যমান আকাশের,
চন্দ্র-সূর্য ও শুকতারা আলো পায় তাঁর থেকে।
বর্ণনা, ইঙ্গিত ও ধারণার ঊর্ধ্বে তাঁর অবস্থান,
চিত্রকরের সৃষ্টির তিনি মূলতত্ত্ব।
সৃষ্ট জীবের রক্ষণে তিনি সদাতৎপর,
তাঁর অস্তিত্বে সংশয়াপন্ন ব্যক্তির দুঃখও তিনিই দূর করেন।
কল্পনা পথ পায় না তাঁর মধ্যে;
কারণ, নাম ও স্থানের বাইরে তিনি।
কিন্তু বাণী থেকে নাম ও স্থান অন্তর্হিত হলে
প্রাণ ও প্রজ্ঞা দুই-ই স্তব্ধ ও নিশ্চল হয়ে যায়।
তাই, প্রজ্ঞা ভাষাকে নিয়োজিত করে
অমূর্তকে চাক্ষুষ করার জন্যে।’ (মনিরউদ্দীন ইউসুফ অনূদিত শাহনামা, ১ম খ-, পৃ. ১)
ফেরদৌসি তাঁর শাহনামায় প্রজ্ঞা ও যুক্তিনির্ভর একটি আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। সে বিষয়বস্তুর দিকে তাকালে শাহানামা কাব্যগ্রন্থে যে তাঁর আধ্যাত্মিকতার অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে, তার পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। কবি বলেন :
حکيم اين جهان را چو دريا نهاد برانگيخته موج ازو تندباد
چو هفتاد کشتي برو ساخته همه بادبانها برافراخته
يکي پهن کشتي بسان عروس بياراسته همچو چشم خروس
محمد بدو اندرون با علي همان اهل بيت نبي و ولي
خردمند کز دور دريا بديد کرانه نه پيدا و بن ناپديد
بدانست کو موج خواهد زدن کس از غرق بيرون نخواهد شدن
‘এই জগৎকে জ্ঞান কর এক সমুদ্র বলে,
যেখানে গর্জন করে ফিরছে প্রবল ঝঞ্ঝা ক্রুদ্ধ ঊর্মিদল;
যেখানে সত্তরটি অর্ণবযান অনুকূল হাওয়ায়
তুলে দিয়েছে তাদের প্রসারিত বাদবান।
তার মধ্যে একটি জলযান সজ্জিত কনের বেশে
রাজহংসের গতিতে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে।
তার মধ্যে রয়েছেন মুহাম্মদ ও আলী
এবং নবী ও আলী পরিবারের সকলে।
দূরে দাঁড়িয়ে জ্ঞানীজন দেখতে পায়Ñ
এই সমুদ্র অসীমÑতার তটরেখা অদৃশ্য।
তারা বুঝতে পারে উত্তাল তরঙ্গ যখন হানবে তার অভিঘাত,
তখন হয়তো নিমজ্জন থেকে কেউই রক্ষা পাবে না।’ (মনিরউদ্দীন ইউসুফ অনূদিত শাহনামা, ১ম খ-,পৃ. ১১)
ধারণা করা হয়ে থাকে যে, উপরে উল্লিখিত পঙ্ক্তিগুলোতে রাসূল (সা.)-এর একটি হাদিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে হাদিসটির মূল বক্তব্য হলো এই যে, মুহাম্মাদ (সা.)- এর উম্মত খুব শীঘ্রই তিহাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। যার বাহাত্তরটি দলই যাবে জাহান্নামে এবং একটি দল যাবে জান্নাতে। যদিও কবিতার পঙ্ক্তিতে সত্তরটি কিশ্তি তথা জাহাজের কথা উল্লেখ রয়েছে। এখানে রূপকভাবে গোটা জগতকে সাগর হিসাবে জ্ঞান করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়াটা হলো সাগরতুল্য। আর এ সাগরে অবস্থানরত সত্তরটি জাহাজ হলো সত্তরটি দল। মহান আল্লাহ তায়ালা এ বিশ্বকে সমুদ্ররূপে সৃষ্টি করেছেন। এ পৃথিবীকে যেহেতু তিনি সমুদ্রের ন্যায় সৃষ্টি করেছেন তাই নানাবিধ ঘটনাপ্রবাহে পূর্ণ রয়েছে এ পৃথিবী। এতে যেমন রয়েছে বিপদ ও বিচ্যুতির আশংকা, তেমনি রয়েছে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের সম্ভাবনা। উত্তাল তরঙ্গ মাঝে অস্থির বাতাস, তুফান ও ধ্বংসাত্মক দমকা হাওয়া জগতের এ সমুদ্রকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। এই সংকটময় অবস্থায় যারা অবিচল থেকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে আঁকড়ে ধরবে তারাই তথা সে দলটি সফলতা লাভ করবে। শাহনামায় বর্ণিত এইরূপ অনেক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ফেরদৌসির আধ্যাত্মিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।
কবি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল (সা.)- এর আনুগত্যের প্রতি জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে মুক্তির পথ অন্বেষণ করা এবং অধঃপতিত জীবন থেকে বাঁচার একমাত্র পথ ও অবলম্বন হলো পয়গম্বরের বাণীকে ধারণ করা। যে বাণী ও আদর্শকে ধারণ করলে হৃদয়ের অন্ধকারকে দূরীভূত করে আলোয় উদ্ভাসিত হওয়া সম্ভব। কবি বলেন :
ترا دانش و دين رهاند درست در رستگاري ببايدت جست
وگر دل نخواهي که باشد نژند نخواهي که دايم بوي مستمند
به گفتار پيغمبرت راه جوي دل از تيرگيها بدين آب شوي
‘তোমার জ্ঞান ও ধর্মকে কর কুসংস্কার থেকে মুক্ত,
মুক্তির পথ অন্বেষণ করাই হলো তোমার কাজ।
অধঃপতিত জীবন থেকে উঠে আসার যদি বাসনা থাকে
যদি বাসনা থাকে চিরদিনের দুঃখ থেকে রেহাই পাওয়ার,Ñ
তবে তোমার পয়গম্বরের বাণী নিয়ে কর পথের অন্বেষণÑ
হৃদয়ের অন্ধকার গুহা সকলকে কর তার আলোয় আলোকিত।’ (মনিরউদ্দীন ইউসুফ অনূদিত শাহনামা, ১ম খ-, পৃ. ১০)
আমরা জানি যে, মহাকাব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে পৌরাণিক কাহিনীগুলোর বিশ্লেষণ, মহান বীরযোদ্ধাদের গুণ, বৈশিষ্ট্য ও কীর্তি বর্ণনা এবং বিভিন্ন জাতির ভাগ্য নির্মাণে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস তুলে ধরা। পাশাপাশি সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও আত্মউদ্দীপক বিষয়গুলোও এতে সমভাবে অনুরণিত হয়ে থাকে। এছাড়া মাহাকাব্যে ফেলে আসা অতীত যুগের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, একটি জাতি প্রতিষ্ঠার ঘটনা ও নিজের প্রসিদ্ধ বীরত্বগাথা বিধৃত থাকে।
মহাকাব্যের রচয়িতাগণ এ ধরনের সাহিত্যকর্মে নিজ জাতি ও মানবসভ্যতার আশা-আকাক্সক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকেন এবং তাঁদের ভিতরের রহস্যকে নিজদের সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে উন্মোচিত করেন। তাঁরা মনে করেন জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য ও বীরত্ব জানার মধ্য দিয়ে আত্মপরিচয় লাভ করা যায় এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা ও জাতীয় আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠায় উজ্জীবিত হওয়া যায়। মহাকাব্যে বিধৃত বীরদের কাহিনী থেকে শিক্ষা নিয়ে অত্যাচার ও নীপিড়নের বিরুদ্ধে জাতি ও দেশকে ধ্বংস থেকে রক্ষার উপায় ও অবলম্বন অন্বেষণ করা যায়। বিশ্বে যে কয়টি নির্ভরযোগ্য মহাকাব্য রয়েছে সেগুলোর মূল বক্তব্য ও বিষয় অনেকটা একই বলে প্রতিভাত হয়।
ফেরদৌসি তাঁর শাহনামা কাব্যগ্রন্থে প্রাচীন পারস্যের ইতিহাস-ঐতিহ্য বর্ণনার মাধ্যমে চরিত্র গঠন, বীরত্ব, পা-িত্য, বিচক্ষণতা ও জ্ঞানের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। জ্ঞানের যে বিশাল শক্তি রয়েছে সে বিষয়ে তিনি বলেন :
توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پير برنا بود
যে জ্ঞানী সেই শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান,
আর জ্ঞানসমৃদ্ধ বৃদ্ধের হৃদয় চির যৌবন থাকে।
জ্ঞান ও প্রজ্ঞা যে অমূল্য সম্পদ সে সম্পর্কে কবি ফেরদৌসি অন্যত্র বলেন :
خرد بهتر از هر چه ايزد بداد ستايش خرد را به از راه داد
خرد رهنماي و خرد دلگشاي خرد دست گيرد به هر دو سراي
ازو شادماني وزويت غميست وزويت فزوني وزويت کميست
خرد تيره و مرد روشن روان نباشد همي شادمان يک زمان
چه گفت آن خردمند مرد خرد که دانا ز گفتار از برخورد
کسي کو خرد را ندارد ز پيش دلش گردد از کردۀخويشريش
মহান প্রভুর দানের মধ্যে সবচেয়ে অধিক মূল্যবান হলো জ্ঞান,
জ্ঞানের প্রশংসা করাই বদান্যতার পথে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।
জ্ঞান পথের দিশারী আর জ্ঞানই হলো হৃদয়-মুক্তকারী
জ্ঞানে মাধ্যমেই উভয় জগতকে আঁকড়ে ধরা যায়।
জ্ঞানের মাধ্যমে জানা যায় আনন্দ ও দুঃখকে
এ (জ্ঞান) থেকে অর্জিত হয় উৎকর্ষ আর এর (জ্ঞান) অভাবে আসে খর্বতা।
জ্ঞান অন্ধকার ও জড়ত্বকে দেয় চলমান ঔজ্জ্বল্য
জ্ঞান ছাড়া এক মুহূর্তও প্রফুল্লে ভরে ওঠে না মন।
জ্ঞান সম্পর্কে কতই না সুন্দর বলেছেন জ্ঞানীজনÑ
জ্ঞানীজন বাগ্মিতায় হয়ে ওঠেন অনন্য উচ্চমার্গীয়।
যার রয়েছে জ্ঞানের বিস্তর অভাব
সে নিজেকে দুষ্টক্ষতের ভা-ারে পরিণত করেছে।
ফেরদৌসি শাহনামা রচনা করে ফারসি ভাষাকে নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করেন। এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি প্রতিরোধের মানসিকতা, খোদার আনুগত্য, স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু শাহনামার বড় পরিচয় হচ্ছে ফারসি ভাষার অস্তিত্বের সনদ হিসাবে।
ফেরদৌসি শাহনামা কাব্যগ্রন্থে যুদ্ধ ও বীরত্বপূর্ণ কাহিনী বর্ণনার পাশাপাশি তথ্যপূর্ণ উপদেশাদি, ন্যায়পরায়ণতা, বদান্যতা, মহত্ত্ব ও নৈতিক কর্তব্যাদি সম্পর্কে বক্তব্য দিতেও সচেষ্ট ছিলেন। শাহনামায় বর্ণিত এমনি উপদেশ সম্পর্কিত কয়েকটি পঙ্ক্তি নিচে তুলে ধরা হলো :
بيا تا جهان را به بد نسپريم به کوشش، همه دست نيکي بريم
نماند همي نيک و بد پايدار همان بِه، که نيکي بود يادگار
نه گنج و نه ديهيم و کاخ بلند نخواهد بدن مر ترا سودمند
فريدون فرخ فرشته نبود ز مُشک و ز عنبر سرشته نبود
بِه داد و دهش يافت اين نيکويي تو داد و دهش کن فريدون تويي
এসো, এ পৃথিবীকে যেনো আমরা অকল্যাণের দিকে ঠেলে না দেই,
প্রচেষ্টার মাধ্যমে একে সামগ্রিক কল্যাণে পরিণত করবো।
ভালো-মন্দ কিছুই স্থায়ী রবে না,
তবে কল্যাণকর স্মৃতি ধরে রাখাই উত্তম।
সুউচ্চ প্রাসাদ, ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্য
তোমার কোনো কল্যাণেই আসবে না
ফরিদুন কোনো ফেরেশতা ছিলো না,
কিংবা কোনো মৃগনাভি বা কস্তুরী দ্বারাও সৃষ্ট নয় সে।
সেতো ন্যায়পরায়ণতা ও বদান্যতা দিয়ে এ মহত্ত্বের অধিকারী হয়েছে,
তুমিও ন্যায়পরায়ণতা ও বদান্যতা অর্জন কর, তবেই তুমি হবে ফরিদুন ।
ফেরদৌসির শাহনামা কাব্যগ্রন্থে তাঁর জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মনে করেন এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে মনুষত্বই শ্রেষ্ঠ আর জ্ঞান ছাড়া সে মনুষত্ব অজির্ত হয় না। সৎ ও সততার দ্বারাই কেবল সকলের মাঝে সাম্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। কবি বলেন :
دگر گفت روشن روان آن کسي که کوتاه گويد به معني بسي
چو گفتار بيهوده بسيار گشت سخنگوي در مردمي خوار گشت
هنر جوي و تيمار بيشي مخور که گيتي سپنج است و ما برگذر
بگيتي به از مردمي کار نيست بدين با تو دانش به پيکار نيست
ز دانش چو جان ترا مايه نيست بِه از خاموشي هيچ پيرايه نيست
সে (বুজুর্গ মেহের নুশিরওয়ানকে) বললো: সে-ই আলোকিত আত্মার অধিকারী
যে সংক্ষেপে অধিক অর্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলে।
যদি বক্তব্য বহুলাংশে অনর্থক হয়ে ওঠে
তবে লোকদের কাছে বক্তা তুচ্ছে পরিণত হয়।
জ্ঞান অন্বেষণ কর আর দুঃখকে প্রশ্রয় দিও না
এ পৃথিবী ক্ষণিকের, আর আমাদের চলে যেতেই হবে।
এ জগতে মনুষ্যত্ব বৈ আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নয়
তাই জ্ঞান ব্যতিরেকে তোমার শরীরের কোনো মূল্য নেই।
যদি জ্ঞানসমৃদ্ধ আত্মা তোমার নাই বা থাকে
তবে মৌনতা ছাড়া তোমার আর কোনো ভূষণ নেই।
পুরো শাহনামাই চিত্রকল্পে ভরপুর। যুদ্ধ-বিগ্রহের চিত্র এবং এর চরিত্রগুলো প্রাণবন্তভাবে এ গ্রন্থে অনুরণিত হয়েছে। পাশাপাশি এতে আধ্যাত্মিকতা, প্রজ্ঞা, আদর্শ এবং জীবনঘনিষ্ঠ নানা উপদেশও বাণী এমনিভাবে বিধৃত রয়েছে যে, পাঠক সহসাই তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। এছাড়া শাহনামায় বর্ণিত প্রতিটি কাহিনীতে রয়েছে একেকটি উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয়। কবি অভিযানের কাহিনীতেও পাঠকদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেনÑ যা সিনেমার পর্দার মতো কাজ করেছে। আর এতেই শাহনামার বিশ^জনীনতার প্রমাণ মেলে। এ গ্রন্থের আবেদন পাঠক হৃদয়ে যুগ যুগ ধরে অক্ষুণœ থাকবে। আর তাঁর প্রদত্ত বাণী নিজ নিজ জাতির জন্য হয়ে থাকবে শিক্ষণীয় ।
তথ্যসূত্র
১. আবদুল মওদুদ (১৯৮০ খ্রি.) : মুসলিম মনীষা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
২. আহমাদ তামিমদারি (২০০৭ খ্রি.) : ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস, আলহুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ইরান।
৩. আবুল কাসেম ফেরদৌসী (১৯৭৭ খ্রি.) : ফেরদৌসীর শাহনামা (মনিরউদ্দীন ইউসুফ অনূদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৪. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী (২০১৪ খ্রি.) : ফারসি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, বাড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
৫. সাদেক রেযা যাদে শাফাক (১৩৫২ সৌরবর্ষ) : তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান (ইরানি সাহিত্যের ইতিহাস), এনতেশারাতে দানেশগাহে পাহলাভি, ইরান।
৬. হরেন্দ্র চন্দ্র পাল (১৩৬০ বঙ্গাব্দ) : পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস, প্রকাশক অজিত চট্ট ঘোষ, শ্রী জগদীশ প্রেস, কলকাতা।
৭. নিউজ লেটার, (ঢাকাস্থ ইরানি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মুখপত্র), ৩য় সংখ্যা, মে-জুন, ২০১৩।
৮. যঃঃঢ়ং://মধহলড়ড়ৎ.হবঃ/ভবৎফড়ঁংর/ংযধযহধসব
লেখক : অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়