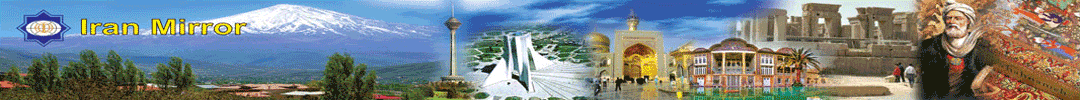বাংলাদেশের ঐতিহাসিক মসজিদের ইতিকথা
পোস্ট হয়েছে: অক্টোবর ১৯, ২০২০
রাশিদুল ইসলাম
ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর গৌড় জয়ের পরে ও দিল্লি সালতানাত আমলে ভারতবর্ষে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপবাসীরা শাহী বাংলাকে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী বাণিজ্য দেশ হিসেবে গণ্য করত। বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলায় ৬৯ হিজরি সনে নির্মিত একটি মসজিদের সন্ধান পাওয়া গেছে। মসজিদটির কেবল ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট থাকায় এটি স্থানীয়ভাবে ‘হারানো মসজিদ’ নামে পরিচিত। এই মসজিদটিকে বাংলাদেশের তথা দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে পুরনো মসজিদ বলে ধারণা করা হয়। মসজিদের স্থাপত্যের কথা বলতে গেলে বলতে হয় ইসলামিক এবং মুঘল স্থাপত্যের কথা। বাংলার সালতানাত ছিল ১৩৪২ থেকে ১৫৭৬ এর মধ্যবর্তী সেই সময় যখন মধ্য এশীয় বংশোদ্ভূত মুসলিম নবাবেরা মুঘল সাম্রাজ্য থেকে প্রভাবমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে শাসন করছিলেন। এই সময়ের অধিকাংশ মুসলিম স্থাপত্য পাওয়া যায় গৌড় অঞ্চলে, যা আজকের রাজশাহী বিভাগ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলা জুড়ে ছিল। এই সময়ের স্থাপত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল স্থানীয় বাঙালি স্থাপত্য ঐতিহ্যের প্রভাব। সালতানাতের স্থাপত্যের প্রভাব বিস্তার করেছিল ষাট গম্বুজ মসজিদ, সোনা মসজিদ এবং কুসুম্বা মসজিদ এর মতো স্থাপত্যতে।
১৫৭৬ এর দিকে মুঘল সাম্রাজ্য বাংলার বেশিরভাগ জায়গায় বিস্তার লাভ করে। ঢাকা মুঘলদের সামরিক ঘাঁটি হিসেবে আবির্ভূত হয়। ১৬০৮ সালে সুবাদার প্রথম ইসলাম খান শহরটিকে বাংলা সুবাহর রাজধানী হিসেবে ঘোষণা দিলে নগরায়ন এবং আবাসনের ব্যাপক উন্নতির ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং এই সময়ে অসংখ্য মসজিদ এবং দুর্গ নির্মাণ হতে থাকে। বড় কাটরা নির্মাণ করা হয়েছিল ১৬৪৪ থেকে ১৬৪৬ সালের মধ্যে, সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজার দাপ্তরিক বাসভবন হিসেবে।
আজকের বাংলাদেশে ভারতীয় মুঘল স্থাপত্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় সুবেদার শায়েস্তা খানের শাসনামলে, যিনি আধুনিক নগরায়ন ও সরকারি স্থাপত্যকে উৎসাহ দিয়ে একটি বিশাল মাত্রার নগরায়ন ও অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ শুরু করেন। তিনি শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং প্রদেশজুড়ে অসংখ্য বিশাল স্থাপত্য, যেমন মসজিদ, সমাধিসৌধ এবং প্রাসাদ নির্মাণে উৎসাহ দিয়েছেন, যেগুলো কিছু সেরা মুঘল স্থাপত্য নিদর্শনের প্রতিনিধিত্ব করত। শায়েস্তা খান লালবাগ কেল্লা (আওরঙ্গবাদ কেল্লা নামেও পরিচিত), চক বাজার মসজিদ, সাত মসজিদ এবং ছোট কাটরার ব্যাপক সম্প্রসারণ করেন। তিনি তাঁর কন্যা পরীবিবির সমাধিসৌধের নির্মাণ কাজ তদারকি করেন।
বাংলাদেশের কয়েকটি প্রাচীন মসজিদ
বাংলাদেশে মুঘল আমলের বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংস হয়ে গেলেও এখনও টিকে আছে অনেক নিদর্শন। এর মধ্যে প্রাচীন মসজিদগুলো অন্যতম। বাংলাদেশে অবস্থিত কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী মসজিদের দেখা মিলেছে। এখনো কালের গর্ভে ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিষ্কার হচ্ছে অনেক প্রাচীন মসজিদ। জানান দিচ্ছে এদেশের সুপ্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ইতিবৃত্ত।
বাবা আদম মসজিদ
মুন্সীগঞ্জের দরগাবাড়ি গ্রামে ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে বাবা আদম মসজিদটি নির্মিত হয়। এ মসজিদ চত্বরে রয়েছে বাবা আদমের (র.) মাজার। ছয় গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটির দৈর্ঘ্য ৪৩ ফুট ও প্রস্থ ৩৬ ফুট। বর্তমানে বাবা আদম মসজিদটি বাংলাদেশ প্রতœতত্ত্ব অধিদফতরের তত্ত্বাবধানে রয়েছে।
দারাসবাড়ি মসজিদ
চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে দারাসবাড়ি মসজিদ অবস্থিত। ১৪৯৩ সালে নির্মাণের পর মসজিদটি ফিরোজপুর জামে মসজিদ নামে পরিচিত ছিল। মসজিদটি দীর্ঘদিন মাটিচাপা ছিল, যা গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে উন্মোচন করা হয়।
ছোট সোনা মসজিদ
চাঁপাইনবাবগঞ্জে আরও একটি ঐতিহাসিক মসজিদ রয়েছে। এ মসজিদও ১৪৯৩ সালে নির্মিত হয়। শিলালিপি থেকে জানা যায়, মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ওয়ালি মোহাম্মদ। উত্তর-দক্ষিণে ৮২ ফুট লম্বা ও পূর্ব-পশ্চিমে ৫২ দশমিক পাঁচ ফুট চওড়া মসজিদটি সম্পূর্ণ সোনালি রঙে ঢাকা ছিল। তাই একে ‘গৌড়ের রতœ’ বলা হতো।
বাঘা মসজিদ
রাজশাহী সদর থেকে ৪১ কিলোমিটার দূরে বাঘা উপজেলায় ঐতিহাসিক বাঘা মসজিদটি অবস্থিত। ১৫২৩ সালে আলাউদ্দিন শাহের ছেলে সুলতান নুসরাত শাহ এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। ২৫৬ বিঘা জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে ১০টি গম্বুজ রয়েছে। ২২ দশমিক ৯২ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১২ দশমিক ১৮ মিটার প্রস্থের বাঘা মসজিদে রয়েছে চারটি কারুকার্যময় মেহরাব। এ মসজিদের পাশে একটি মাজার শরিফ রয়েছে।
কুসুম্বা মসজিদ
নওগাঁর মান্দা উপজেলার কুসুম্বা গ্রামে অবস্থিত কুসুম্বা মসজিদ। এটি বাংলাদেশের একটি প্রাচীন স্থাপনা। ১৫৫৪ সালে নির্মিত মসজিদটির দৈর্ঘ্য ৫৮ ফুট, প্রস্থ ৪২ ফুট। কুসুম্বা মসজিদের ছাদে দুই সারিতে ছয়টি গম্বুজ রয়েছে। আফগানী শাসনামলে জনৈক সুলায়মান নামক এক ব্যক্তি এ মসজিদটি নির্মাণ করেন।
চাটমোহর শাহি মসজিদ
পাবনার চাটমোহর উপজেলায় অবস্থিত চাটমোহর শাহি মসজিদ। ১৫৮১ সালে মাসুম খাঁ কাবলি নামের সম্রাট আকবরের জনৈক সেনাপতি চাটমোহর শাহি মসজিদ নির্মাণ করেন। একসময় এ মসজিদ প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ প্রতœতত্ত্ব অধিদফতর এটিকে পুনঃনির্মাণ করে।
হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদ
চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে অবস্থিত শৈল্পিক কারুকার্যময় হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদটি আয়তনের দিক দিয়ে উপমহাদেশের বড় মসজিদগুলোর অন্যতম। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে হাজী আহমদ আলী পাটোয়ারী হাজীগঞ্জ ঐতিহাসিক বড় মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এর আয়তন ২৮ হাজার ৪০০ বর্গফুট।
আতিয়া মসজিদ
টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলায় অবস্থিত আতিয়া বা আটিয়া মসজিদ। এ মসজিদের প্রধান কক্ষের ওপর একটি এবং বারান্দার ওপর ছোট তিনটি গম্বুজ রয়েছে। জানা যায়, আফগানের সাঈদ খান পন্নি ১৬০৯ সালে মসজিদটি নির্মাণ করেন। ২২৮ বছর পর অর্থাৎ ১৮৭৩ সালে মসজিদটি ঝুঁকিপূর্ণ হলে সংস্কার করা হয়। শেষ সংস্কার করা হয় ১৯০৯ সালে।
ফুলচৌকি মসজিদ
রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার ফুলচৌকি গ্রামে মসজিদটির অবস্থান। গ্রামের নামেই এর নামকরণ করা হয়েছে। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এ মসজিদটির কোনো সংস্কার করার প্রয়োজন পড়ে নি। এর দৃষ্টিনন্দন কারুকাজ এখনও আগের মতোই সুন্দর। মসজিদের প্রবেশদ্বারে একটি ফুলবাগান ছিল। বর্তমানে স্থানীয়রা সে জায়গাটি কবরস্থান হিসেবে ব্যবহার করছে।
লক্ষ্য করার মতো বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এবং ইসলামি সংস্কৃতির পরিচয় জানান দেয়া এসব মসজিদের অবস্থান, ইতিহাস, শিলালিপি, গবেষণা, স্থাপত্যশৈলী, গ্যালারি, তথ্যসূত্র বহিঃসংযোগ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নানা ধরনের ঐতিহাসিক ঘটনা, মুসলিম শাসকদের শাসনামলের গৌরব উঠে আসে সহজেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদের কথা। সুপ্রাচীন এই মসজিদটি রংপুর-কুড়িগ্রাম মহাসড়কের ১ কিলোমিটার দক্ষিণে লালমনিরহাট সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাস মৌজায় অবস্থিত। লালমনিরহাটের পঞ্চগ্রাম ইউনয়নের রামদাস মৌজায় বহুদিন ধরে একটি পতিত জঙ্গল ছিল। জঙ্গলের নাম ছিল মজদের আড়া। স্থানীয় ভাষায় আড়া শব্দের মানে জঙ্গলময় স্থান। জঙ্গল পরিষ্কার করার সময় প্রাচীনকালের কিছু ইট বেরিয়ে আসে। এমনিভাবে মাটি ও ইট সরাতে গিয়ে একটি মসজিদের ভিত খুঁজে পাওয়া যায়। এখানের একটি প্রচিীন শিলালিপির পাঠ থেকে মসজিদের প্রতিষ্ঠাকাল ৬৯ হিজরি জানা গেছে। মসজিদের ধ্বংসস্তূপের ভিতরে একটি শিলালিপি পাওয়া যায়। লিপিটিতে আরবি ভাষায় স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে ‘লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, হিজরি সন ৬৯’। লিপিটি থেকে বোঝা যায় যে, মসজিদটি প্রায় ৬৯০ খ্রিস্টাব্দের দিকে নির্মিত হয়েছিল। শিলালিপিটি বর্তমানে রংপুরের তাজহাট জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।
১৯৮৭ সালের প্রথমভাগে স্থানীয়রা সাংবাদিক ও গবেষকদের কাছে হারানো মসজিদ সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন শতাধিক গবেষক, প্রতœতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদ এখানে গবেষণা করতে ছুটে আসেন। প্রথাগত ইতিহাস অনুযায়ী ১০০০ শতকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে সুফিদের প্রথম আগমন ঘটে। ১১০০ থেকে ১২০০ শতকে সুফিদের মাধ্যমে পূর্ববাংলায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার শুরু হয় এবং তাঁদের হাতেই এই অঞ্চলে প্রথম মসজিদ নির্মাণ হয়। তাই এত আগে এখানে মসজিদ নির্মাণের বিষয়টি আশ্চর্যজনক। গবেষক টিম স্টিল তখন আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ আর্কিওলজিস্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সেখানকার ইসলামের ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষকগণ বলেন অনেক রোমান ও জার্মান ইতিহাসবিদের লেখায় আরব ও রোমান বণিকদের ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় নৌ-বাণিজ্যের সূত্রে আসা-যাওয়ার কথা জানা যায়। এছাড়া বেশ কয়েকটি চলমান গবেষণায় ব্রহ্মপুত্র-তিস্তা অববাহিকাকে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নৌপথ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার প্রমাণও পাওয়া গেছে। টিম স্টিল পঞ্চগড়ের ভিটাগড়ে প্রাচীন নগরের নিদর্শন পাওয়া প্রতœতাত্ত্বিক অধ্যাপক শাহনেওয়াজের গবেষণা থেকেও সহায়তা পান। তিনি মনে করেন মসজিদটি নির্মাণের ইতিহাস খুঁজে পেলে হয়তো বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ইতিহাসের সঙ্গে বিশ্ব সভ্যতার সম্পর্কের আরেক ইতিহাস জানার পথ উন্মোচিত হবে। মসজিদটি ২১ ফুট চওড়া এবং ১০ ফুট লম্বা ছিল। এর চারটি স্তম্ভ ছিল, যার দুটি সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত।
বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাকে মসজিদের শহর বলা হলেও ঐতিহাসিক মসজিদের শহর বলা হয় বাগেরহাটকে। ১৯৮৫ সালে বাগেরহাটকে ঐতিহাসিক মসজিদের শহর হিসেবে ঘোষণা করে ৩২১তম বিশ্ব-ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করে ইউনেস্কো। এর মধ্যে বাগেরহাটের ১৭টি স্থাপনাকে তালিকাভুক্ত করা হয়, যার ১০টিই মসজিদ। মসজিদগুলো হল বিশ্ব-ঐতিহ্য ষাট গম্বুজ মসজিদ, বিবি বেগুনি মসজিদ, চুনাখোলা মসজিদ, নয় গম্বুজ মসজিদ, জিন্দা পীরের মসজিদ, দশ গম্বুজ মসজিদ, রন বিজয়পুর মসজিদ, রেজা খোদা মসজিদ, সিংগাইর মসজিদ ও এক গম্বুজ মসজিদ। মসজিদগুলো বাগেরহাট শহরের আশপাশ জুড়ে রয়েছে। এছাড়াও খানজাহান আলী (রহ.)-এর কবর, পীর আলী তাহেরের কবর, জিন্দা পীরের কবর, সাবেক ডাঙ্গা প্রার্থনা কক্ষ, খানজাহান আলী (রহ)-এর বসতভিটা, বড় আদিনা ডিবি, খানজাহানের তৈরি প্রাচীন রাস্তাকেও বিশ্ব-ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করা হয়।
চুনাখোলা মসজিদ
ষাট গম্বুজ মসজিদ থেকে প্রায় এক কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এবং বিবি বেগুনি মসজিদের উত্তরে বাগেরহাট সদর উপজেলার ষাট গম্বুজ ইউনিয়নের চুনোখোলা গ্রামে মাঠের মধ্যে এ মসজিদটির অবস্থান। ১৯৮৩ সালে ইউনেস্কো ঐতিহাসিক ষাট গম্বুজ মসজিদসহ তৎকালীন ‘খলিফাবাদ’ নগর রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ‘খান-উল-আযম উলুঘ খান-ই-জাহান’ নির্মিত প্রাচীন নগরীর অংশ হিসেবে এই মসজিদটিকে ‘বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য’ হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। এর আগে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সরকার চুনাখোলা মসজিদকে ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণা করে এবং প্রতœতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতায় সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়।
চুনাখোলা মসজিদের বাইরের অংশ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪০ ফুট এবং প্রস্থে ২৫ ফুট। পূর্বদিকে ১টি বড় (প্রধান) দরজাসহ মোট ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ১টি করে মোট ২টি দরজা রয়েছে। পূর্বদিকের বড় দরজাটির উচ্চতা ৯ ফুট, প্রস্থ ৪ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং ছোট ২টি দরজার উচ্চতা ৭ ফুট এবং প্রস্থ ৩ ফুট। উত্তর-দক্ষিণ দিকের দরজা ২টির উচ্চতা ৯ ফুটের বেশি এবং প্রস্থ ৫ ফুট করে। মসজিদের মধ্যে ১টি কেন্দ্রীয় মেহরাব ও ২টি ছোট মেহরাব রয়েছে। বড়টির উচ্চতা ৭ ফুট ও প্রস্থ ৪ ফুট। ছোট মেহরাব ২টির উচ্চতা ৪ ফুট প্রায় এবং প্রস্থ ৩ ফুট। মসজিদের দেওয়ালের পুরুত্ব ৭ ফুট ৮ ইঞ্চি এবং বাইরের চার কোণের চারটি খান জাহানি-রীতি অনুযায়ী গোলাকার ইটের খাম্বা বা পিলার রয়েছে। মসজিদে স্থানীয়রা নিয়মিত নামাজ আদায় করে। লোকালয় থেকে মসজিদে যাওয়ার জন্য একটি ইটের সড়ক করা হয়েছে।
নয় গম্বুজ মসজিদ
ঠাকুর দিঘী বা খাঞ্জেলী দিঘীর পশ্চিম পাড়ে ১৬.৪৫ মি. থেকে ১৬.১৫ মি. ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত নয় গম্বুজ মসজিদটি অবস্থিত। এর দেয়ালগুলো ২.৫৯ মি. পুরো। মসজিদের ছাদ ৯টি নিচু অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে তিনটি করে প্রবেশ পথ এবং পশ্চিম দেয়ালে পোড়া-মাটির ফুল ও লতা পাতায় অলংকৃত তিনটি মেহরাব রয়েছে। মসজিদের মত এ মসজিদের কেন্দ্রীয় মেহরাবটিও অপেক্ষাকৃত বড়। মসজিদের কার্নিশ সামান্য বক্র। মসজিদের ভেতরের একটি পিলারে বড় আকারের তেলতেলে গর্ত রয়েছে। জনশ্রুতি রয়েছে কোন এক পীর আঙ্গুলের খোঁচায় ওই গর্ত করেছিলেন। মসজিদের কার্নিশ সামান্য বক্র। এ মসজিদে এখনও নিয়মিত নামাজ পড়েন স্থানীয়রা।
জিন্দা পীরের মসজিদ
বর্গাকারে নির্মিত এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি ষাটগম্বুজ মসজিদ থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে সদর উপজেলার সুন্দরঘোনা গ্রামে অবস্থিত। জিন্দাপীর মাজার কমপেস্নক্সের উত্তর-পশ্চিম কোনে মধ্যযুগীয় এই মসজিদটি অবসিহত। মসজিদটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় (৬মি.-৬মি.) নির্মিত এটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। মসজিদের চারপাশের চারটি গোলাকার বুরুজ রয়েছে। মসজিদের দেয়ালগুলো গড়ে ১.৫২ মি. পুরু। পূর্ব বাহুতে ৩টি, উত্তর ও দক্ষিণ বাহুতে একটি করে খিলান দরজা আছে। সামনের বাহুতে আছে তিনটি মিহরাব। ছাদের অর্ধগোলাকার গম্বুজটি ভাঙ্গা অবস্থায় ছিল। ২০০২ সালে এটিকে প্রতœতাত্ত্বিক সংস্কারের মাধ্যমে পূর্ণ অবয়ব প্রদান করা হয়েছে।
ষাট গম্বুজ মসজিদ থেকে পূর্বে রনবিজয়পুর গ্রামে অবস্থিত এ মসজিদটিতে দশটি গম্বুজ রয়েছে। খানজাহান আমলের মসজিদ বলে জনশ্রুতি থাকলেও ইতিহাসবিদরা এটিকে খানজাহান পরবর্তী হোসেন শাহ-ই আমলের মসজিদ বলে উল্লেখ করেছেন। ৫০.৫ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১৮.১০ ফুট প্রস্থ মসজিদটিতে এখন আর আগের অবয়ব নেই। সংস্কার ও সম্প্রসারণের ফলে মসজিদটি তার নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়েছে। মসজিদের সামনে একটি বারান্দা ও উত্তর পাশে কবর স্থান রয়েছে। সড়ক থেকে মসিজিদে ঢোকার জন্য একটি সু-সজ্জিত গেট করা হয়েছে। মূল মসজিদের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ পাশে দু’টি করে প্রবেশদ্বার রয়েছে। দক্ষিন-পশ্চিম কোনে ছাদে ওঠার জন্য একটি সিঁড়ি রয়েছে। এ মসজিদে বর্তমানে স্থানীয় লোকজন নামাজ আদায় করেন। মসজিদের বিপরীত দিকে মসজিদের নামে একটি হাফেজিয়া মাদরাসা রয়েছে।
এছাড়া ষাট গম্বুজ মসজিদের দেড় কিলোমিটার পূর্ব দিকে রণবিজয়পুর গ্রামে এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকার (১৮.৪৯/১৮.৪৯মি.) মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদটি বাংলাদেশে প্রাচীন আমলে নির্মিত এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের মধ্যে সর্ববৃহৎ। মসজিদের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে তিনটি করে প্রবেশ পথ এবং পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মেহরাব রয়েছে। মসজিদটিতে স্থানীয় লোকজন নামাজ আদায় করে এখনও।
রেজা খোদা মসজিদ
বাগেরহাট শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার ও ষাটগম্বুজ থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে সুন্দরঘোনা গ্রামে অবস্থিত ঐতিহাসিক রেজাখোদা মসজিদ। বর্তমানে মসজিদটির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। ধারণা করা হয়, এটি ছয় গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ ছিল। বর্তমানে শুধু দেয়ালের কিছু কিছু অংশ ও খিলানযুক্ত মিহরাবের অংশ বিশেষ টিকে আছে। প্রায় অর্ধশত বছর আগে স্থানীয় লোকজন মসজিদের ওই জায়গায় নতুন করে একটি টিনশেড মসজিদ নির্মাণ করে। সেখানে এখন নামাজ আদায় করে স্থানীরা।
খান-জাহান-আলী (রহ.)-এর মাজারের পশ্চিম পাশে এবং ঠাকুর দিঘীর পূর্ব পাড়েই এ মসজিদটি অবস্থিত। সংস্কার ও সম্প্রসারণের ফলে এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের মূল অবয়ব এখন বোঝা যায় না। এখানে মসজিদের খাদেম ও দিঘীর আশপাশের লোকজন নামাজ পড়ে। খানজাহানের ভক্তবৃন্দ মাজার জিয়ারতের পরে এখানে নামাজ আদায় করেন।
বাংলাদেশে মসজিদের সংখ্যা দুই লাখ ৫০ হাজার ৩৯৯টি। ঐতিহাসিক ছাড়াও বাংলাদেশের দৃষ্টিনন্দন কয়েকটি মসজিদের মধ্যে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম অন্যতম। ১৯৫৯ সালে বায়তুল মোকাররম মসজিদ সোসাইটি গঠনের মাধ্যমে ঢাকায় একটি উচ্চ ধারণক্ষমতাসম্পন্ন মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেন তৎকালীন বিশিষ্ট শিল্পপতি লতিফ বাওয়ানি ও তাঁর ভাতিজা ইয়াহিয়া বাওয়ানি। পুরান ঢাকা ও নতুন ঢাকার মিলনস্থলে মসজিদটির জন্য ৮.৩০ একর জায়গা অধিগ্রহণ করা হয়।
স্থানটি নগরীর প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র থেকেও ছিল নিকটবর্তী। সেই সময় মসজিদের অবস্থানে একটি বড় পুকুর ছিল, যা পল্টন পুকুর নামে পরিচিত ছিল। পুকুরটি ভরাট করে ১৯৬০ সালের ২৭ জানুয়ারি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান মসজিদের কাজের উদ্বোধন করেন। পুরো মসজিদ কমপ্লেক্সটির নকশা করেন সিন্ধুর বিশিষ্ট স্থপতি আব্দুল হুসেন থারিয়ানি। নকশায় স্থান পায় দোকান, অফিস, গ্রন্থাগার, কার পার্কিংয়ের ব্যবস্থাসহ নানা সুবিধা। মসজিদটির প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৩ সালের ২৫ জানুয়ারি, শুক্রবার। অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন ও মনোমুগ্ধকর এই মসজিদে একসঙ্গে ৩০ হাজার মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারে। ধারণক্ষমতার দিক দিয়ে এটি বিশ্বের দশম বৃহত্তম মসজিদ।
১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এই মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে। বর্তমানে বায়তুল মোকাররম মসজিদটি আটতলা। নিচতলায় রয়েছে বিপণিবিতান ও অত্যাধুনিক সুসজ্জিত একটি বৃহৎ মার্কেট কমপ্লেক্স। দোতলা থেকে ছয়তলা পর্যন্ত প্রতি তলায় নামাজ পড়া হয়। মসজিদের অভ্যন্তরে রয়েছে অজুর ব্যবস্থাসহ মহিলাদের জন্য পৃথক নামাজকক্ষ ও পাঠাগার।
২০০৮ সালে সৌদি সরকারের অর্থায়নে মসজিদটি সম্প্রসারণ করা হয়। বর্তমানে এই মসজিদে একসঙ্গে ৪০ হাজার মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারে। এই মসজিদের শোভাবর্ধন ও উন্নয়নের কাজ এখনো অব্যাহত।
ধনবাড়ী শাহি মসজিদ
ইসলামি ঐতিহ্য ও কালের সাক্ষী হয়ে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন স্থাপত্যশিল্পের ধারক ও বাহক টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী নওয়াব শাহি জামে মসজিদ। এটি টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলার প্রাণকেন্দ্র পৌরসভায় অবস্থিত। মসজিদটির প্রথম খ- নির্মাণ করেন তুর্কি বংশোদ্ভূত ইসপিঞ্জার খাঁ ও মনোয়ার খাঁ নামের দুই সহোদর। পরবর্তী সময়ে মসজিদটির সম্প্রসারণকাজ করেন বাংলা ভাষার প্রথম প্রস্তাবক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, যুক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী, ধনবাড়ীর বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। আজ থেকে ১১৫ বছর আগে মসজিদটির সম্প্রসারণের মাধ্যমে আধুনিক রূপ দেন তিনি। প্রায় ১০ কাঠা জমির ওপর বানানো এই মসজিদ সংস্কারের আগে ছিল আয়তাকার। তখন এর দৈর্ঘ্য ছিল ১৩.৭২ মিটার (৪৫ ফুট) এবং প্রস্থ ছিল ৪.৫৭ মিটার (১৫ ফুট)।
বর্তমানে এটি একটি বর্গাকৃতির মসজিদ এবং সাধারণ তিন গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার মোগল মসজিদের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। সংস্কারের পর মসজিদের প্রাচীনত্ব কিছুটা লোপ পেলেও এর চাকচিক্য ও সৌন্দর্য অনেক বেড়েছে। দৃষ্টিনন্দন এই মসজিদের ভেতরের দেয়ালে ব্যবহার করা হয়েছে কড়িপাথরের লতা-পাতা আঁকা অসংখ্য রঙিন নকশা ও কড়িপাথরের মোজাইক, যা প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন বহন করছে। বাইরের দেয়ালে ব্যবহার করা হয়েছে সিমেন্ট আর কড়িপাথরের টেরাকোটা নকশা।
মসজিদে প্রবেশ করার জন্য বানানো হয়েছে পাঁচটি প্রবেশপথ। পূর্ব দিকে বহু খাঁজবিশিষ্ট খিলানযুক্ত তিনটি আর উত্তর ও দক্ষিণে আরো একটি করে দুটি সর্বমোট পাঁচটি। ৩৪টি ছোট ও বড় গম্বুজ মসজিদটিকে করেছে আরো নান্দনিক। আরো আছে ১০টি বড় মিনার। প্রতিটির উচ্চতা ছাদ থেকে প্রায় ৩০ ফুট। মসজিদের দোতলার মিনারটির উচ্চতা প্রায় ১৫ ফুট। মিনারের ওপর লাগানো তামার চাঁদগুলো মসজিদের সৌন্দর্য আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।
মসজিদের ভেতরটা অলংকৃত করেছে মুঘল আমলের তিনটি ঝাড়বাতি। শোভা পাচ্ছে সংরক্ষিত ১৮টি হাঁড়িবাতি, যা নারকেল ব্যবহার করে জ্বালানো হতো। সুপ্রাচীন মসজিদটিতে একসঙ্গে ২০০ মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারে।
মসজিদের পাশেই রয়েছে শান-বাঁধানো ঘাট ও কবরস্থান। এখানে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন নবাব বাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। ১৯২৯ সালের ১৭ এপ্রিল তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর দুই বছর আগে তিনি এই মসজিদে চালু করেন ২৪ ঘণ্টা কোরআন তিলাওয়াতের ব্যবস্থা (নামাজের সময় বাদে), যা গত প্রায় এক শ বছরে এক দিনের জন্যও বন্ধ হয়নি। নিরবচ্ছিন্ন তিলাওয়াত সচল রাখতে নিয়োজিত আছেন পাঁচজন হাফেজ, যা প্রতিদিন মসজিদে আসা মুসল্লি ও দর্শনার্থীদের অভিভূত করে। এককথায় প্রাচীন আমলের মানুষের ইবাদত-বন্দেগি ও ইসলামি ঐতিহ্যের স্মৃতিচিহ্ন ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে ধনবাড়ী শাহি মসজিদ।
ষাট গম্বুজ মসজিদ
খুলনা বিভাগের বাগেরহাট জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ। মসজিদটির গায়ে কোনো শিলালিপি না থাকায় এর নির্মাণকারী সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে মসজিদটির স্থাপত্যশৈলী দেখলে এটি যে খান-ই-জাহান নির্মাণ করেছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। ধারণা করা হয়, তিনি ১৫০০ শতাব্দীতে এটি নির্মাণ করেন। মসজিদটি বহু বছর ধরে বহু অর্থ খরচ করে নির্মাণ করা হয়েছিল। পাথরগুলো আনা হয়েছিল রাজমহল থেকে।
মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে বাইরের দিকে প্রায় ১৬০ ফুট, ভেতরের দিকে প্রায় ১৪৩ ফুট লম্বা এবং পূর্ব-পশ্চিমে বাইরের দিকে প্রায় ১০৪ ফুট, ভেতরের দিকে প্রায় ৮৮ ফুট চওড়া। দেয়ালগুলো প্রায় ৮.৫ ফুট পুরু। সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহর (১৪৩৫-৫৯) আমলে খান আল-আজম উলুগ খান-ই-জাহান সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে খলিফাবাদ রাজ্য গড়ে তোলেন। খান-ই-জাহান বৈঠক করার জন্য একটি দরবার হল গড়ে তোলেন, যা পরে ষাটগম্বুজ মসজিদ হয়। তুঘলকি ও জৌনপুরি নির্মাণশৈলী এতে সুস্পষ্ট।
মসজিদটির পূর্ব দেয়ালে ১১টি বিশাল আকারের খিলানযুক্ত দরজা আছে। মাঝের দরজাটি অন্যগুলোর চেয়ে বড়। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আছে সাতটি করে দরজা। মসজিদের চার কোণে চারটি মিনার আছে। এগুলোর নকশা গোলাকার এবং ওপরের দিকে সরু হয়ে গেছে। এদের কার্নিসের কাছে বলয়াকার ব্যান্ড এবং চূড়ায় গোলাকার গম্বুজ আছে। মিনারগুলোর উচ্চতা ছাদের কার্নিসের চেয়ে বেশি। সামনের দুটি মিনারে পেঁচানো সিঁড়ি আছে এবং এখান থেকে আজান দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এর একটির নাম রওশন কোঠা, অন্যটির নাম আন্ধার কোঠা। মসজিদের ভেতরে ৬০টি স্তম্ভ বা পিলার আছে। এগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণে ছয় সারিতে অবস্থিত এবং প্রতি সারিতে ১০টি স্তম্ভ আছে। প্রতিটি স্তম্ভই পাথর কেটে বানানো, শুধু পাঁচটি স্তম্ভ বাইরে থেকে ইট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এই ৬০টি স্তম্ভ এবং চারপাশের দেয়ালের ওপর তৈরি করা হয়েছে গম্বুজ। মসজিদটির নাম ষাটগম্বুজ মসজিদ হলেও এখানে গম্বুজ মোটেও ৬০টি নয়, গম্বুজ ১১টি সারিতে মোট ৭৭টি। পূর্ব দেয়ালের মাঝের দরজা ও পশ্চিম দেয়ালের মাঝের মেহরাবের মধ্যবর্তী সারিতে যে সাতটি গম্বুজ, সেগুলো দেখতে অনেকটা বাংলাদেশের চৌচালা ঘরের চালের মতো। বাকি ৭০টি গম্বুজ অর্ধগোলাকার।
মসজিদের ভেতরে পশ্চিম দেয়ালে ১০টি মেহরাব আছে। মাঝের মেহরাবটি আকারে বড় এবং কারুকার্যম-িত। এই মেহরাবের দক্ষিণে পাঁচটি এবং উত্তরে চারটি মেহরাব আছে। শুধু মাঝের মেহরাবের ঠিক পরের জায়গাটিতে উত্তর পাশে যেখানে একটি মেহরাব থাকার কথা, সেখানে আছে একটি ছোট দরজা। কারো কারো মতে, খান-ই-জাহান এই মসজিদটি নামাজের কাজ ছাড়াও দরবারঘর হিসেবে ব্যবহার করতেন, আর এই দরজাটি ছিল দরবারঘরের প্রবেশপথ। আবার কেউ কেউ বলেন, মসজিদটি মাদরাসা হিসেবেও ব্যবহৃত হতো।
বজরা শাহি মসজিদ
মুঘল স্থাপত্যশৈলীর উজ্জ্বল নিদর্শন বজরা শাহি মসজিদ, যা নোয়াখালী জেলার প্রাণকেন্দ্র মাইজদী থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার উত্তরে সোনাইমুড়ী উপজেলার বজরা নামক স্থানে অবস্থিত। প্রায় তিন শ বছর আগে, ১৭৪১ সালে মোগল জমিদার আমান উল্লাহ খান দিল্লির বিখ্যাত জামে মসজিদের আদলে এই মসজিদ নির্মাণ করেন, যা আজও মোগল স্থাপত্যশিল্পের এক অনন্য নিদর্শন হিসেবে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে। জমিদার আমান উল্লাহ তাঁর বাড়ির সামনে ৩০ একর জমির ওপর উঁচু পারযুক্ত একটি বিশাল দিঘি খনন করেছিলেন। সেই দিঘীর পশ্চিম পারেই নির্মাণ করা হয়েছিল আকর্ষণীয় তোরণবিশিষ্ট ঐতিহাসিক এই মসজিদ। প্রায় ১১৬ ফুট দৈর্ঘ্য, ৭৪ ফুট প্রস্থ ও ২০ ফুট উচ্চতার তিন গম্বুজবিশিষ্ট এই মসজিদ যে কাউকে মুগ্ধ করবে।
মসজিদকে মজবুত করার জন্য মাটির প্রায় ২০ ফুট নিচ থেকে ভিত তৈরি করা হয়েছিল। দৃষ্টিনন্দন মার্বেল পাথরে অলংকৃত করা হয়েছিল গম্বুজগুলো। মসজিদে প্রবেশের জন্য রয়েছে তিনটি ধনুকাকৃতি দরজা। প্রবেশপথের ওপরই রয়েছে কয়েকটি গম্বুজ। পশ্চিমের দেয়ালে আছে কারুকার্যখচিত তিনটি মেহরাব।
মুঘল সম্রাট মোহাম্মদ শাহর বিশেষ অনুরোধে মক্কা শরিফের বাসিন্দা, তৎকালীন অন্যতম বুজুর্গ আলেম হজরত মাওলানা শাহ আবু সিদ্দিকী ঐতিহাসিক এই মসজিদের প্রথম ইমাম হিসেবে নিয়োজিত হন। তাঁর বংশধররা যোগ্যতা অনুসারে আজও এই মসজিদের ইমামের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বর্তমানে প্রথম ইমাম সাহেবের সপ্তম পুরুষ ইমাম হাসান সিদ্দিকী ওই মসজিদের ইমামের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। প্রতিদিন দূর-দূরান্ত থেকে আসা বহু মানুষ এই মসজিদে নামাজ আদায় করে। বাংলাদেশ প্রতœতত্ত্ব বিভাগ ঐতিহাসিক মসজিদটির ঐতিহ্য রক্ষার্থে এবং দুর্লভ নিদর্শন সংরক্ষণের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
আজগর আলী চৌধুরী জামে মসজিদ
চট্টগ্রামের বাণিজ্যিক এলাকা আগ্রাবাদ থেকে সোজা পশ্চিমে তিন কিলোমিটার গেলেই হালিশহরের বড়পোল এলাকা। সেখান থেকে আরো প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পশ্চিম-উত্তরে এগোলেই হালিশহরের চৌধুরীপাড়া। ১৭৯৫ সালে এখানেই নির্মাণ করা হয় মোগল স্থাপত্য নকশায় চুন-সুরকির দৃষ্টিনন্দন আজগর আলী চৌধুরী জামে মসজিদ। মসজিদটি নির্মাণ করেন হালিশহরের সম্ভ্রান্ত চৌধুরী পরিবারের প্রয়াত আজগর আলী চৌধুরী। ১০ শতক জায়গায় তৈরি মসজিদটির সামনে আছে বিশাল এক পুকুর, যা প্রায় ১০০ শতক জায়গাজুড়ে। মসজিদের দক্ষিণে ২০ শতক জায়গায় আছে কবরস্থান। উত্তরে ২৬ শতক জায়গার ওপর আছে চৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত উত্তর হালিশহর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
প্রায় আড়াই শ’ বছর আগে মসজিদটি তৈরি করা হয়েছিল তাজমহলের আদলে। মসজিদের ছাদে শোভা পেয়েছে বড় তিনটি গম্বুজ ও ২৪টি মিনার। পোড়ামাটির রঙের এই মসজিদের চারপাশ সাজানো হয়েছে নানা রকম নকশা দিয়ে। শুধু বাইরের দেয়ালই নয়, ভেতরের দেয়াল ও কাঠামোজুড়ে মোগল স্মৃতিচিহ্ন প্রদর্শন করে যাচ্ছে চোখ-ধাঁধানো নানা রকম নকশা। মজার ব্যাপার হলো, এই মসজিদে প্রচলিত কোনো জানালা নেই। মসজিদটি দেখতে দেশি-বিদেশি অনেক পর্যটক প্রতিদিন এখানে ভিড় জমায়।
এলাকাবাসীর আগ্রহে পুরাতাত্ত্বিক এই নির্দশন না ভেঙে পেছনে ৭০ শতক জায়গার ওপর সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন মসজিদটি নির্মাণ করছেন চৌধুরী পরিবারের ওয়ারিশরা। নতুন মসজিদের নকশাও নজর কাড়ছে দর্শনার্থীদের। নতুন মসজিদটি বানানো হয়েছে অনেকটা সংসদ ভবনের আদলে। মসজিদটির তিন পাশেই রাখা হয়েছে জলাধার। ওপর থেকে মনে হবে পানির ওপরই ভেসে আছে যেন আল্লাহর এই প্রিয় ঘর।
তারা মসজিদ
সাদা মার্বেলের গম্বুজের ওপর নীলরঙা তারায় খচিত ঐতিহাসিক তারা মসজিদ। পুরান ঢাকার আরমানিটোলায় আবুল খয়রাত সড়কে অবস্থিত এটি, যা তৎকালে মহল্লা আলে আবু সাঈয়ীদ নামে পরিচিত ছিল। মসজিদটি নির্মিত হয় আঠারো শতকের প্রথম দিকে; যদিও মসজিদের গায়ে কোনো ধরনের নির্মাণ তারিখ খোদাই করা নেই। মসজিদটির পূর্ব নাম মির্জা সাহেবের মসজিদ। জানা যায়, আঠারো শতকে ঢাকার মহল্লা আলে আবু সাঈয়ীদ (পরে যার নাম আরমানিটোলা হয়) আসেন ঢাকার ধনাঢ্য ব্যক্তি মীর আবু সাঈয়ীদের নাতি জমিদার মির্জা গোলাম পীর (মির্জা আহমদ জান)। তিনিই এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। সেকালে মির্জা সাহেবের মসজিদ হিসেবে এটি বেশ পরিচিতি পায়। ১৮৬০ সালে মারা যান মসজিদের মূল নির্মাণকারী মির্জা গোলাম পীর।
পরে ১৯২৬ সালে ঢাকার তৎকালীন স্থানীয় ব্যবসায়ী আলী জান বেপারী মসজিদটির সংস্কার করেন। সে সময় মসজিদের সৌন্দর্য বর্ধনে এর কারুকার্যে ব্যবহার করা হয় জাপানের রঙিন চিনি-টিকরি পদার্থ। মনোমুগ্ধকর কারুকার্যখচিত মসজিদটিতে মোগল স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব পাওয়া যায়। জমিদার মির্জা গোলামের আমলে মসজিদটি ছিল তিন গম্বুজবিশিষ্ট। মসজিদের দৈর্ঘ্য ছিল ৩৩ ফুট (১০.০৬ মিটার) আর প্রস্থ ছিল ১২ ফুট (৪.০৪ মিটার)।
পরবর্তী সময়ে ১৯২৬ সালে আলী জানের সংস্কারের সময় মসজিদের পূর্ব দিকে একটি বারান্দা বাড়ানো হয়। ১৯৮৭ সালে তিন গম্বুজ থেকে পাঁচ গম্বুজ করা হয়। পুরনো একটি মেহরাব ভেঙে দুটি গম্বুজ আর তিনটি নতুন মেহরাব বানানো হয়। বর্তমানে মসজিদের দৈর্ঘ্য ৭০ ফুট (২১.৩৪ মিটার) এবং প্রস্থ ২৬ ফুট (৭.৯৮ মিটার)।