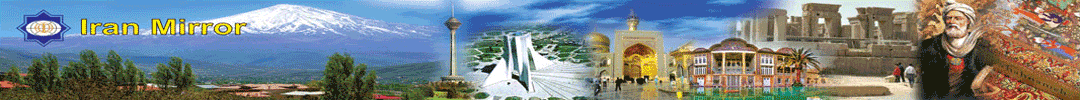নজরুল কাব্যে ফারসি সাহিত্য ও সুফিবাদের প্রভাব
পোস্ট হয়েছে: আগস্ট ২৭, ২০২০

মুজতাহিদ ফারুকী
কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে এক কালজয়ী প্রতিভা। বাংলাদেশের জাতীয় কবি বিশেষ করে কবিতা ও গানে স্বকীয় মহিমায় ভাস্বর। তিনি এমন এক সময় বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন যখন মধ্যগগণে উজ্জ্বল রবির মতই প্রখর আলো ছড়াচ্ছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সর্বগ্রাসী রবীন্দ্রপ্রভাববলয়ের বাইরে গিয়ে নজরুল সম্পূর্ণ নতুন এক কাব্যধারা ও সঙ্গীতরসসুধায় বাঙালির মনপ্রাণ ভরিয়ে দেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি অমর হয়ে থাকবেন তাঁর মানবতাবাদী বৈপ্লবিক চেতনাসমৃদ্ধ কাব্য এবং প্রেম ও ইসলামী গানের অপূর্ব সমৃদ্ধ বাণী ও সুরের অতুলনীয় সৃজনশীলতার জন্য।
নজরুল সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং বৈশ্বিক চিন্তা-চেতনার আলোয় অবগাহন করেছেন। আলোকিত হয়েছেন নিজ ভাষার সৃষ্টিসম্ভারের পাশাপাশি বিশ্বসাহিত্যের বর্ণচ্ছটায়। তাঁর রচনায় নিজ ধর্ম ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী, সুফিবাদী চিন্তাধারা যেমন মূর্ত হয়ে উঠেছে, তেমনই সমানভাবে উঠে এসেছে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের দর্শনও। তিনি ইসলামি সংগীত যেমন, তেমনই শ্যামা সংগীতও রচনা করেছেন। আবার প্রাচীন ফারসি সাহিত্য বিশেষ করে মহাকবি হাফিজ এবং ওমর খৈয়ামের রচনা তাঁকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে।
কাজী নজরুলের কবিতায় ফারসি সাহিত্যের এবং বিশেষ করে সুফিবাদের প্রভাব নজর এড়িয়ে যায় না। এ বিষয়ে বাংলায় বেশকিছু গবেষণানির্ভর আলোচনা হয়েছে। অনেক বিশিষ্ট গবেষক এ বিষয়ে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেগুলিও বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আমরা এখানে নজরুল সাহিত্যে ফারসি প্রভাব নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।
মহাকবি হাফিজের সঙ্গে নজরুলের কালগত ব্যবধান কয়েক শতাব্দীর। তবে উপমহাদেশে ফারসি ভাষা প্রচলনের সুবাদে হাফিজ তাঁর সমকালেই ভারতে তথা বাংলায় ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছিলেন। বাংলার শিক্ষিত প্রতিটি মানুষই ফারসি সাহিত্যের অমর কবি হিসেবে হাফিজকে জানতেন এবং তাঁর কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তবে আধুনিককালে হাফিজকে বাংলাভাষাভাষীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি হাফিজের কবিতার বাংলা তরজমা করেন।
হাফিজের কবিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে নজরুল নিজেই বলেন, ‘আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ইংরেজি ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙালি পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেব থাকতেন। একদিন তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শুনে আমি এমনই মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেইদিন থেকেই তাঁর কাছে ফার্সি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি। তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি।
তখন থেকেই আমার হাফিজের ‘দীওয়ান’ অনুবাদের ইচ্ছা হয়। কিন্তু তখনো কবিতা লিখবার মত যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি। এর বৎসর কয়েক পরে হাফিজের দীওয়ান অনুবাদ আরম্ভ করি। অবশ্য তাঁর রুবাইয়াৎ নয়- গজল। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছিলো।’
‘রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ’ নজরুল ইসলাম অনূদিত বাংলা ভাষায় বহুল প্রচারিত ও পঠিত একমাত্র সফল অনুবাদ কাব্য। শুধু হাফিজই নন, পারস্যের অন্যান্য কবির অমর কাব্যমহিমা দিয়েও নজরুল ইসলাম বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তারই আরেকটি অমর দৃষ্টান্ত হলো নজরুলের ‘রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম’ যা ওমর খৈয়ামের কবিতার তরজমা। কবি অসুস্থ হয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ার ১৬ বছর পর ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।
হাফিজ ও খৈয়াম এই দুই মহাকবির রচনাই নজরুলকে বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করে। তাঁদের মনন-মেধা, সুর-চেতনায় নজরুল এতটাই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর অনেক গজল-গানে, ধর্মীয় আধ্যাত্মিক সংগীতে তাঁদের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ‘নজরুল-গীতিকা’, ‘সুর-সাকী’, ‘জুলফিকার’, ‘বন-গীতি’, ‘গুল-বাগিচা’, ‘গীতি শতদল’ ও ‘গানের মালা’র অনেক কবিতা-গানে ফারসি সাহিত্যের প্রভাব লক্ষণীয়। ‘নজরুল গীতিকা’তে তো ‘ওমর খৈয়াম-গীতি’ ও ‘দীওয়ান-ই-হাফিজ-গীতি’ নামে আটটি করে কবিতা গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, ফারসি সাহিত্য তথা পারস্যের মহাকবি হাফিজ ও খৈয়ামের দ্বারা নজরুল কতটা অনুপ্রাণিত ছিলেন!
বহুমুখী প্রতিভার দৃষ্টান্ত দিতে বলা হলে বিশ্বসাহিত্য কিংবা ইতিহাসে যাঁদের নাম উপেক্ষা করা কঠিন ওমর খৈয়াম তাঁদের অন্যতম ও শীর্ষস্থানীয়। ফারসি কাব্য-জগতে ওমর খৈয়াম এক বিশেষ চিন্তাধারা ও বিশ্বদৃষ্টির পথিকৃৎ। তিনি জীবন এবং জগতের ও পারলৌকিক জীবনের রহস্য বা দর্শন সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। আল্লাহকে জানতে হলে আগে নিজেকে জানা প্রয়োজন এমন ইসলামি বর্ণনা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি লিখেছেন-
‘বিশ্ব-দেখা জামশেদিয়া পেয়ালা খুঁজি জীবন-ভর
ফিরনু বৃথাই সাগর গিরি কান্তার বন আকাশ-ক্রোড়।
জানলাম শেষে জিজ্ঞাসিয়া দরবেশ এক মুর্শিদে
জামশেদের এই জাম-বাটি এই আমার দেহ আত্মা মোর।’
মহান আল্লাহর দয়া সম্পর্কে খৈয়াম প্রার্থনাসূচক রুবাইয়ে লিখেছেন-
‘দয়া যদি কৃপা তব সত্য যদি তুমি দয়াবান
কেন তবে তব স্বর্গে পাপী কভু নাহি পায় স্থান?
পাপীদেরই দয়া করা সেই তো দয়ার পরিচয়
পুণ্যফলে দয়া লাভ সে তো ঠিক দয়া তব নয়।’
নজরুলের কাব্যেও একই ধরণের দর্শণ মূর্ত। স্রষ্টার উদ্দেশে তিনি বলছেন,
‘বিচার যদি করবে কেন রহমান নাম নিলে?
ঐ নামের গুণে তরে যাব কেন এ জ্ঞান দিলে?
রোজ হাশরে আল্লাহ আমার কোরো না বিচার।’
নজরুল ইসলামের ‘নতুন চাঁদ’ কাব্যে তাঁর সুফি তত্ত্বজ্ঞানের গভীর পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। ‘অভেদম্’ কবিতায় সুফি তত্ত্বের পরম পুরুষকে অনুসন্ধানের কথা বলা হয়েছে:
‘দেখিয়াছ সেই রূপের কুমারে, গড়িছে যে এই রূপ?
রূপে রূপে হয় রূপায়িত যিনি নিশ্চল নিশ্চুপ!
কেবলই রূপের আবরণে যিনি ঢাকিছেন নিজ কায়া
লুকাতে আপন মাধুরী যে জন কেবলি রচিছে মায়া!
সেই বহরূপী পরম একাকী এই সৃষ্টির মাঝে
নিষ্কাম হয়ে কিরূপে সতত রত অনন্ত কাজে।
পরম নিত্য হয়ে অনিত্য রূপ নিয়ে এই খেলা
বালুকার ঘর গড়িছে ভাঙিছে সকাল সন্ধ্যা বেলা।
আমরা সকলে খেলি তারই সাথে, তারই সাথে হাসি কাঁদি
তারই ইঙ্গিতে পরম ‘আমি’রে শত বন্ধনে বাঁধি।
মোরে ‘আমি’ ভেবে তারে স্বামী বলি দিবাযামী নামি উঠি,
কভু দেখি-আমি তুমি যে অভেদ, কভু প্রভু বলে ছুটি।’
প্রেমের লীলার মধ্য দিয়ে যেখানে পরম পিতা এবং মানুষ একীভূত হয়ে গেছে প্রেমের ব্যঞ্জনায়। তারই পরিচয় নজরুলের এই কবিতায়। ‘নতুন চাঁদ’-এর ‘আর কতদিন?’ কবিতায়ও সুফিতত্ত্বের গভীর ও প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটেছে। কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবক :
‘আমি ছিনু পথ-ভিখারিনী, তুমি কেন পথ ভুলাইলে,
মুসাফির-খানা ভুলায়ে আনিলে কোন্ এই মঞ্জিলে?
মঞ্জিলে এনে দেখাইলে কার অপরূপ তস্বির,
‘তসবি’তে জপি যত তার নাম তত ঝরে আঁখি-নীর!
‘তশবিহি’ রূপ এই যদি তার ‘তনিজহি’ কিবা হয়,
নামে যার এত মধু ঝরে, তার রূপ কত মধুময়।
কোটি তারকার কীলক রুদ্ধ অম্বর-দ্বার খুলে
মনে হয় তার স্বর্ণ-জ্যোতি দুলে ওঠে কুতূহলে।
ঘুম-নাহি-আসা নিঝ্ঝুম নিশি-পবনের নিঃশ্বাসে
ফিরদৌস-আলা হতে যেন লালা ফুলের সুরভি আসে।
চামেলী জুঁই-এর পাখায় কে যেন শিয়রে বাতাস করে,
শ্রান্তি ভুলাতে কী যেন পিয়ায় চম্পা-পেয়ালা ভরে।’
নজরুল ইসলামের রচনায় উপলব্ধির গভীরতা লক্ষ্যণীয়। তিনি আপন চৈতন্যে সুফি সাধনার মূল রসাবেশটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুফিরা বলে থাকেন, নিজেকে খুঁজতে গিয়ে এক পর্যায়ে তাঁরা মহাশক্তিকে স্পর্শ করেন। নজরুল বলছেন, এই পরম শক্তিই পৃথিবীতে প্রথম ঈদের চাঁদরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। কথাটি রূপক। কবি বলতে চাচ্ছেন, প্রকৃতির যে লীলা-বৈচিত্র্য এবং আকাশের নক্ষত্র এবং সূর্য যেগুলো আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে, সেগুলোর মধ্য দিয়ে বিধাতা আত্মপ্রকাশ করেন। ‘নতুন চাঁদ’-এর ‘কেন জাগাইলি তোরা’ কবিতায় কবি সে কথাই তুলে ধরেছেন :
‘মহা সমাধির দিকহারা লোকে জানি না কোথায় ছিনু
অমরা খুঁজিতে সহসা সে কোন শক্তিরে পরশিনু-
সেই সে পরম শক্তিরে লয়ে আসিবার ছিল সাধ-
যে শক্তি লভি এল দুনিয়ায় প্রথম ঈদের চাঁদ-
তারি মাঝে কেন ঢাকঢোল লয়ে এলি সমাধির পাশে
ভাঙাইলি ঘুম? চাঁদ যে এখনো ওঠেনি নীল আকাশে।’
নজরুল বিশ্বাস করতেন সুফিবাদের উদ্ভব হয়েছিল ইসলামের মহানবীর নবুওয়াত প্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গেই। একটি জনপ্রিয় গানে নজরুল বলেছেন :
‘হেরা হতে হেলেদুলে নূরানী তনু ও কে আসে হায়
সারা দুনিয়ার হেরেমের পর্দা খুলে খুলে যায়
সে যে আমার কামলিওয়ালা।’
যিনি হেরা পর্বতের গুহা থেকে হেলেদুলে নেমে আসছেন, অর্থাৎ ইসলামের নবী (স.)- একজন কামলিওয়ালা অর্থাৎ সুফি।
নজরুলের কবিতায় ফারসি সাহিত্যের প্রভাব প্রসঙ্গে নজরুল গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ লিখেছেন, ‘নজরুলের কবিতায় ফরাসি কবিতার প্রভাবের কথা বলতে গেলে প্রথমেই যে বিষয়টির উল্লেখ করতে হবে, সেটি ফারসি কবিতার কার্লাড ইমেজ বা রঙিন চিত্রকল্পের কথা। নজরুলের কবিতায় এই রঙিন চিত্রকল্পের রূপ দেখা যায়।’ যেমন-
“নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া!
আম্মা লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।” (মোহররম)
অথবা
“লাটে তোমার ভাস্বর টীকা
বস্রা গুলের বহ্নিতে লিখা;
এ যে বসোরার খুন-খারাবী গো রক্ত গোলাপ মঞ্জুরীর।” (শাত-ইল-আরব)
নজরুল এই রঙিন চিত্রকল্পের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন তাঁর গানে বা গীতিকবিতায়। হাফিজ বা ওমর খৈয়ামের চিত্রকল্পময় রুবাইয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই তা সহজে বোধগম্য হয়ে ওঠে।
কাজী নজরুল যেমন পারদর্শী ছিলেন দ্রোহ ও প্রেমের কবিতায় তেমনই সার্থক ছিলেন কবিতায় মরমী ভাবধারার সজীব উপস্থাপনে।