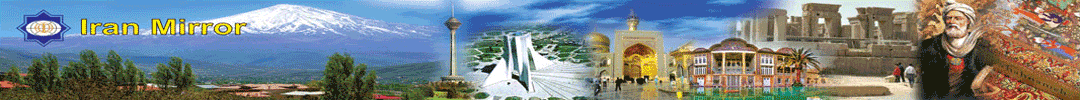খৈয়াম, রুবাইয়াত ও কাজী নজরুল ইসলাম
পোস্ট হয়েছে: আগস্ট ৩১, ২০১৬
ড. ফরহাদ দরুদগারিয়ান
গিয়াস উদ্দীন আবুল ফাতাহ উমর ইবনে ইবরাহীম খৈয়াম নিশাপুরী। তিনি ছিলেন একাধারে প্রাজ্ঞ মনীষী, গাণিতিক, জ্যোতির্বিদ ও বিখ্যাত ইরানি কবি। অধিকাংশ প্রাচীন সূত্রে তাঁর খ্যাতি হচ্ছে খৈয়ামী নামে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক সূত্রগুলোতে তিনি খৈয়াম নামেই প্রসিদ্ধ। অভিধানে খৈয়াম অর্থ তাঁবুনির্মাতা। জালাল উদ্দীন হুমায়ীর মতে খৈয়ামী নামের শেষে যে ‘য়ী’ প্রত্যয় রয়েছে তা দ্বারা বোঝা যায়, তিনি নিজে তাঁবুনির্মাতা ছিলেন না; বরং তিনি এমন কারো সাথে সম্বন্ধযুক্ত যিনি তাঁবুনির্মাতা ছিলেন। (জালাল উদ্দীন হুমায়ী, খৈয়ামনামে, পৃ. ২২১) বিভিন্ন সূত্রে তাঁকে তাঁর নামের সাথে ‘হুজ্জাতুল হক’ (আল্লাহর হুজ্জাত বা দলিল), ‘খাজায়ে ইমাম’ (মহামান্য ইমাম) ও ‘হাকীমে ফীলসুফ’ (দার্শনিক মনীষী) প্রভৃতি যোগে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (রেযাযাদে মালিক, দানেশনামেয়ে খৈয়াম, পৃ. ৪৩-৪৪)
উমর খৈয়ামের জন্মতারিখ সঠিক ভাবে জানা নেই। আবুল হাসান বায়হাকী বলেন, তাঁর জন্ম হয়েছে মিথুনরাশিতে। কয়েকটি সূত্রে যেমন (বায়হাকী, পৃ. ১১২), তীর্থ (ভারতীয় গবেষক, পৃ. ৩২-৩৪) খৈয়ামের জন্মদিন ১৮ মে ১০৪৮ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৩রা খোরদাদ ৪২৭ ইরানি বর্ষ এবং ৪৩৯ হিজরি সাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। খৈয়াম জন্মগ্রহণ করেন নিশাপুরে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, তাঁর পূর্বপুরুষরা সবাই ছিলেন এই শহরের আদি বাসিন্দা। বায়হাকীর বর্ণনা অনুযায়ী (পৃ. ৯৭) হাকীম আবুল হাসান আনবারীর কাছে ‘মাজিস্তী’ কিতাবটি অধ্যয়ন করেন। তিনি তখনকার হানাফী ফিকাহশাস্ত্রবিদ শেখ মুহাম্মাদ মানসুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ফিকাহশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। খৈয়াম নিজেই ‘রেসালা আল কাউন ওয়াত তাকলিফ’ গ্রন্থে শায়খুর রাঈস আবু আলী ইবনে সীনাকে নিজের শিক্ষক বলে উল্লেখ করেছেন। তবে ইবনে সীনার মৃত্যু যেহেতু ৪২৮ হিজরিতে অর্থাৎ খৈযামের জন্মের আগেই হয়েছে সেহেতু বলা যায় যে, ইবনে সীনা অন্য কারো মাধ্যমে অথবা তাঁর রচনাবলির সুবাদে খৈয়ামের কাছে শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন। (রেযাযাদে মালিক, প্রাগুক্ত) আরব ঐতিহাসিক ও জীবনীকার সাফাদী বলেন যে, খৈয়াম ছিলেন ইবনে সীনার বিখ্যাত শিষ্য বাহমানইয়ার ইবনে মরযেবানের শিষ্য। (ইকবাল আশতিয়ানী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৪-৪০৭)
খৈয়ামের সমসাময়িক মনীষীবৃন্দ, যেমন: সানায়ী গজনবী, আবুল কাসেম যামাখ্শারী, আরুযী সামারকান্দী ও আবুল হাসান বায়হাকী প্রমুখ যে তাঁকে ‘হাকীম’ (প্রাজ্ঞ মনীষী) ও গাণিতিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং কবি হিসেবে তাঁর নাম বা তাঁর রুবাইয়াতের নাম তাঁর সময়ের কোন রচনায় পাওয়া যায় না, তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে, কবিতাচর্র্চা তাঁর আসল পেশা ছিল না; বরং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-গবেষণার ফাঁকে যখন অবসর হয়েছেন তখন তিনি কৌতুহলবশত কবিতা রচনা করেছেন। (ফুরুগী, পৃ. ১৭-১৯) তাছাড়া কবিতাগুলো সংরক্ষণ বা বিন্যস্ত করে রাখার ব্যাপারেও তিনি তেমন গুরুত্ব দিতেন না।
বর্তমানে সবচেয়ে প্রাচীন যে রচনায় খৈয়ামের নামে ফারসি রুবাইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় তা হচ্ছে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর একটি রেসালা (৬০৬ হিজরি), যা তাফসীরুল কুরআনে সন্নিবেশিত। (মীনাবী, আয খাযায়েনে তুরকিয়ে, পৃ. ৭১)। হিজরি সপ্তম শতকে জামাল খলিল শারওয়ানী রচিত ‘নুযহাতুল মাজালিস’ গ্রন্থ, যাতে ২৯০ জন ফারসি কবির ৪০০০ প্রাচীন রুবাই সন্নিবেশিত আছে, সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, তা উমর খৈয়ামের মৌলিক রুবাইসমূহ চিহ্নিত করার একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। তাতে খৈয়ামের নামে মোট ৩৩টি রুবাই পাওয়া যায়। (ফুরুগী, পৃ. ২৯-৩৫)
১৮৫৭ সালে লন্ডনের অক্সফোর্ড বুদলিয়ান গ্রন্থাগারে খৈয়ামের রুবাইয়াতের একটি সংকলন ফিটজিরাল্ডের হস্তগত হয়। তিনি এর ৭৫টি রুবাইয়ের মুক্ত অনুবাদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং খৈয়ামের আত্মজীবনীসহ বিন্যস্ত করেন এবং ১৮৫৯ সালে সেটার ২৫০ কপি মুদ্রিত করেন। ১৮৬৮ সালে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ হওয়ার পরই সর্বমহলে বইটির ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় এবং বিশ্বজুড়ে খ্যাতি অর্জন করে। এরপর রুশ-ইরানবিশারদ যুকুফস্কি (১৮৫৮-১৯১৮ খ্রি.) খৈয়াম সম্বন্ধে এবং ‘উ™£ান্ত রুবাইয়াত’ শিরোনাম দিয়ে তাঁর গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেন এবং তাঁর কতিপয় মৌলিক রুবাই মুদ্রিত করেন। ডেনমার্কের বিখ্যাত লেখক আর্থার ক্রিস্টান সেন ‘খৈয়ামের রুবাইয়াত নিয়ে গবেষণা’ শিরোনামে একটি গ্রন্থে তাঁর কতিপয় মৌলিক রুবাই মুদ্রিত করেন। (ক্রিস্টান সেন, পৃ. ৪৬)। তাঁর পরে জার্মান পণ্ডিত ফেডরিস রূযেন (১৮৫৬-১৯৪৫ খ্রি.) খৈয়ামের নির্ভরযোগ্য রুবাই নিয়ে আরেকটি গ্রন্থ জার্মান ভাষায় মুদ্রিত করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি খৈয়ামের রুবাইয়াত নির্ণয় ও বাছাই করার মানদণ্ড হিসেবে ‘রুবাইয়াতে কলীদী’ বা চাবিরূপ রুবাইয়াত মতবাদ উপস্থাপন করেন। (মীনুরেস্কী, পৃ. ৩৬)
ইরানে সাদেক হেদায়াত ও আলী দাশ্তী ছিলেন প্রথম সারীর গবেষক যাঁরা ইউরোপীয় ইরানবিশেষজ্ঞদের রচনাবলি অধ্যয়ন করে ‘রুবাইয়াতে খৈয়াম’ নিয়ে সমালোচনামূলক মূল্যায়ন ও গ্রন্থনায় নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। সাদেক হেদায়াত ১৩০৩ ইরানি সালে রুবাইয়াতে খৈয়াম (১৯২৪) এবং খৈয়াম সংগীত ১৩১৩ সালে (১৯৩৪) প্রকাশ করেন। তিনি প্রাচীন রচনা থেকে ১৪টি চাবিরূপ রুবাই নিয়ে ১৪৩টি খৈয়াম সংগীত চয়ন করেন। ১৩২০ ইরানি সাল তথা ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মাদ আলী ফুরুগী ৬৬টি রুবাইকে অপর ১১৩টি রুবাই বাছাই করার চাবি হিসেবে ব্যবহার করেন, যা হেদায়াতের কাজের চেয়ে আরো বেশি সমাদৃত হয়। অনুরূপভাবে আলী দাশ্তী, রশীদ ইয়াসেমী ও মুহসিন ফরযানার মতে অন্যান্য ইরানি গবেষকও খৈয়ামের রুবাইয়াত বাছাইয়ের কাজ আঞ্জাম দেন এবং আরো নতুন রুবাই খৈয়ামের বলে শনাক্ত করেন। খৈয়ামের রুবাইয়াতসমূহ অন্যদের সাদৃশ্যপূর্ণ রুবাইয়ের সাথে মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি ফারসি ভাষায় খৈয়াম মতবাদ নামে একটি মতবাদের বিদ্যমানতা প্রমাণ করে। বিষয়টিকে ক্রিস্টান সেন ঠিকই এই রুবাইয়াতের ‘ইরানি প্রাণসত্তা’ নামে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি মনে করেন যে, এ রুবাইসমূহের মৌলিকতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ এর কাব্যিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বকে কিছুমাত্র হ্রাস করে না।
সাম্প্রতিককালে গবেষকগণ রুবাইসমূহ পরিশোধন করে রুবাইয়াতের অর্থের পরিমণ্ডলটি চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। সাদেক হেদায়াত রুবাইয়াতে খৈয়ামকে (১) সৃষ্টির রহস্য (২) জীবনের বেদনা (৩) অনাদির লিখন (৪) কালের চক্রবাক (৫) ঘূর্ণায়মান অণু (৬) যাই হবার হোক (৭) মুহূর্তকে কাজে লাগাই প্রভৃতি শিরোনামে বিভাজিত করেছেন। তবে আলী দাশ্তী এসব রুবাইয়াতকে অস্তিত্বের জগত, অনস্তিত্ব, মৃত্যু, জীবনপ্রবাহ, মাটির কলসি ও আদম প্রভৃতি শিরোনামে বিন্যস্ত করেছেন।
উমর খৈয়াম ও কাজী নজরুল ইসলাম
কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৪৪ সালের শেষভাগে কুরআন মজীদের ত্রিশতম পারা আমপারার অনুবাদের সময় রুবাইয়াতে খৈয়ামের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। নজরুল রচনাবলী তৃতীয় খণ্ডে ১০১ থেকে ১৩৯ পৃষ্ঠায় রুবাইয়াতে খৈয়ামের বাংলা অনুবাদ সন্নিবেশিত আছে। এতে বাংলা ভাষায় একটি ভূমিকা ও ১৯৭টি রুবাইয়ের অনুবাদ সন্নিবেশিত আছে। নজরুল ইসলাম কীভাবে খৈয়ামের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন এবং কে বা কোন জিনিস তাঁকে উমর খৈয়ামের রুবাইয়াত অনুবাদ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল সে ব্যাপারে সঠিক তথ্য জানা নেই। (আহমদ, ২০০১) কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে, হয়ত শ্রী কান্তি ঘোষের রচনা পড়ে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। কেননা, নজরুল ইসলাম সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে ফিরে আসার আগেই রুবাইয়াতে খৈয়ামের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। ফিটজিরাল্ডের অনুবাদ দ্বারা তাঁর প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনাও খুবই কম। কেননা, নজরুল ইসলাম ফিটজিরাল্ডের অনুবাদ ঠিকভাবে জানতেন না এবং তার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন : ‘যারা খৈয়ামের রুবাইয়াত পড়ে তাঁকে ভোগবাদী বলে মনে করেন, তাঁরা ভুলের মধ্যে আছেন। কেননা, শুধু কতিপয় রুবাইয়ের কারণে তাঁর কবিতা সম্বন্ধে এমন মন্তব্য করা যেতে পারে।’ (আহমদ, পৃ. ৭-৮)। ফিটজিরাল্ডের সাথে নজরুল ইসলামের প্রধান তফাত হচ্ছে ফিটজিরাল্ড খৈয়ামকে নাস্তিক বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু নজরুল ইসলাম এ কথা স্বীকার করেন নি, তিনি খৈয়ামকে একেশ্বরবাদী, সুফি এবং শরীয়তপন্থী মুসলমান বলে মনে করেন। নজরুল ইসলাম হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে খৈয়ামের চারটি রুবাই অনুবাদ করেন এবং বলেন : ‘যে ব্যক্তি ধর্মপ্রাণ অথবা শরীয়তের প্রতি আস্থাশীল নন, তিনি কিছুতেই ধর্মীয় মহান ব্যক্তি ও পয়গাম্বরদের প্রতি এমন ভক্তি ও সম্মান দেখাতে পারেন না।’
নজরুল ইসলাম রুবাইয়াতে উমর খৈয়ামকে ছয় ভাগে ভাগ করেন। (১) অভিযোগ (যুগের নানা চালচিত্রের প্রতি অভিযোগ) (২) নিন্দামূলক (৩) বিরহ (৪) বাসন্তি (৫) ধর্মহীনতা (৬) মুনাজাত (প্রার্থনা)।
তিনি রুবাইয়াত অনুবাদে মূল ফারসির সাহায্য নিয়েছেন। তিনি ‘রুবাইয়াতে খৈয়াম’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘বাজারে উমর খৈয়ামের বলে যে ১০০০ এর বেশি রুবাই পাওয়া যায় তা থেকে ২০০ এর কিছু বেশি, তাও ফারসি ভাষায় রচিত রুবাই থেকে চয়ন করেছি। কেননা, আমার দৃষ্টিতে বাকি রুবাইগুলো খৈয়ামের চিন্তাদর্শনের সাথে মোটেও খাপ খায় না।… আমি আমার পাণ্ডিত্য দেখানোর জন্যে খৈয়ামের ভাব, ভাষা ও বর্ণনারীতিকে মোটেও পরিবর্তন করি নি। অবশ্য এ কাজের জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করেছি।’ নিশ্চয়ই যদি নজরুল ইসলাম ফারসি ভাষার উপর পারদর্শী না হতেন তাহলে তিনি এমন দাবি করতে পারতেন না। (আহমদ, পৃ. ১০) কোন কোন লেখক মনে করেন যে, তিনটি কারণে বাংলায় ‘রুবাইয়াতে খৈয়াম’ এর অন্যান্য অনুবাদক, যেমন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, কান্তি চন্দ্র, সিকান্দর আবু জাফর, উমর আলী শাহ, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও নরেন দেব প্রমুখ তাঁদের অনুবাদে নজরুল ইসলামের মতো সূক্ষ ও তীক্ষè দৃষ্টি, দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য দেখাতে পারেন নি, এই কারণগুলো হচ্ছে-
১. নজরুল ইসলাম ‘রুবাইয়াতে খৈয়াম’ অনুবাদের আগেই ‘রুবাইয়াতে হাফেজ’ অনুবাদ করে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করেন।
২. নজরুল ইসলাম ও খৈয়াম উভয়ে ছিলেন মুসলমান, তাঁদের মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক অভিন্নতা ও মিল ছিল।
৩. নজরুল ইসলাম ফারসি ভাষা জানতেন এবং সরাসরি ফারসি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। (সাঈদ, ২০০৪, পৃ. ১১, ১২)
কাজী নজরুল ইসলাম পূর্ণ দক্ষতা, রুচিবোধ ও নিজস্ব শৈল্পিক আঙ্গিকে ‘রুবাইয়াতে খৈয়াম’কে বাংলাদেশের সমাজে উপস্থাপন করতে সক্ষম ও সফল হয়েছেন।
‘রুবাইয়াতে খৈয়াম’ এর বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য
উমর খৈয়াম কবিতার কাঠামো বা শব্দ চয়ন ও পরিভাষা ব্যবহারে কিংবা কাব্যভাবনায় অন্য কোন কবিকে অনুসরণ করেন নি। কেননা, তাঁর কাব্যরীতি সম্পূর্ণ আলাদা। যখন ‘খৈয়াম আদর্শ’ বলা হয় তখন তাঁর কাব্যভাবনাকেই বুঝানো হয়। তিনি কেবল সংক্ষিপ্ততার কাব্যালঙ্কার ব্যবহার করেছেন। তাঁর কবিতার ভাবধারা দার্শনিক। তাও আংশিক ও বাস্তবানুগ। যা সহজে শ্রোতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ফেরদৌসির মতো তাঁর ভাষার বৈশিষ্ট্য ছিল ফারসির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ। নেহাত প্রয়োজনে আরবি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর কবিতার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে :
(১) সৃষ্টিজগতের রহস্য
آنان که محیط فضل و آداب شدند
در جمع کمال شمع اصحاب شدند
ره زین شب تاریک نبردند برون
گفتند فسانه ای و در خواب شدند.
জ্ঞান গরিমায় ঋদ্ধ ও যশস্বী যারা মহিয়ান
পূর্ণতার গুণে যারা সবার মধ্যমণি আজ
আঁধার রাতের ঘোমটা খুলতে পারে নি তারা কেউ
বলেছেন কতক রূপকথা, ঘুমিয়ে গেছেন তার পরে।
(২) জীবনের বেদনা
افسوس که بی فایده فرسوده شدیم
وز داس سپهر سرگون سوده شدیم
دردا و ندامتا که تا چشم زدیم
نا بوده به کام خویش نابوده شدیم.
আফসোস যে অনর্থক নিঃসার ¤্রয়িমাণ হলাম
আকাশের কাস্তে বিছিয়ে দিয়েছে জমিনে নিঃস্ব
হায় আফসোস, হায় বেদনা! চোখের পলক না ফেলতে
ধ্বংসে তলিয়েছি, আশা-আকাক্সক্ষা রয়ে গেল অপূরণ।
(৩) কালের চক্রবাল
افسوس که نام جوانی طی شد
وان تازه بهار زندگانی طی شد
حالی که و را نام جوانی گفتند
معلوم نشد که او کی آمد کی شد.
আফসোস যে যৌবনের সুনাম হারিয়ে গেল
জীবনের এই নতুন বসন্ত ফুরিয়ে গেল
এখন যাকে তারা যৌবন নামে আখ্যায়িত করে
বুঝাই গেল না সে কখন এল, কখন চলে গেল।
(৪) দুনিয়ার তুচ্ছতা
بنگر به جهان چه طرف بر بستم هیچ
وز حاصل عمرم چیست در دستم هیچ
شمع طربم ولی چو بنشیتم هیچ
من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ.
দেখ এ জগতটা, চোখ মুদলে তো সব হবে শেষ
জীবনের সঞ্চয়ের আছে কী, আমার হাতে কিছুই না
আমি উৎসবের বাতি বটে তবে বসে গেলে কিছুই না
জামশিদ বাদশাহর বাটি, তবে ভেঙে গেলে কিছুই না।
(৫) মৃত্যুর পর দেহ নিঃশেষ হওয়া
هر ذره که بر روی زمین بوده است
خورشید رخی زهره جبینی بوده است
گرد از رخ آستین به آزرم افشان
کان هم رخ خوب نازنینی بوده است.
পৃথিবীর মাটির উপরে যত অণু পরমাণু ছিল
সূর্য সম আনন, কপাল ছিল সপ্তর্ষি মণ্ডল
আস্তিনের আননের ধুলো পড়েছে আমার লজ্জায়
তাও যে কোন এক প্রেয়সীর সুন্দর আনন ছিল।
(৬) মুহূর্তকে কাজে লাগাই
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
این یک دم عمر را غنیمت شمریم
فردا که از این دیر کهن در گذریم
با هفت هزار سالگان سربه سریم.
হে বন্ধু! এস কালকের চিন্তা নিয়ে যেন না থাকি
জীবনের এই একটি মুহূর্তকে অমূল্য গণ্য করি
কাল যখন এই পুরনো বসত ছেড়ে চলে যাব
অনন্তকালবাসীদের সাথে হবে বসতবাড়ি।
উপসংহার
আমরা যদি তিনজন ইরানি কবির কথা উল্লেখ করি, যাঁদের কবিতা ইরানের বাইরে ও ভেতরে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং শত শত বছর ধরে তা নিয়ে গবেষণা ও আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে, তাহলে তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন হাকীম উমর খৈয়াম এবং তাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। ইরানপ্রেমিক এই মহান ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্ব, প্রাজ্ঞ মনীষী ও অতি উচ্চমানের কবির সঠিক পরিচিতি যদি তুলে ধরা হতো, তাহলে তাঁর প্রকৃত ইতিহাস ও তাঁর চিন্তাধারার গভীরতার চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হতো; কিন্তু দুঃখজনকভাবে ফিটজিরাল্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর সংস্কৃতিসেবীদের পক্ষ হতে এমন প্রচার-প্রপাগান্ডার ধু¤্রজাল সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে এই ধু¤্রজালের মাঝে উমর খৈয়ামের আসল পরিচয় ধোঁয়াশা হয়ে গেছে। আলী ইবনে যায়দ বায়হাকী ‘তাতিম্মা সাওয়ানুল হিকমা’ কিতাবে মুহাম্মাদ বাগদাদী সূত্রে হাকীম উমর খৈয়ামের সর্বশেষ যেসব কথাবার্তা এবং এ জাতীয় আরো যেসব শক্তিশালী ও প্রামাণ্য সাক্ষ্য বিদ্যমান আছে, তাতে দেখা যায় যে, উমর খৈয়ামকে নিয়ে যে ধরনের প্রপাগান্ডা চালানো হয়েছে আসল ব্যাপার তার উল্টা। জর্জ সার্টনসহ সকল ঐতিহাসিকের সাক্ষ্য অনুযায়ী হাকীম উমর খৈয়াম ছিলেন জগদ্বিখ্যাত একজন গাণিতিক। ‘চাহার মাকালে’ গ্রন্থে নিযামী আরুযীর বর্ণনা এবং ‘তাযকিরা আরাফাতুল আ‘শেকীন ওয়া আরাসাতুল আরেফীন’ গ্রন্থে তাকিউদ্দীন বালায়ানীর বর্ণনা মোতাবেক উমর খৈয়াম ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন মনীষী এবং আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত মহান বুযুর্গ। একই সাথে রুবাই রচনায় একটি নিজস্ব রীতির প্রবর্তক।
তথ্যসূত্র
১. দাশ্তী, আলী, ‘দামী বা খাইয়াম’ (খৈয়ামের সাথে কিছুক্ষণ), ১৩৪৯ (১৯৭০)
২. হুমায়ী, জালাল উদ্দীন, ‘তারাবখানায়ে রুবাইয়াতে খৈয়াম ’, ১৩৬৭ (১৯৮৮)
৩. ফরজানা, মুহসেন, ‘নকদো বাররাসী রুবায়ীহা’য়ে খৈয়াম’, ১৩৫৬ (১৯৭৭)
৪. ফুরুগী, মুহাম্মাদ আলী, ‘রুবাইয়াতে খৈয়াম’, ১৩৭১ (১৯৯২)
৫. ক্রিস্টান সেন, আর্থার, ‘বাররাসী ইন্তেকাদী রুবাইয়াতে খাইয়াম’, ফরীদুন বাদরেয়ী অনূদিত, ১৩৭৪ (১৯৯৫)
৬. মীনুরেস্কী, উইলিয়াম, ‘উমর খৈয়াম’, বাহাউদ্দীন খুররমশাহী অনূদিত, ১৩৭৩ (১৯৯৪)
৭. মুজতবা, মীনাবী, ‘আয খাযায়েনে তুর্কিয়ে’, ১৩৩৫ (১৯৫৪)
৮. নাজম উদ্দীন রাযী, ‘মিরসাদুল ইবাদ’, ১৩৫২ (১৯৭৩)
৯. হেদায়াত, সাদেক, ‘তারানেহা’য়ে খৈয়াম’, ১৩৩৪ (১৯৫৫)
১০. বেলায়াতী, আলী আকবর, ‘হাকীম উমর খৈয়াম, আফরীনান্দেগা’নে ফারহাঙ্গো তামাদ্দুনে ইসলাম ও বূমে ইরান’ (ইসলাম ও ইরান ভূমির সভ্যতা সংস্কৃতির নির্মাতারা), তেহরান, ১৩৮৯
১১. মির্জা ফতেহ আলী, সৈয়দ আলী, ‘রুবাইয়াতে খৈয়াম, দা’নেশনা’মায়ে যাবা’ন ও আদাবে ফা’রসি’, ১৩৮৮ (২০০৯)
১২. বায়হাকী, আবুল হাসান আলী ইবনে যায়দ, ‘তাতিম্মা সাওয়ানুল হিকমা’, ১৩১৮ (১৯৩৯)
১৩. রেযা’যাদে মালেক, রহীম, ‘দা’নেশনা’মেয়ে খৈয়া’মী’, ১৩৭৭ (১৯৯৮)
১৪. নেযামী আরূযী সামারকান্দী, ‘চাহার মাকালে’, ১৩৮৪ (২০০৫)
১৫. নজরুল ইসলাম, ‘নজরুল রচনাবলী’, সম্পাদনা: আব্দুল কাদের, খণ্ড ১-৪, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪
১৬. নজরুল ইসলাম, নজরুল ইসলামের ইসলামি গান, সম্পাদনা : আব্দুল মুকিত চৌধুরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮০
১৭. আরেফীন, শাহনাজ, ‘কাজী নজরুল ইসলাম ও বাংলাদেশে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব’, তেহরান, ১৩৯৪ (২০১৫)
*ভিজিটিং প্রফেসর
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অনুবাদ : ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী