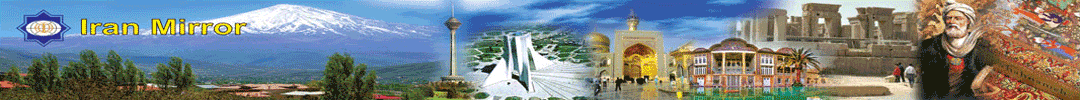ইতিহাসের দৃষ্টিতে হাফিজ
পোস্ট হয়েছে: মার্চ ১২, ২০১৬
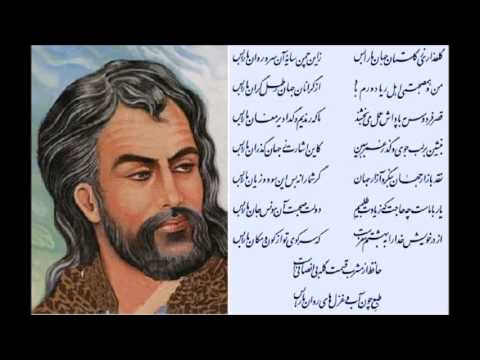
শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহহারী :
হাফিজকে তাঁর নিজের যুগ কেমন মানুষ হিসাবে জানত? ঘটনাক্রমে হাফিজ তাঁর নিজের যুগে এমনভাবে পরিচিত হতেন যে, তাঁর অন্যান্য গুণবৈশিষ্ট্য একদিকে তাঁর কবিত্বের ওপরে যেমন প্রবল ছিল তেমনি তাঁর আরেফ ও দরবেশ হওয়ার ওপরও প্রবল ছিল। অর্থাৎ প্রথমত তাঁকে একজন পেশাদার কবি হিসেবে মানা হতো না। হাফিজ আসলেও বেশি কবিতা লেখেননি। হাফিজের নিজের লেখা কবিতা যেগুলোকে সত্যিই প্রমাণ করা যায় যে, তাঁর লেখা, এমন কবিতার সংখ্যাকে তাঁর জীবনের আয়ুষ্কাল দিয়ে ভাগ করে দেখা গেছে যে, হয়তো বা তিনি প্রতি মাসে একটি করে গযল তথা কবিতা রচনা করে থাকবেন। তিনি অন্যান্য কবি, যেমন নিযামী, ফেরদৌসী, এমনকি মৌলাভী’র (রূমীর) থেকেও ভিন্ন। কেননা, তাঁরা নিজ যুগে কবি হিসেবেই বেশি পরিচিত ছিলেন। অবশ্য, হাফিজের কবিতার স্বল্পতা সত্ত্বেও সে যুগেই তা খ্যাতি লাভ করে। সেগুলো কেবল শিরাজের গণ্ডিই নয়, বরং ইরানের সীমানাও পার হয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। তবে কথা হলো, তিনি কবিতা বেশি রচনা করেন নি এবং তাঁর আমলে একজন কবি বলে প্রসিদ্ধও ছিলেন না। তদ্রুপ, নিজের যুগে তিনি একজন পেশাদার দরবেশ ও সুফি হিসেবেও বিখ্যাত ছিলেন না। সে সময়ে সুফি-সাধকরা গোপনে বিচরণ করতেন না, তাঁদের সিলসিলা, পীর, গুরু সবই নির্দিষ্ট ছিল। সুফিদের সিলসিলায় কে কার পীর ছিলেন, কে কার শিষ্য ছিলেন এগুলো পরিষ্কারভাবে লেখা রয়েছে। এছাড়াও দেখা যাবে যে, তাঁরা অধিকাংশই বেশভূষায় ও আলখেল্লায় অন্যদের থেকে আলাদা, মাথার টুপিও তাঁদের স্বতন্ত্র। শেষের দিকে এমনকি কাশকুল ও বাঁকা কুড়ালও তাঁদের হাতে শোভা পেত। মাথার চুল কাটতেন না। স্বয়ং হাফিজের ভাষায় : ‘মাথার চুল না কাটলেই যে কেউ দরবেশ হয়ে যায় না।’
বাহ্যত, হাফিজের কোনো সুফি আলখেল্লা ছিল না। যদিও কখনো কখনো তাঁর উক্তিতে ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন : ‘হাফিজ! এ পশমি খিরকা ফেলে দিয়ে এগিয়ে যাও।’
কিন্তু এসব কথা প্রমাণ করে না যে, প্রকৃতই হাফিজ এ পশমি খিরকা পরতেন। এখানে যে ‘পশমি খিরকা’ কথাটি এসেছে এটিও হাফিজের অনেক কথার মতোই যা নিয়ে পরবর্তীকালে আলোচনা করব। আমি এটা শতভাগ নাকচ করব না যে, হাফিজ সুফি বেশভূষা পরিধান করতেন না। তবে আমি যতটুকু পড়াশুনা করেছি তাতে কোথাও প্রমাণ মেলেনি যে, তিনি সুফি বেশ ধারণ করতেন; বরং সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে এর বিপরীতে। এমনকি এ মানুষটি যিনি তাঁর কাব্যে একটি বিশেষ চিন্তাধারার ওপর খুব বেশি জোর দিয়েছেন যে, মুরুব্বীবিহীন (অর্থাৎ পথনির্দেশবিহীন) সুফিবাদে তথা মুর্শিদ, ‘শেখ’ কিংবা ‘গুরু’কে বাদ দিয়ে কেউ এ পথ পাড়ি দেবে, এটা অসম্ভব।
قطع اين مرحله بي همرهي خضر مكن
ظلمات است بترس از خطر گمراهي
‘খিযিরকে সঙ্গে না নিয়ে এ পথ পাড়ি দিতে যেও না
সাবধান! অন্ধকার অমানিশা চারদিকে, বিপথগামিতাকে ভয় কর।’
পরবর্তীকালে আমরা বলব যে, হাফিজ এ মর্মে অনেক কবিতা লিখেছেন। এটি একটি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার ওপর এ শ্রেণিটি বেশি বেশি নির্ভর করে চলেন। যেন একজন পারিবারিক চিকিৎসকের মতো (সাধারণ চিকিৎসকদের মতো নয়) এই আত্মিক ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসায় একজন সতর্ক প্রহরী চিকিৎসকের দরকার। অর্থাৎ যে সর্বক্ষণ তার আত্মার ওপর দখল রাখবে। তবে এমন যেন না হয় যে, আগে অসুস্থ হয়ে পড়বে তারপর অনুসন্ধান করতে বের হবে কোথায় চিকিৎসক রয়েছে। তারপর তার কাছে গিয়ে নিজের অসুখের বিবরণ তুলে ধরবে যেমনটা আমরা সচরাচর করে থাকি।
এমনটা নয়। শুধু কিতাব পড়াই যথেষ্ট নয়। চিকিৎসকের সাথে সাক্ষাৎ করাও যথেষ্ট নয়। বরং এদের বিশ্বাস হলো প্রত্যেকেরই একজন করে সার্বক্ষণিক চিকিৎসক প্রয়োজন যে তাকে দেখভাল করবে। এভাবে ছাড়া সাধনা অসম্ভব (কেউ এ পথ পরিভ্রমণ করতে পারবে না)।
এ মানুষটি মুর্শিদের বিষয়টির ওপর এত বেশি জোর দেয়ার পরও এখনো পর্যন্ত কেউ দেখাতে পারেনি যে, তাঁর মুর্শিদ কে? নিঃসন্দেহে কেউ না কেউ ছিলেন, তবে (নির্দিষ্ট) নেই। বোঝা যায় যে, তাঁর মুর্শিদ সুফিদের এ প্রসিদ্ধ রীতির শ্রেণিভুক্ত কেউ ছিলেন না। আর সামগ্রিক বিচারে শিয়া চিন্তাধারায় সুফিবাদ সুন্নি চিন্তাধারার সুফিবাদ থেকে এক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। কেননা, এসব সিলসিলা ও আনুষ্ঠানিকতার ঝক্কি বেশি বেশি আহলে সুন্নাতের সুফিবাদে পরিলক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে, শিয়া সুফিবাদ একদিকে যেমন গভীরতাসম্পন্ন, অন্যদিকে এসব গুরু ও মুর্শিদের কাহিনীও সেখানে খুব বেশি প্রাসঙ্গিক নয়। কার মুর্শিদ কে কিংবা কার শেখ কে তা দেখিয়ে দেবার প্রয়োজন হতো না। এমনও অনেকে ছিলেন যাঁদেরকে তাঁদের সমসাময়িক লোকজনও তেমন চিনত না, অথচ ঐশী সাধনায় তাঁরা উচ্চতর মাকামের অধিকারী ছিলেন। এমনকি তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও স্বজন-পরিজনরাও জানত না যে, তিনি উচ্চতর আধ্যাত্মিক সাধক। অথচ নিঃসন্দেহে তাঁরও মুর্শিদ ছিল । আর শুধু তাঁর ঐ বিশেষ গুরুই তাঁকে চিনতেন। তিনি ভিন্ন অন্য সবার কাছে (ঐ ব্যক্তি) সবসময় লুক্কায়িত থাকতেন। আমি অবশ্য একটি লক্ষণ খুঁজে পেয়েছি যা ইনশা আল্লাহ্ পরে বলব। হাফিজ কিছুকাল চেষ্টা করেছেন ওস্তাদ, গুরু ও মুরুব্বী ছাড়াই নিজে নিজে এ পথকে পরিভ্রমণ করতে। বেশ কয়েক বছর ধরে হাড়ভাঙা পরিশ্রম চালিয়ে এমনকি কিছু কিছু মুকাশিফাত তথা রহস্যও উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হন। কিন্তু উপলব্ধি করেন যে, গুরু ও মুর্শিদ বিনা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, ‘এমনটি করেছিলাম, কিন্তু হয়নি। ঐরকম করেছিলাম, তবুও হয়নি।’ পরিশেষে বলেন, ‘পথপ্রদর্শক মুর্শিদ বিনা চেষ্টা করেছি, কিন্তু সাধন হয়নি।’ বোঝা যায় যে, হাফিজ কিছুকাল এমনটি ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে নিশ্চিতভাবে মুর্শিদ খুঁজে পান।
-জ্বি, এটাই হলো একটি চিহ্ন যে, হাফিজ যদি এমন কেউ হতেন যিনি তাঁর নিজের যুগে (সাধক) বেশধারী আর তাঁর মাথায় কয়েক কোনাবিশিষ্ট টুপি ইত্যাদি থাকত, তাহলে নিঃসন্দেহে তাঁর শেখ তথা মুর্শিদও বিখ্যাত ও পরিচিত থাকতেন। আর সবাই বলত (তিনি অমুক মুর্শিদের শিষ্য ছিলেন)।
যাঁরা হাফিজের সমসাময়িক কালে কিংবা তাঁর কাছাকাছি সময়ে এসে তাঁর গুণের কথা লিখেছেন এবং তাঁকে নানা উপাধিতে ভূষিত করেছেন তাঁরা হাফিজকে ‘কবি’ উপাধিও প্রদান করেননি, ‘আরেফ’ উপাধিও প্রদান করেননি। বরং যেন মনে হবে আসলে একজন ফকীহ, একজন হাকিম, একজন সাহিত্যিকেরই প্রশংসা তুলে ধরেছেন। তাঁর সব শিরোনামই রয়েছে শুধু ওই ধরনের শিরোনাম ছাড়া। অবশ্য অন্যরা এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করেছেন। মরহুম শেখ মুহাম্মাদ খান কাযভীনি ‘দিওয়ানে হাফিজ’ গ্রন্থের ভূমিকায় এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আপনারা জানেন যে, ‘দিওয়ানে হাফিজ’ গ্রন্থটি প্রথমবার হাফিজের মৃত্যুর পর তাঁরই সমসাময়িক ব্যক্তিদের একজন, দৃশ্যত তাঁর সহপাঠী- যাঁরা কতিপয় শিক্ষকের কাছে এসব বাহ্যিক বিষয়, যেমন হিকমত, কালাম, যুক্তিবিদ্যা, তাফসীর পড়াশুনা করতেন- সংকলন করেন। তাঁর নাম কোনো কোনো মুদ্রণে ‘মুহাম্মাদ গুল আন্দম’ লেখা রয়েছে। তবে কাযভীনি ও অন্যরা বলেন, এ নামটি পরবর্তী যুগের সংস্করণগুলোতে সংযুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু অনেক প্রাচীন সংস্করণে মুহাম্মাদ গুল আন্দম নামটি নেই। তবে এটা স্পষ্ট যে, তিনি হাফিজের সমসাময়িকদের একজন ছিলেন। ওই সমসাময়িক ব্যক্তি বলেন, আমাদের শিক্ষক কিয়ামুদ্দীন আব্দুল্লাহ্ (তাঁদের ওস্তাদদের একজন) হাফিজকে তাগিদ করতেন, ‘এসব কবিতা জমা করে রাখ। এসব কবিতা নষ্ট হয়ে যাবে- এটা দুঃখজনক হবে।’ পক্ষান্তরে হাফিজ তুচ্ছতা প্রকাশ করতেন। যেন এক আধ্যাত্মিক উৎকৃষ্ট অবস্থা তাঁকে অনুমতি দিত না যে, তিনি এগুলো গুছিয়ে রাখবেন। (উক্ত ব্যক্তি) বলেন, ৭৯২ হিজরিতে হাফিজের ইন্তেকালের পর আমরা উদ্যোগী হয়ে কবিতাগুলো একত্র করি। হাফিজের সহপাঠী এ ব্যক্তিটি যখনই হাফিজের নাম উল্লেখ করেন তখন তাঁকে এইসব শিরোনামে সম্বোধন করেন :
ذات ملك صفات، مولانا الاعظم السعيد، المرحوم الشهيد، مفخر العلماء، استاد نحارير الادباء، معدن اللطايف الروحانية، مخزن المعارف السبحانية، شمس الملة و الدين محمد الحافظ الشيرازي
‘ফেরেশতার গুণ-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, মহা সৌভাগ্যবান মাওলানা, মরহুম শহীদ (আধ্যাত্মিক সাধনার পথে), আলেমদের গৌরব, সাহিত্যিকদের শিরোমণি, আত্মিক সূক্ষ্ম বিষয়াদির খনি, ঐশ্বরিক জ্ঞান-শিক্ষার ভাণ্ডার, মিল্লাত ও দ্বীনের সূর্যসম, মুহাম্মাদ হাফিজ শিরাজী।’’
এর মধ্যে কোনো ‘আরেফ’ শিরোনাম নেই, কোনো ‘কবি’ শিরোনামও নেই। পরবর্তীকালে আরো যোগ করে বলেন,্রطيب الله تربته و رفع في عالم القدس رتبتهগ্ধ – ‘আল্লাহ্ তাঁর কবরের মাটিকে পবিত্র করুন, আর ঐশ্বরিক জগতে তাঁর স্থানকে উচ্চ করুন।’ যেন একজন আলেম ফকীহ’কে প্রশংসা করছেন। মরহুম কাযভীনি আরো বলেন, ‘দিওয়ানে হাফিজের’ একটি পাণ্ডুলিপি এমন একজন লেখকের হাতে লেখা যা হয় হাফিজের সময়কালের খুব কাছাকাছি হবে, না হয় তাঁর সমসাময়িক হবে, সেই পাণ্ডুলিপি থেকে কপি করা। সেখানে শেষাংশে এসে যখনই এই মানুষটিকে স্মরণ করা হয়েছে তখন নিম্নোক্ত ভাষায় বলা হয়েছে :
تم ديوان المولي العالم الفاضل، ملك القرّاء و افضل المتأخرين، شمس الملة و الدين ، مولانا محمد الحافظ روّح الله روحه و اوصل فتوحه و نوّر مرقده
‘সমাপ্ত হলো এ দিওয়ান যার লেখক একজন মাওলা, আলেম ও ফাজেল, ক্বারীদের অধিপতি, বর্তমান শেষযুগের শ্রেষ্ঠতম, জাতি ও ধর্মের সূর্য, মাওলানা মুহাম্মাদ হাফিজ, আল্লাহ্ তাঁর আত্মাকে সুরভিত করুন এবং তাঁর অন্তরকে প্রসন্ন করুন আর আলোময় করুন তাঁর কবরকে।’
মরহুম কাযভীনি বলেন :
‘খাজা হাফিজের আমলের খুব নিকটবর্তী কিংবা হয়তো বা খাজার সমসাময়িক এ লেখকের যেসব উপাধি ও বন্দনা তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়েছে, যেমন قطب السالكين – সাধকদের কেন্দ্রবিন্দু, فخر المتألهين – আল্লাহতাত্ত্বিকদের গৌরব,ذخر الاولياء – আউলিয়াগণের সঞ্চয়, شمس العرفاء – আরেফগণের সূর্য, عارف معارف لا ريبي – সন্দেহাতীত জ্ঞানের দিব্য জ্ঞানী, واقف مواقف اسرار غيبي – গায়েবী রহস্যাবলি সম্পর্কে অবগত ইত্যাদি (যেগুলো অধুনা রচনাবলিতে সচরাচর তাঁর নামের সাথে যুক্ত করা হয়) সেগুলোর কোনোটাই এমন কোনো ভাষা নয় যা থেকে প্রমাণিত হতে পারে যে, খাজা সে যুগের একজন খ্যাতিমান আরেফ তথা সুফি ছিলেন। এ থেকে হয়তো এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, খাজা তাঁর স্বীয় আমলে আরেফ ও সুফিদের কাতারভুক্ত হওয়ার চাইতে বরং বেশি বেশি আলেম, গুণী ও পণ্ডিতদের কাতারভুক্ত গণ্য হতেন। অর্থাৎ তাঁর ইরফান ও সুফিবাদী দিকটির চেয়ে জ্ঞান, গুণ ও সাহিত্যের দিকটি প্রবল ছিল। এছাড়া লেখক কর্তৃক তাঁকে ملك القرّاء -‘ক্বারীদের অধিপতি’ বলে আখ্যায়িত করা থেকে ইঙ্গিত মেলে যে, খাজা তাঁর আমলে ক্বারীদের মধ্যে একজন ক্বারী হিসেবে গণ্য হতেন এবং সে যুগে এ পদবি দ্বারাই অধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত কবিতার এ ছত্রেও তার সত্যতা প্রতিপন্ন হয় :
عشقت رسد به فرياد ار خود به سان حافظ قرآن زِبَر بخواني با چارده روايت روايت
‘তোমার প্রেম পৌঁছে যাবে ফরিয়াদ রূপে যদি তুমি কুরআনকে
মুখস্থ পাঠ করতে পারো ক্বিরাআতের চৌদ্দ রীতিতে হাফিজের মতো করে!’
তাঁর ব্যাপারে প্রযোজ্য এ ধরনের স্পষ্ট ঘোষণা কখনো কাব্যিক অতিরঞ্জন হতে পারে না। আর তাঁর নামের পৃথক অংশ হিসেবে ‘হাফিজ’ (অর্থাৎ কুরআনের হাফিজ) হলো তাঁর নামের সাথে সংযুক্ত এবং তার উল্লেখযোগ্য ও প্রকাশ্য বিশেষণ মাত্র।
আমার কাছে হাফিজের দিওয়ানের দু’টি সংস্করণের বেশি নেই। একটি মরহুম কাযভীনির, অন্যটি জনাব সাইয়্যেদ আবুল কাশেম আঞ্জাবী শিরাজীর। অবশ্য এ দু’টি পরস্পর পরিপূরক হতে পারে। কেননা, মরহুম কাযভীনি বেশি বেশি নির্ভর করেছেন প্রাচীন পাণ্ডুলিপির ওপর। তিনি এসব রুচি-অভিরুচির কথায় আস্থা রাখেন না। পক্ষান্তরে জনাব আঞ্জাবী ও তাঁর সমগোত্রীয়রা হলেন এমন যে, পুরাতন সংস্করণগুলোর প্রতি খুব বেশি ভ্রুক্ষেপ করার পক্ষপাতি নন। তাঁরা বলেন, আমরা এমনকি কথিত দিওয়ানসমূহের কোনো কবিতা যদি দেখি যে, হাফিজের কবিতার সাথে খাপ খায় তাহলেও তা গ্রহণ করব।
হাফিজের আনুষ্ঠানিক শিক্ষকও ছিলেন অনেক। তাঁদের মধ্যে একজন মীর সাইয়্যেদ শরীফ জুরজানী নামে প্রসিদ্ধ। আঞ্জাবীর ‘দিওয়ানে হাফিজ’ এর ভূমিকায় মরহুম ড. মুয়ীন লিখিত সুভাষী হাফিজ থেকে বর্ণনা করেন (মরহুম ড. মুয়ীন এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি সর্বদা সপ্রমাণ কথা বলতেন, প্রমাণ ছাড়া কখনোই কথা বলতেন না) :
“যখনই মীর সাইয়্যেদ শরীফ আল্লামা গুরগানীর ক্লাসে কবিতা পড়া হতো, তিনি বলতেন, ‘এসব অনর্থক কথাবার্তা বাদ দিয়ে হিকমত ও দর্শনের কথা বল।’ কিন্তু যখন শামসুদ্দীন মুহাম্মাদের পালা আসত তখন বলতেন, ‘তোমার ওপর কি ইলহাম হয়েছে? তোমার গযল পড়ে শোনাও।’ এ প্রেক্ষাপটে আল্লামার শিষ্যরা প্রতিবাদ করতেন। ‘এর রহস্য কি যে আপনি আমাদেরকে কবিতা পড়তে নিষেধ করেন, অথচ হাফিজের কবিতা শোনার জন্য আগ্রহ দেখান?’ উত্তরে ওস্তাদ বলতেন, ‘হাফিজের কবিতা সবই ইলহাম, হাদীসে কুদ্সী, হিকমতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব আর কুরআনিক রহস্যাবলি।”
‘কুরআনিক রহস্যাবলির সাথে হিকমতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব’ শিরোনামটি স্বয়ং হাফিজেরই দেয়া। তিনি বলেন, ‘আমি যা বলি তা হিকমতের সূক্ষ্মতত্ত্ব (ঐশী দর্শনপ্রজ্ঞা), তবে কুরআনিক তথ্য সংশ্লিষ্ট।’ তাই মীর সাইয়্যেদ শরীফ আসলে হাফিজের নিকট থেকেই এ শিরোনামটি গ্রহণ করেছেন।
প্রতীয়মান হয় যে, হাফিজ তখনো যুবক ছিলেন এবং সে সময় মীর সাইয়্যেদ শরীফের ন্যায় পণ্ডিতদের হাফিজ সম্পর্কে মূল্যায়ন ছিল ঠিক এ ধরনের। হাফিজকে যে ‘লিসানুল গায়েব’ لسان الغيب তথা অদৃশ্যলোকের মুখপাত্র বা ভাষ্যকার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে- এটা তাঁকে পরবর্তীকালে দেয়া হয়নি। বরং সেই প্রাচীনকাল থেকেই তাঁকে ‘লিসানুল গায়েব’ বলা হতো। যদি একথা সঠিক হয় তাহলে এটা হবে আরেকটা প্রমাণ যে, এ মানুষটি তাঁর স্বীয় যুগ থেকেই একজন উঁচু আরেফ বা আধ্যাত্মিক পুরুষ হিসেবেই পরিচিত হতেন, এমনরূপে যে, মূলগতভাবে তাঁকে অদৃশ্যলোকের মুখপাত্র বলে গণ্য করা হতো। অর্থাৎ এই যে কবিতাগুলো তাঁরই আবৃত্তি, আসলে তাঁর ছিল না যে, একজন মানুষ হিসেবে সেগুলো আবৃত্তি করবেন; বরং অদৃশ্যলোক থেকেই তাঁর মুখে উচ্চারিত হতো- এ বিশ্বাস পোষণ করা হতো।
হাফিজের ইতিহাস বৃত্তান্ত থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, হাফিজ একজন মানুষ ছিলেন সচরাচর আলেমের বেশে। যদিও পাশাপাশি তিনি একজন আরেফও বটে। (তাঁর স্বজনরা তাঁকে একজন আরেফ বলেই জানতো- কোনো পেশাদার সুফি বা দরবেশ হিসেবে নয়।) তিনি একজন আলেম হিসেবেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। এদিকে মুহাম্মাদ গুল আন্দাম যখন অজুহাত দাঁড় করাতে চান যে, হাফিজ কেন নিজে তাঁর দিওয়ানকে সংকলন করে যাওয়ার অবসর পাননি কিংবা করতে চাননি, তখন বলেন, ‘তিনি এত বেশি আরবি দিওয়ানসমূহ, কাশশাফ, মেফতাহ, মেসবাহ ইতাদি পড়াশুনায় নিমগ্ন ছিলেন যে, তাঁর কোনো অবসরই ছিল না।’ হাফিজ সম্পর্কে এরূপ মনে করা হয় যে, তাঁর পড়াশুনার এতো ব্যস্ততা ছিল যে, তাঁর জন্য আর অবসর ছিল না নিজ দিওয়ান সংকলন করার। সুতরাং ইতিহাসে হাফিজের চেহারা এরূপেই প্রতিফলিত হয়েছে।
অনুবাদ : আব্দুল কুদ্দুস বাদশা