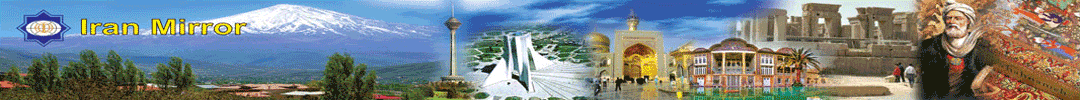আমাদের শিরাজ ভ্রমণ
পোস্ট হয়েছে: জুন ২২, ২০১৬
মোঃ মফিদুর রহমান
ইরানের রাজধানী তেহরান। কিন্তু আমার মন পড়ে ছিল শিরাজ’এ। তেহরান থেকে শিরাজ বিমানপথে সোয়া এক ঘণ্টার পথ। অথচ মনের দূরত্বে তা কিছুই নয়। বাংলাদেশ থেকে যখন আমরা তেহরান আন্তর্জাতিক বইমেলার উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিলাম তখন বলা হয়েছিল ইরানের আরো একটি শহরে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু কোন্্ সে শহর? বলা হয়েছিল হয় ইসফাহান নয়তো শিরাজ। শেষ পর্যন্ত আমাদের যাওয়া হলো শিরাজে। মহকবি শেখ সাদী আর হাফিজ এর জন্মভূমি। যে শহর খ্যাত হয়ে আছে এ দুই কবি, সুফিসাধক আর পুণ্যাত্মার নামে।
তেহরান বিমানবন্দর থেকে যে বিমানে চড়ে বসলাম, তার নাম আসমান। কী আশ্চর্য্য এ নামতো আমার কাছে ভীষণ পরিচিত; কারণ, বাংলায় আসমান-জমিন শব্দ দু’টি হরহামেশা ব্যবহৃত হচ্ছে। আসমান শব্দের অর্থ হলো আকাশ। ফারসির বদৌলতে দিব্বি ঢুকে গেছে বাংলায়। কারো আর বোঝার সাধ্যি নেই যে, এ শব্দ বাংলার নয়। এরকম হাজার হাজার ফারসি শব্দ বাংলায় প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হচ্ছে। বলা হয় প্রায় সাড়ে আট হাজার ফারসি শব্দ বাংলা ভায়ায় ঢুকে গেছে। আমরা তার হদিসও রাখি না। মোগল আমলে এদেশের রাজভাষা ছিল ফারসি। এরই সুবাদে ফারসির এমন রমরমা আধিপত্য।
শিরাজ বিমানবন্দরে নামতে না নামতেই অভ্যর্থনার পুষ্পবৃষ্টিতে সিক্ত হলাম। বিমানবন্দরের ভিভিআইপিতে গিয়ে বসলাম প্রথমে। অভ্যর্থনা জানাতে শিরাজ এর গভর্নর মহোদয় স্বয়ং হাজির। বিমান বন্দরেই ছোটখাট একটা সাংবাদিক সম্মেলন হয়ে গেল। তাদের জানবার মূল আগ্রহ হলো, কেন বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের এ সফর? কী কী বিষয় নিয়ে ইরান সরকারের সাথে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি হলো। পরবর্তীকালে দু’দেশের সরকারের মধ্যে কাজের পরিকল্পনা কী ইত্যাদি। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী মহোদয় সাংবাদিকদের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরলেন। যে কথাটি তিনি বললেন তা হলো, ইরান ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ইতিহাস অনেক পুরনো। দু’দেশের মধ্যে ধর্মীয় দিক ছাড়াও সাংস্কৃতিক অনেক বিষয়ে মিল রয়েছে। আমাদের বাংলা নববর্ষের মতো ইরানিরা নওরোজ পালন করে থাকে। ভবিষ্যতে দু’দেশের মধ্যে চিত্রকলা, নাটক, সেমিনার, সাহিত্য, অনুবাদ ইত্যাদি বিষয়ে বিনিময় কার্যক্রম আরো জোরদার হবে।
শিরাজে এসে প্রথমেই মনে হলো এখানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছিলেন ১৯৩২ সালে। কেমন ছিল শিরাজ তখন? জানা যাক রবীন্দ্রভাষ্যেই: ‘শিরাজ শহরটি যে প্রাচীন তা বলা যায় না। আরবেরা পারস্য জয় করার পরে তবে এই শহরের উদ্ভব। সাফাবি-শাসনকালে শিরাজের যে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল আফগান আক্রমণে তা ধ্বংস হয়ে যায়। আগে ছিল শহর ঘিরে পাথরের তোরণ, সেটা ভূমিসাৎ হয়ে তার জায়গায় উঠেছে মাটির দেয়াল। নিষ্ঠুর ইতিহাসের হাত থেকে পারস্য যেমন বারবার আঘাত পেয়েছে পৃথিবীতে আর-কোনো দেশ এমন পায় নি, তবু তার জীবনশক্তি বার বার নিজের পুনঃসংস্কার করেছে। বর্তমান যুগে আবার সেই কাজে সে লেগেছে, জেগে উঠেছে আপন মূর্ছিত দশা থেকে।’
শিরাজে আমাদের মূল আকর্ষণ হলো শেখ সাদীর সমাধি-দর্শন। শেখ সাদীর সমাধিদর্শন আমার জীবনে একটি অনন্য ঘটনা। আমরা যখন তাঁর সমাধি কমপ্লেক্সে যাই তখন দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল। ইরানের তপ্ত আবহাওয়ায় রোদের তেজ কিছুটা হলেও কমে এসেছে। এ ধরনের শুষ্ক আবহাওয়ার সাথে আমি একদমই অভ্যস্ত ছিলাম না। ইরানে যে ক’দিন থেকেছি আমার শরীর পানিশুষ্ক হয়ে বেশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। প্রচুর পানি খাওয়া হলেও অবস্থার তেমন একটিা উন্নতি হয়নি। রাতে ক্লান্ত শরীরে হোটেলে ফিরলে লক্ষ করতাম নাক দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। প্রথমদিকে ভীষণ ভয় পেলেও পরে আসল কারণ ধরতে পারায় আর সমস্যা হয়নি। একদিন বাংলাদেশ মিশনের গাড়ির ড্রাইভারকে বললাম, ‘ভাই তুমি আমাকে বাঁচাও।’ সে বাজার থেকে একটি ভেজলিনের ছোট্ট কৌটা এনে দিল; যেটি ব্যবহার করে সে যাত্রায় রক্ষা পেয়েছিলাম।
শেখ সাদীর কবিখ্যাতি দুনিয়াজোড়া। তাঁর জন্মতারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবু যতটুকু জানা যায়, তিনি ১১৬৪ সালে জন্মগ্রহণ ও ১১৯২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। শেখ সাদীর প্রকৃত নাম শরফুদ্দীন। তাঁর ডাক নাম মসলেহউদ্দীন। সাদী ছিল তাঁর উপাধি। বিশ্বের মানুষের কাছে তিনি পরিচিত শেখ সাদী নামে। সাদীর বাবা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু ও নৈতিকতা পরায়ণ মানুষ। সাদীও এসব গুণে গুণান্বিত হয়েছিলেন শৈশব থেকেই। বাল্যকালে তাঁর বাবা মারা গেলে তিনি তাঁর মামা পণ্ডিত আল্লামা কুতুবউদ্দিন শিরাজীর ¯েœহধন্য হন। ছোটবেলা থেকে সাদী শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তিনি উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বাগদাদ চলে যান এবং সেখানকার বিখ্যাত মাদ্রাসা নিযামিয়ায় ভর্তি হন। সাদী ছিলেন একাধারে একজন কবি-সাহিত্যক-জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি একাধিক ভাষা জানতেন। ভ্রমণ করেছিলেন অনেক দেশ। বলা হয়, তিনি পায়ে হেঁটে চৌদ্দবার হজ করেছিলেন। শেখ সাদীর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হল: গুলিস্তাঁ, বুস্তাঁ, করিমা, সাহাবিয়া, কাসায়েদে ফারসি, কাসায়েদে আরাবিয়া, গযলিয়াত, কুল্লিয়াত ইত্যাদি। গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁ গ্রন্থের অনেক কথা আজ প্রবাদে পরিণত হয়েছে। অনেকে শেখ সাদীকে ইংরেজ লেখক উইলিয়ম শেক্সপীয়রের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। গুলিস্তাঁ উপদেশমূলক গল্পে ভরা। শেখ সাদীর অনেক নৈতিকতাপূর্ণ গল্প শৈশবে আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলতো। একটি গল্প তো অত্যন্ত প্রচলিত। শেখ সাদীর পায়ে একবার কোন জুতা ছিল না। এ অবস্থায় তিনি গিয়ে উঠলেন কুফার এক মসজিদে। তাঁর মন বেজায় খারাপ। এমন সময় তিনি দেখলেন, একটি লোক মসজিদে শুয়ে আছে যার একখানি পা-ই নেই। তখন তিনি খোদাকে মনে মনে অনেক ধন্যবাদ দিলেন নিজের সৌভাগ্যের জন্য। শেখ সাদীর পোশাকের গল্পটিও আমাদের অনেক শোনা ও শিক্ষামূলক একটি বিখ্যাত গল্প।
শেখ সাদীর মাজারে প্রচুর পর্যটকের ভিড় দেখলাম। এরা যে সাবাই বিদেশি পর্যটক তা কিন্তু নয়। ইরানের নাগরিকেরাও শিরাজ ভ্রমণে এসেছে। একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম ইরানের মানুষেরা প্রতি সপ্তাহে ছুটির দিনে ছেলেমেয়ে ও পরিবার নিয়ে লং ড্রাইভে বেরিয়ে যায়।
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও শেখ সাদীর মাজারে এসেছিলেন ১৯৩২ সালে। তিনি লিখেছেন, ‘১৭ এপ্রেল। আজ অপরাহ্নে সাদীর সমাধিপ্রাঙ্গণে আমার অভ্যর্থনার সভা।… সাদীর সমাধিতে স্থাপত্যের গুণপনা কিছুই নেই।’
রবীন্দ্রনাথের দেখা শেখ সাদীর সমাধি নিয়ে বর্ণনা বর্তমান সময়ের সাথে মেলে না। এখন সাদীর সমাধি ক্ষেত্র অনেক দূর থেকে চোখে পড়ে। সবুজ গম্বুজে ঢাকা কবি-দার্শনিক-পণ্ডিত শেখ সাদীর সমাধি দেখতে খুবই সুন্দর। সবচেয়ে অবাক করে এ জায়গার গাম্ভীর্য ও আধ্যাত্মিকতা। মনে হয় জীবন এখানে বিছিয়ে রেখেছে অপার শান্তি। এ সমাধিতে এসে নিজেকে আত্মআবিষ্কারের সুযোগ পাওয়া যায়। মনে হয় এ অমর জীবন-দার্শনিক হয়তো এখনি জেগে উঠবেন। শোনাবেন তাঁর সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে কোন কাব্য নয়তো নৈতিকতার বা উপদেশমূলক গল্প, যা শুনে জীবন হবে ঋদ্ধ। এভাবেই ভাবের গভীর সাগরে ডুব দিয়ে মহাকবি শেখ সাদীকে সালাম জানিয়ে তাঁর সমাধিপ্রাঙ্গণ ত্যাগ করলাম।
ইরানের আরেক মহাকবি হাফিজ শিরাজী। পুরো নাম খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ হাফিজ শিরাজী। তিনি ৭১০-৭৩০ হিজরি সনের মধ্যে ইরানের শিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ হরেন। তাঁর পিতার নাম বাহাউদ্দিন সুলগারী। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, হাফিজের পিতা ইসফাহান হতে ব্যবসার উদ্দেশ্যে শিরাজে আসেন। প্রথমদিকে ব্যবসায়ে প্রচুর উন্নতি করলেও মৃত্যুকালে তাঁর ব্যবসা পতিত হয়ে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। এতে হাফিজ ও তাঁর মা দারিদ্র্যের করাল গ্রাসে পড়েন। একারণে পিতৃহারা হাফিজকে ছোট বয়সেই বিদ্যালয়ে গমনের পরিবর্তে জীবিকার তাগিদে একটি রুটির দোকানে কাজ করতে হয়। বুলবুল-ই-শিরাজের সঙ্গে এদিক থেকে বাংলাদেশের জাতীয় ও বিদ্রোহী কবি বাংলার বুলবুল কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের মিল পরিলক্ষিত হয়। তিনিও শৈশবে রুটির দোকানে কাজ করতেন। হাফিজ রুটির দোকানে কাজ করার পাশাপাশি মক্তবে পড়াশুনা করতে থাকেন এবং অল্পদিনেই কুরআন মুখস্থ করে অশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। কথিত আছে তিনি চৌদ্দটি পদ্ধতিতে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারতেন।
কাব্যপ্রতিভায় হাফিজ এতটাই উৎকৃষ্টমানের ছিলেন যে, পাশ্চত্যের আরেক মহান কবি গ্যেটে বলেন, ‘হঠাৎ প্রাচ্যের আসমানি খুশবু এবং ইরানের পথ-প্রান্তর হতে প্রবাহিত চিরন্তন প্রাণ সঞ্জীবনী সমীরণের সাথে পরিচিত হলাম। আমি এমন এক ব্যক্তিকে চিনতে পারলাম, যাঁর বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব আমাকে আপাদমস্তক তার জন্য পাগল করেছে।’
শুধু পাশ্চাত্য নয়, হাফিজ প্রাচ্যের, এমনকি বাংলা ভাষার কবি ও চিন্তাশীল ব্যক্তিকে সমানভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩২ সালে হাফিজের মাজারে যান। তাঁর শরীর তখন তেমন একটা ভাল নয়। তথাপি তিনি এ সুফি কবির সমাধি দর্শনের টান উপেক্ষা করতে পারেন নি। শোনা যায় তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও হাফিজের অসম্ভব ভক্ত ছিলেন। শিরাজে কবি হাফিজের সমাধিপাশে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন এভাবে: ‘এই সমাধির পাশে বসে আমার মনের মধ্যে একটা চমক এসে পৌঁছল, এখানকার এই বসন্তপ্রভাতে সূর্যের আলোতে দূরকালের বসন্তদিন থেকে কবির হাস্যোজ্জ্বল চোখের সংকেত। মনে হল আমরা দুজনে একই পানশালার বন্ধু, অনেকবার নানা রসের অনেক পেয়ালা ভরতি করেছি। আমিও তো কতবার দেখেছি আচারনিষ্ঠ ধার্মিকদের কুটিল ভ্রূকুটি। তাদের বচনজালে আমাকে বাঁধতে পারেনি; আমি পলাতক, ছুটি নিয়েছি অবাধপ্রবাহিত আনন্দের হাওয়ায়। নিশ্চিত মনে হল আজ, কত-শত বৎসর পরে জীবনমৃত্যুর ব্যবধান পেরিয়ে এই কবরের পাশে এমন একজন মুসাফির এসেছে যে মানুষ হাফেজের চিরকালের জানা লোক।’ (পারস্যে: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
আমাদের জাতীয় কাজী নজরুল ইসলাম হাফিজের এতটাই অনুরক্ত ছিলেন যে, তিনি ফারসি থেকে ৭৩টি রুবাই সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। তিনি যেদিন অনুবাদ শেষ করেন সেদিন কবির পুত্র বুলবুল মারা যান। কবি তাই বেদনার সাথে উচ্চারণ করেছিলেন, ‘আমি আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান ও সবচেয়ে প্রিয় সম্পদকে উপঢৌকন দিয়ে শিরাজের বুলবুল কবিকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। ইরানের কবিস¤্রাট হাফিজ বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিনের আমন্ত্রণে সাড়া দেননি। কিন্তু আমার আমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে পারতেন না।’
হাফিজ জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁর সেই শাশ্বত প্রেমময় উক্তির জন্য: ‘প্রিয়ার গালের একটি তিলের জন্য বিলিয়ে দিতে পারি সমরখন্দ বোখারা।’ কে সেই ভাগ্যবতী তা অবশ্যি আজো জানা যায়নি। তবে প্রত্যেক কালে প্রতিটি প্রেমিক হৃদয় কল্পনায় তার প্রেমিককে নিশ্চয়ই হাফিজ-কথিত প্রেমিকার আসনে স্থান দিয়ে এ কথাটিই ভাবে। এখানে হাফিজের কাব্যের অমরতা ও প্রাসঙ্গিকতা।
হাফিজের সমাধির উদ্দেশে যখন আমরা রওয়ানা হই তখন শিরাজে সন্ধ্যা নামছে। আমার মাথায় একটা প্রশ্ন বিকেল থেকেই ঘুরপাক খাচ্ছিলো, কেন সন্ধ্যারাতে আমরা হাফিজের মাজার-সন্দর্শনে যাচ্ছি? রাতের অন্ধকারে ওখানে আমরা কি দেখব? দিনের আলো মিলিয়ে গেলে তো ভালভাবে কিছুই দেখা যাবে না। শেষ পর্যন্ত আমি বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তা এবং গাইডকে জিজ্ঞেস করেই বসলাম। প্রতিউত্তরে যা শুনলাম তাহলো, হাফিজভক্তরা সন্ধ্যা থেকেই তাঁর মাজারে ভিড় করতে থাকে। কারণ, হাফিজ হলেন প্রেমের কবি। তাঁর কবিতায় প্রেমের কথকতায় প্রেমিককূল আবেগাপ্লুত হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে সন্ধ্যার আলোআঁধারিতে তাঁর সমাধিপ্রাঙ্গনে আসে। আমি সত্যিই অবাক হলাম। রাতের আলোআঁধারিতে প্রচুর নারী-পুরুষ, প্রেমিক-প্রেমিকা জুটিকে দেখে। মুগ্ধনয়নে নির্বাক হয়ে কিছুক্ষণের জন্যে আমিও প্রেমিক হৃদয়ে পরিণত হলাম। মনে জাগলো এক আশ্চর্য শিহরণ!
এরই মধ্যে আমাদের গাইড একটি অদ্ভুত কথা বললেন। তিনি হাফিজের একটি কবিতার বই এনে আমাদেরকে বললেন মনে মনে একটি কথা স্মরণ করতে বা ভাবতে। একথা বলে তিনি বললেন যে, ‘তুমি একটি ভাবনা ভাবতে ভাবতে হাফিজের বইয়ের যে পাতাটি মেলে ধরবে দেখা যাবে সেই কবিতার মূল ভাবের সাথে তোমার ভাবনা মিলে যাবে।’ আমরা পরীক্ষা দিলাম এবং যথারীতি কবি হাফিজ সেই পরীক্ষায় দারুণভাবে উত্তীর্ণ হলেন। মনে মনে ভাবলাম, এর রহস্য কী? মনের গহীন থেকে উত্তর এলো, যুগে যুগে প্রেমের তপস্যা এক, প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ের ভাষা, চোখের চাহনির মর্ম এক, মনের আকুতি কিংবা বিরহের তপস্যা- সেও তো একই। হাফিজ যদি সে কথাই তাঁর কবিতায় বলেন, তা হলে যুগে যুগে কালে কালে সব প্রেমিক-প্রেমিকা, নর-নারীর হৃদয়ের ভাবনা তো মিলেই যাবে। শত কোটি সালাম সুফি-দরবেশ ও প্রেমিক কবি হাফিজকে।